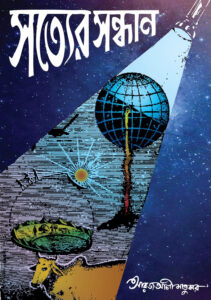সত্যের সন্ধান সর্বহারা পথ প্রকাশনা পুস্তিকা
সত্যের সন্ধান কভার পৃষ্ঠা মুদ্রন সত্যের সন্ধান সর্বহারা পথ বই মুদ্রনের জন্য
সত্যের সন্ধান
[লৌকিক দর্শন]
আরজ আলী মাতুব্বর বাংলাদেশের মাটি থেকে উঠে আসা এক বস্তুবাদী দার্শনিক। আজীবন তিনি সমাজে বিদ্যমান মিথ্যা ও কুসংস্কারকে যুক্তিযুক্তভাবে খন্ডন করতে আর বস্তুবাদী সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এজন্য তার উপর নেমে এসেছে জেলহাজত থেকে শুরু করে বহুবিধ অত্যাচার-নির্যাতন, যা তাকে দমাতে পারেনি দ্বান্দ্বিক ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা থেকে। আরজ আলীর রচনা অধ্যয়ন করলে ভাববাদী মিথ্যা-মায়া-মরীচিকাকে চূর্ণ করে দেয়া সহজ হবে, আর বস্তুবাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য তা অবশ্য প্রয়োজন
—কেন্দ্রীয় অধ্যয়ন গ্রুপ
সিপিএমএলএম বাংলাদেশ
২৫ জুন ২০২২
লেখক কর্তৃক প্রথম প্রকাশ ২০ শ্রাবণ ১৩৮০ বাং
লেখক কর্তৃক দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৬ জৈষ্ঠ্য ১৩৯০ বাং
পাঠক সমাবেশ কর্তৃক রচনাবলী প্রকাশ ১৯৯৫-২০১২ ইং
সিপিএমএলএম বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বহারা পথ www.sarbaharapath.com
এর অনলাইন প্রকাশনা ২৫ জুন ২০২২ ইং
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা
এলোমেলোভাবে মনে যখন যে প্রশ্ন উদয় হইতেছিল, তখন তাহা লিখিয়া রাখিতেছিলাম, পুস্তক প্রণয়নের জন্য নহে, স্মরণার্থে। ওগুলি আমাকে ভাসাইতেছিল অকূল চিন্তা-সাগরে এবং আমি ভাসিয়া যাইতেছিলাম ধর্মজগতের বাহিরে।
১৩৫৮ সালের ১২ই জৈষ্ঠ্য; বরিশালের তদানীন্তন ল-ইয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও তবলিগ জামাতের আমির জনাব এফ. করিম সাহেব আমাকে তাঁহার জামাতভুক্ত করার মানসে সদলে হঠাৎ তসরিফ নিলেন আমার বাড়ীতে। তিনি আমাকে তাঁহার জামাতভুক্তির অনুরোধ জানাইলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, ধর্মজগতে এরূপ কতগুলি নীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি এবং ঘটনার বিবরণ প্রচলিত আছে, যাহা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নহে এবং ওগুলি দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এমনকি অনেকক্ষেত্রে বিপরীতও বটে। ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান এই তিনটি মতবাদের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে চিন্তা করিতে যাইয়া আমার মনে কতগুলি প্রশ্নের উদয় হইয়াছে এবং হইতেছে। আমি ঐগুলি সমাধানে অক্ষম হইয়া এক বিভ্রান্তির আঁধার কূপে নিমজ্জিত
হইয়া আছি। আপনি আমার প্রশ্নগুলির সুষ্ঠু সমাধানপূর্বক আমাকে সেই বিভ্রান্তির আঁধার কূপ হইতে উদ্ধার করিতে পারিলে আমি আপনার জামাতভুক্ত হইতে পারি। জনাব করিম সাহেব আমার প্রশ্নগুলি কি, তাহা জানিতে চাহিলে আমি আমার প্রশ্নের একখানা তালিকা (যাহা অত্র পুস্তকের ‘সূচীপত্র’ রূপে লিখিত আছে সেই রূপেই) তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তিনি উহা পাঠ করিলেন এবং সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন, আর বলিয়া গেলেন — “কিছুদিন বাদে এর জওয়াব পাবেন”।
করিম সাহেব চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে আমি পাইয়াছিলান কম্যুনিজমের অপরাধে আসামী হিসাবে ফৌজদারী মামলার একখানা ওয়ারেন্ট, কিন্তু আমার প্রশ্নগুলির জবাব আজও পাই নাই। করিম সাহেবকে প্রদত্ত তালিকার প্রশ্নের সহিত কোন ব্যাখ্যা ছিল না। ফৌজদারী মামলার জবাবদিহি করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে প্রশ্নগুলির কিছু ব্যাখ্যা লিখিতে হয়। সেই ব্যাখ্যা লিখাই হইল এই পুস্তক রচনার মূল উৎস। নির্দোষ প্রমাণে মামলা চূড়ান্ত হইলে ঐগুলিকে আমি পুস্তক আকারে গ্রথিত করিলাম। গ্রন্থনায় আমাকে উৎসাহিত ও সহযোগিতা দান করিয়াছিল স্নেহাস্পদ মো. ইয়াছিন আলী সিকদার।
এই পুস্তকখানার সম্পাদনা সম্পর্কে নানাবিধ উপদেশ, ভ্রম সংশোধন, এলোমেলো প্রশ্নগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির সাহেব।
এই পুস্তকখানার সম্পাদনা শেষ হইয়াছিল বিগত ১৩৫৮ সালে। কিন্তু নানা কারণে এযাবৎ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে ইহার কোন কোন অংশের কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া প্রকাশ করা হইল। বর্ধিত অংশের ভ্রম সংশোধনের শ্রম স্বীকার করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মুহাম্মদ শামসুল হক সাহেব এবং প্রকাশনায় আর্থিক সাহায্যদান করিয়াছেন মাননীয় অধ্যাপক শরফুদ্দিন রেজা হাই সাহেব। এতদকারণে সহযোগীদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।
বিনীত
গ্রন্থকার
লামচরি, বরিশাল
২০ শ্রাবণ ১৩৮০
দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা
‘সত্যের সন্ধান’ পুস্তিকাখানা প্রকাশিত হইলে ইহা সুধীমহলে সমাদৃত হয়, বহু পত্র-পত্রিকায় প্রশংসামূলক সমালোচনা হইতে থাকে এবং বইখানার জন্য বাংলাদেশ লেখক শিবির আমাকে ‘হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার’ প্রদান করে [৮. ৫. ১৯৭৯]।
আশা ছিল যে, ‘সত্যের সন্ধান’ পুস্তিকাখানার দ্বিতীয় মুদ্রণ সম্ভব হইলে তাহাতে কিছু নতুন তত্ত্ব জানার জন্য কিছু নতুন প্রশ্ন পরিবেশন করিব, কিন্তু নানা কারণে তাহা আর সম্ভব হইল না। এই বইখানা প্রথম প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং বর্তমানেও হইতেছে — আমি আশা করি যে, আমার লিখিত ‘মুক্তমন’ নামীয় পুস্তকখানার ‘ভূমিকা’-এ তাহা ব্যক্ত করিব। তবে সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন যাহা করা হইল, তাহার মধ্যে — ‘ঈশ্বর কি দয়াময়?’ শীর্ষক একটি প্রশ্ন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ) সরদার ফজলুল করিম সাহেবের লিখিত (সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত) একটি অভিমত ছাড়া আর কিছুই উল্লেখযোগ্য নহে। কালোপযোগী পরিবর্তন করা গেল না সময়ের অভাবে।
‘সত্যের সন্ধান’ বইখানা প্রণয়নকালে ইহার একটি উপনাম দেওয়া হয় ‘যুক্তিবাদ’। কিন্তু বর্তমানে সুধীমহল এ পুস্তিকাখানাকে ‘দর্শন’ শ্রেণীভুক্ত করায় ইহার উপনাম দেওয়া হইল ‘লৌকিক দর্শন’।
বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে এ পুস্তিকাখানার পুনঃপ্রকাশ আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হইত না — ঢাকাস্থ বর্ণমিছিল প্রেসের অধিকারী তাজুল ইসলাম সাহেবের সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া। আমি তাঁহার নিকট শুধু কৃতজ্ঞই নহি, অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী।
আরজ আলী মাতুব্বর
১৬ জৈষ্ঠ্য ১৩৯০
মূলকথা
[প্রশ্নের কারণ]
অজানাকে জানার স্পৃহা মানুষের চিরন্তন। বাক্যস্ফূরণ আরম্ভ হইলেই শিশু প্রশ্ন করিতে থাকে, এটি কি? ওটি কি? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে, কলেজে ও কাজে-কর্মে অনুরূপ প্রশ্ন চলিতে থাকে, এটি কি, ওটি কি, এরূপ কেন হইল, ওরূপ কেন হইল, ওরূপ কেন হইলনা ইত্যাদি। এই রকম ‘কি’ ও ‘কেন’র অনুসন্ধান করিতে করিতেই মানুষ আজ গড়িয়া তুলিয়াছে বিজ্ঞানের অটল সৌধ।
প্রশ্নকর্তা সকল সময়ই জানিতে চায় — সত্য কি? তাই সত্যকে জানিতে পারিলে তাহার আর কোন প্রশ্ন থাকেনা। কিন্তু কোন সময় কোন কারণে কোন বিষয় এর সত্যতায় সন্দেহ জাগিলে উহা সম্পর্কে পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে থাকে।
কোন বিষয় বা কোন ঘটনা একাধিকবার সত্য হইতে পারে না। একটি ঘটনা যখন দুই রকম বর্ণিত হয়, তখন হয়ত উহার একটি সত্য, অপরটি মিথ্যা; উভয়ই সমরূপ মিথ্যা, উভয়ই যুগপতসত্য হইতে পারেনা – হয়ত সত্য অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। এক ব্যক্তি যাহাকে ‘সোনা’ বলিল, অপর ব্যক্তি তাহাকে বলিল ‘পিতল’। এ ক্ষেত্রে বস্তুটি কি দুই রূপেই সত্য হইবে? কেহ বলিল যে, অমুক ঘটনা ১৫ই বৈশাখ ১২টায় ঘটিয়াছে; আবার কেহ বলিল যে উহা ১৬ই চৈত্র ৩টায়। এস্থলে উভয় বক্তাই কি সত্যবাদী? এমতাবস্থায় উহাদের কোন ব্যক্তির কথায়ই শ্রোতার বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। হয়ত কোন একজন ব্যক্তি উহাদের একজনের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিল, অনুরূপ অন্য এক ব্যক্তি অপরজনের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিল, অপরজন তাহা মিথ্যা বলিয়া ভাবিল। এইরূপে উহার সত্যাসত্য নিরূপণে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ঘটিল মতানৈক্য। আর এইরূপ মতানৈক্য হেতু ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ঘটিয়া থাকে নানারূপ ঝগড়া-কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এই রকম বিষয়বিশেষে ব্যক্তিগত মতানৈক্যের ন্যায় সমাজ বা রাষ্ট্রগত মতানৈক্যও আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; যাহার পরিণতি সাম্প্রদায়িক কলহ ও যুদ্ধবিগ্রহরূপে আজ আমরা চোখের উপরই দেখিতে পাইতেছি।
জগতে এমন অনেক বিষয় আছে, যে সব বিষয়ে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম এক কথা বলে না। আবার ধর্মজগতেও মতানৈক্যের অন্ত নাই। যেখানে একই কালে দুইটি সত্য হইতে পারে না, সেখানে শতাধিক ধর্মে প্রচলিত শতাধিক মত সত্য হইবে কিরূপে? যদি বলা হয় যে, সত্য হইবে একটি; তখন প্রশ্ন হইবে কোনটি এবং কেন? অর্থাৎ সত্যতা বিচারের মাপকাঠি (Criterion of truth) কি? সত্যতা প্রমাণের উপায় (Test of truth) কি এবং সত্যের রূপ (Nature of truth) কি?
আমরা ঐ সকল দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবিষ্ট হইব না, শুধু ধর্মজগতের মতানৈক্যের বিষয় সামান্য কিছু আলোচনা করিব।
আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানিতে পাইতেছি যে, বিশ্বমানবের সহজাত বৃত্তি বা ‘স্বভাবধর্ম’ একটি। এ সংসারে সকলেই চায় সুখে বাঁচিয়া থাকিতে, আহার-বিহার ও বংশরক্ষা করিতে, সন্তান-সন্ততির ভিতর দিয়া অমর হইতে। মানুষের এই স্বভাবধর্মরূপ মহাব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সংসারে সৃষ্টি হইল কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সমাজ, নীতি এবং রাষ্ট্র; গড়িয়া উঠিল জ্ঞান-বিজ্ঞানময় এই দুনিয়া। মানুষ যেখানে যে কাজেই লিপ্ত থাকুক না কেন, একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে সে তাহার ‘স্বভাবধর্ম’ তথা ‘স্বধর্ম’ পালনে ব্রতী। এই মহাব্রত উদযাপনে কাহারো কোন প্ররোচনা নাই এবং এই ধর্ম পালনে মানুষের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই।
এই স্বভাবধর্মই মানুষের ধর্মের সবটুকু নয়। এমনকি ‘ধর্ম’ বলিতে প্রচলিত কথায় এই স্বভাবধর্মকে বুঝায়না। যদিও একথা স্বীকৃত হইয়া থাকে যে পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ এমনিক জল, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদিরও এক-একটি ধর্ম আছে, অথচ বিশ্বমানবের ধর্ম বা ‘মানবধর্ম’ বলিয়া আন্তর্জাতিক ধর্মকে স্বীকার করা হয় না। সাধারণত আমরা যাহাকে ‘ধর্ম’ বলি তাহা হইল মানুষের কল্পিত ধর্ম। যুগে যুগে মহাজ্ঞানীগণ এই বিশ্বসংসারের স্রষ্টা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি তাহা নির্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। “স্রষ্টার প্রতি মানুষের কি কোন কর্তব্য নাই? নিশ্চয়ই আছে” — এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কি তাহা নির্ধারণ করিয়া দিলেন। অধিকন্তু মানুষের সমাজ ও কর্মজীবনের গতিপথও দেখাইয়া দিলেন সেই মহাজ্ঞানীগণ। এইরূপে হইল কল্পিত ধর্মের আবির্ভাব। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মনীষী বা ধর্মগুরুদের মতবাদ হইল ভিন্ন ভিন্ন।
এই কল্পিত ধর্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল উহাতে মতভেদ। ফলে পিতা-পুত্রে, ভাইয়ে-ভাইয়ে, এমনকি স্বামী-স্ত্রীতেও এই কল্পিত ধর্ম নিয়া মতভেদের কথা শোনা যায়। এই মতানৈক্য ঘুচাইবার জন্য প্রথমত আলাপ-আলোচনা, পরে বাক-বিতণ্ডা, শেষ পর্যন্ত যে কত রক্তপাত হইয়া গিয়াছে, ইতিহাসই তাহার সাক্ষী। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে বিশ্বমানব একমত হইতে পারিয়াছে কি?
কেবল যে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন মত এমন নহে। একই ধর্মের ভিতরেও মতভেদের অন্ত নাই। হিন্দু ধর্মের বেদ যাহা বলে, উপনিষদ সকল ক্ষেত্রে তাহার সহিত একমত নহে। আবার পুরাণের শিক্ষাও অনেক স্থলে অন্যরূপ। ‘বাইবেল’-এর পুরাতন নিয়ম (Old Testament) ও নূতন নিয়মে (New Testament) অনেক পার্থক্য। পুনশ্চ প্রোটেষ্ট্যান্ট (Protestant) ও ক্যাথলিকদের (Roman Catholic) মধ্যেও অনেক মতানৈক্য রহিয়াছে।
পবিত্র কোরানপন্থীদের মধ্যেও মতবৈষম্য কম নহে। শিয়া, সুন্নী, মুতাজিলা, ওহাবী, কাদিয়ানী, খারিজী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মত এক নহে। আবার একই সুন্নী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হানাফী, শাফী ইত্যাদি চারি মাজহাবের মতামত সম্পূর্ণ এক নহে। এমনকি একই হানাফী মজহাব অবলম্বী বিভিন্ন পীর ছাহেবদের যথা — জৌনপুরী, ফুরফুরা, শর্ষিণা বিভিন্ন খান্দানের বিভিন্ন রেছালা। মহাত্মা রামমোহন রায়ের অতিআধুনিক ব্রাহ্মধর্মও অধুনা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে।
এতোধিক মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও ভক্তদের নিকট আপন আপন ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ, সনাতন ও ঈশ্বর-অনুমোদিত, মুক্তি বা পরিত্রাণের একমাত্র পন্থা। বলা বাহুল্য যে, এরূপ ধারণা প্রত্যেক ধর্মেই বিদ্যমান। কোন ধর্মে একথা কখনও স্বীকার করে না যে, অপর কোন ধর্ম সত্য অথবা অমুক ধর্মাবলম্বী লোকদের স্বর্গপ্রাপ্তি, মুক্তি বা নির্বাণ ঘটিবে। বরং সকল সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকেরা এই কথাই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের আপন আপন ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম, অন্য কোন ধর্মই সত্য নহে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের স্বর্গপ্রাপ্তি, পরিত্রাণ, নির্বাণ বা মোক্ষলাভ ঘটিবেনা। এ যেন বাজারের গোয়ালাদের ন্যায় সকলেই আপন আপন দধি মিষ্টি বলে।
বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মই আস্তিক। বিশেষত একেশ্বরবাদী। হিন্দুধর্মও মূলত একেশ্বরবাদী। তাহাই যদি হয়, অর্থাৎ জগতের সকল লোকেই যদি একেশ্বরবাদী হয়, তবে তাহাদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃভাব থাকা উচিত। কিন্তু আছে কি? আছে যত রকম হিংসা, কলহ ও বিদ্বেষ। সম্প্রদায়বিশেষে ভুক্ত থাকিয়া মানুষ মানুষকে এত অধিক ঘৃণা করে যে তদ্রুপ কোন ইতর প্রাণীতেও করে না। হিন্দুদের নিকট গোময় (গোবর) পবিত্র, অথচ অহিন্দু মানুষ মাত্রেই অপবিত্র। পক্ষান্তরে মুসলমানদের নিকট কবুতরের বিষ্ঠাও পাক, অথচ অমুলমান মাত্রেই নাপাক। পুকুরে সাপ, ব্যাঙ মরিয়া পচিলেও উহার জল নষ্ট হয় না, কিন্তু বিধর্মী মানুষে ছুঁইলেও উহা হয় অপবিত্র। কেহ কেহ একথাও বলেন যে, অমুসলমানী পর্ব উপলক্ষে কলা, কচু, পাঁঠা বিক্রিও মহাপাপ। এমনকি মুসলমানের দোকান থাকিতে হিন্দুর দোকানে কোন কিছু ক্রয় করাও পাপ। এই কি মানুষের ধর্ম? না ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা?
মানবতার মাপকাঠিতে মানুষ একে অন্যের ভাই, ভালবাসার পাত্র, দয়া-মায়ার যোগ্য, সুখ-দুঃখের ভাগী; এক কথায় একান্তই আপন। কিন্তু ধর্মে বানাইল পর।
স্বভাবতই মানুষ সত্যকেই কামনা করে, মিথ্যাকে নয়। তাই আবহমানকাল হইতেই মানুষ ‘সত্যের সন্ধান’ করিয়া আসিতেছে। দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি জ্ঞানানুশীলনের বিভিন্ন বিভাগ সর্বদাই চায় মিথ্যাকে পরিহার করিতে। তাই দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক, কোন ঐতিহাসিক কিংবা নৈয়ায়িক সজ্ঞানে তাঁহাদের গ্রন্থে মিথ্যার সন্নিবেশ করেন না। বিশেষত তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থের ভূমিকায় এমন প্রতিজ্ঞাও করেন না যে, তাঁহাদের গ্রন্থের কোথাও কোন ভূলভ্রান্তি নাই। অথবা থাকিলেও তাহা তাঁহারা সংশোধন করিবেন না। পক্ষান্তরে যদি কাহারো ভূলত্রুটি প্রমাণিত হয়, তবে তিনি তাহা অম্লানবদনে স্বীকার করেন এবং উহা সংশোধনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এইরূপ পরবর্তী সমাজ পূর্ববর্তী সমাজের ভূলত্রুটি সংশোধন করিয়া নিয়া থাকে। এইরকম যুগে যুগে যখনই অতীত জ্ঞানের মধ্যে কোন ভূলভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়, তখনই উহার সংশোধন হইয়া থাকে। এক যুগের বৈজ্ঞানিক সত্য আরেক যুগে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যায় এবং যখনই উহা প্রমাণিত হয়, তখনই বৈজ্ঞানিক সমাজ উহাকে জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করেন ও প্রমাণিত নূতন সত্যকে সাদরে গ্রহণ করেন।
ধর্মজগতে কিন্তু ঐরূপ নিয়ম পরিলক্ষিত হয় না। তৌরিত, জব্বুর, ইঞ্জিল, কোরআন, বেদ-পুরাণ, জেন্দ-আভেস্তা ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রত্যেকটি অপৌরুষেয় বা ঐশ্বরিক পুঁথি কি না, তাহা জানি না, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটি গ্রন্থ এই কথাই বলিয়া থাকে যে, এই গ্রন্থই সত্য। যে বলিবে যে, ইহা মিথ্যা — সে নিজে মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী, পাপী অর্থাৎ নারকী।
ধর্মশাস্ত্রসমূহের এইরূপ নির্দেশ হেতু কে যাইবে ধর্মশাস্ত্রসমূহের বিরুদ্ধে কথা বলিয়া নারকী হইতে? আর বলিয়াই বা লাভ কি? অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থই গ্রন্থকারবিহীন অর্থাৎ ঐশ্বরিক বা অপৌরুষেয়, সুতরাং উহা সংশোধন করিবেন কে?
প্রাগৈতিহাসিককাল হইতে জগতে শত শত রাষ্ট্রের উত্থান হইয়াছে এবং পরস্পর কলহ-বিবাদের ফলে তাহাদের পতন ঘটিয়াছে। কিন্তু ধর্মে-ধর্মে যতই কলহ-বিবাদ থাকুক না কেন, জগতে যতগুলি ধর্মের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহার একটিও আজ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই। ইহার প্রথম কারণ হইল এই যে, রাষ্ট্রের ন্যায় ধর্মসমূহের আয়ত্তে তোপ-কামান-ডিনামাইট বা এটম বোম নাই, যাহা দ্বারা একে অন্যের ধ্বংস সাধন করিতে পারে। ধর্মের হাতে আছে মাত্র দুইটি অস্ত্র — আশীর্বাদ ও অভিশাপ। এহেন অস্ত্রসমূহ ব্যক্তিবিশেষের উপর ক্রিয়াশীল কিনা, জানি না, কিন্তু কোন সম্প্রদায় বা জাতির উপর একেবারেই অকেজো।
উহার দ্বিতীয় কারণ এই যে, প্রত্যেক ধর্মেই তাহার নির্দিষ্ট বিধি-বিধানসমূহের সত্যাসত্যের সমালোচনা একেবারেই বন্ধ। যেমন পাপ ও নরকের ভয়ে ভিতরের সমালোচনা বন্ধ, তেমন বাহিরের (ভিন্নধর্মের লোকদের) সমালোচনা চিরকালই বাতিল। কাজেই ধর্ম নির্বিঘ্নে আপন মনে দিন কাটাইতেছে। কিন্তু এইখানেই কি শেষ? না, বোবারও কল্পনাশক্তি আছে। মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও সে বিশ্বের ঘটনাবলী সম্পর্কে চিন্তা করে, সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বোবার সেই ভাবসমূহের অভিব্যক্তি ঘটে তাহার কার্যাবলীর মধ্য দিয়া।
ধর্মজগতে মানুষের স্বাধীন চিন্তা-ক্ষেত্র নিতান্তই অপরিসর। তাই বাঁধ-ভাঙ্গা জলস্রোতের ন্যায় সময় মানুষের কল্পনা ধর্মের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বিধি-নিষেধের গণ্ডির বাহিরে চলিয়া যায়। ধর্মশাস্ত্র যে সকল বিষয় ভাবিতে নিষেধ করিয়াছে, মানুষ তাহাও ভাবে এবং সমস্যার সমাধান না পাওয়ায় দুই একজন আনাড়ী লোক ধর্মযাজকদের নিকট গোপনে প্রশ্ন করে, ইহা কেন? উহা কেন? সমস্যা যতই জটিল হউক না কেন, উহার সমাধান হয়ত জলের মত সোজা। যাজক জবাব দেন, “ঐসকল গুপ্ততত্ত্বসমূহের ভেদ সে (আল্লাহ্) ছাড়া কেহই জানেনা। ধরিয়া লও ওসকল তারই মহিমা” ইত্যাদি।
ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে, জ্ঞানই পুণ্য (Knowledge is virtue)। কিন্তু যে বিষয়ে কোন জ্ঞান জন্মিলনা, সে বিষয়ে পুণ্য কোথায়? কোন বিষয় বা ঘটনা না দেখিয়াও বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু একেবারেই না বুঝিয়া বিশ্বাস করে কিরূপে? যাজক যখন দৃঢ়কন্ঠে ঘোষণা করেন যে, না দেখিয়া এমনকি না বুঝিয়াই ঐ সকল বিশ্বাস করিতে হইবে, তখন মনে বিশ্বাস না জন্মিলেও পাপের ভয়ে অথবা জাতীয়তা রক্ষার জন্য মুখে বলা হয়, “আচ্ছা”। বর্তমানকালের অধিকাংশ লোকেরই ধর্মে বিশ্বাস এই জাতীয়।
এই যে জ্ঞানের অগ্রগতিতে বাধা, মনের অদম্য স্পৃহায় আঘাত, আত্মার অতৃপ্তি, ইহারই প্রতিক্রিয়া — মানুষের ধর্ম-কর্মে শৈথিল্য। এক কথায় — মন যাহা চায়, ধর্মের কাছে তাহা পায় না। মানুষের মনের ক্ষুধা অতৃপ্তই থাকিয়া যায়। ক্ষুধার্ত বলদ যেমন রশি ছিঁড়িয়া অন্যের ক্ষেতের ফসলে উদরপূর্তি করে, মানুষের মনও তেমন ধর্ম-ক্ষেত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ছুটিয়া যায় দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।
ধর্মের মূল ভিত্তি বিশ্বাস (ঈমান)। ধর্ম এই বিশ্বাসকেই আঁকড়াইয়া আছে। কিন্তু এই বিশ্বাস কি বা ইহা উৎপত্তির কারণ কি, ধর্ম তা অনুসন্ধান করে না। এই বিশ্বে যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, নিশ্চয়ই তাহার উপাদান বা কারণ আছে। বিশ্বাস জন্মিবার যে কারণসমূহ বর্তমান আছে, পণ্ডিতেরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখাইয়াছেন। বিশ্বাস উৎপত্তির কারণাবলী সূক্ষরূপে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, মনোবিজ্ঞানের যে কোন পুস্তকে উহা পাওয়া যাইবে। আমরা শুধু মোটামুটিরূপে উহার কিঞ্চিৎ আভাস দিব।
জ্ঞানের সহিত বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক। বরং বলা হইয়া থাকে যে, জ্ঞানমাত্রেই বিশ্বাস। তবে যে কোন বিশ্বাস জ্ঞান নহে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর যে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই জ্ঞান বলা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাই খাঁটি বিশ্বাস। পক্ষান্তরে যে বিশ্বাস কল্পনা, অনুভূতি, ভাবানুষঙ্গ বা কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা জ্ঞান নহে। তাহাকে অভিমন (Opinion) বলা হইয়া থাকে। চলতি কথায় ইহার নাম ‘অন্ধ-বিশ্বাস’। সচরাচর লোকে এই অন্ধ-বিশ্বাসকেই ‘বিশ্বাস’ আখ্যা দিয়া থাকে; কিন্তু যাহা খাঁটি বিশ্বাস, তাহা সকল সময়ই বুদ্ধি ও অভিজ্ঞাতা (Lesson Experience) প্রসূত, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা প্রত্যক্ষ তাহা সর্বদাই বিশ্বাস্য। মানুষ যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করে, তাহা তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই করে এবং যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করে, তাহাই বিশ্বাস করে। আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, স্বকর্ণে যাহা শুনিয়াছি, স্বহস্তে যার স্পর্শ করিয়াছি তাহাতে আমার সন্দেহের অবকাশ কোথায়? যাহা আমাদের প্রত্যক্ষীভূত, তাহাতেই আমাদের অটল বিশ্বাস।
সংসারে এমন বস্তুও আছে, যাহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অথচ সেই সকল বস্তুকে যে আমরা সন্দেহ করি এমনও নহে। অনেক অপ্রত্যক্ষীভূত জিনিস আছে, যাহা আমরা অনুমানের ভিত্তিতেই বিশ্বাস করি। এই যে মানুষের ‘প্রাণশক্তি’, যাহার বলে মানুষ উঠা, বসা, চলাফেরা ইত্যাদি সংসারের নানাপ্রকার কাজকর্ম করিতেছে, তাহা কি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি? করি নাই। কারণ ‘প্রাণ’ মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। প্রাণকে কোনরূপে প্রত্যক্ষ না করিলেও প্রাণের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। কারণ প্রাণ যদিও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে, তবুও ইহার কার্যকলাপ দৈহিক ঘটনারূপে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ‘কার্য থাকিলে তাহার কারণ থাকিতে বাধ্য’ — এই স্বতঃসিদ্ধ যুক্তির বলে আমরা দৈহিক ঘটনাবলীর কারণরূপে প্রাণের অস্তিত্বকে অনুমান করিতেছি এবং বিশ্বাস করিতেছি যে, প্রাণ আছে।
পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুইটির উপর খাঁটি বিশ্বাস বা জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত; যে বিশ্বাসের মূলে প্রত্যক্ষ বা অনুমান নাই, অর্থাৎ যে বিশ্বাসের মূলে জ্ঞানের অভাব,তাহা খাঁটি বিশ্বাস নহে, অন্ধ বিশ্বাস। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আমাদের সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান যাহা বলে, তাহা আমরা অকুন্ঠিত চিত্তে বিশ্বাস করি। কিন্তু অধিকাংশ ধর্ম এবং ধর্মের অধিকাংশ তথ্য অন্ধবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রত্যক্ষ বা অনুমানসিদ্ধ নহে। এই জন্য ধর্মের অনেক কথায় বা ব্যাখ্যায় সন্দেহ থাকিয়া যায়। দ্বিধাহীন চিত্তে ধর্মীয় সকল অনুশাসনকে আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তাই বিজ্ঞানের ন্যায় ধর্মের উপর সকল লোকের অটল বিশ্বাস হয় না। ধর্মকে সন্দেহাতীতভাবে পাইতে হইলে উহাকে অন্ধবিশ্বাসের উপর রাখিলে চলিবেনা, উহা খাঁটি বিশ্বাস অর্থাৎ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।
আজকাল যেখানে-সেখানে শোনা যাইতেছে যে, সংসারে নানা প্রকার জিনিসপত্র হইতে ‘বরকত’ উঠিয়া গিয়াছে। কারণ লোকের আর পূর্বের মত ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস নাই। পূর্বে লোকের ঈমান ছিল, ফলে তাহারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিত। আর আজকাল মানুষের ঈমান নাই, তাই তাহাদের অভাব ঘোচে না। ঈমান নাই বলিয়াই ক্ষেতে আর সাবেক ফসল জন্মে না, ফলের গাছে ফল ধরে না, পুকুরে-নদীতে মাছ পড়ে না। ঈমান নাই বলিয়াই মানুষের উপর খোদার গজবরূপে কলেরা, বসন্ত, বন্যা-বাদল, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি নানা প্রকার বালামুছিবত নাজেল হয়। অথচ মানুষের হুঁশ হয় না। এইরূপ যে নানা প্রকার অভাব-অভিযোগের জন্য ঈমানের অভাবকেই দায়ী করা হয় তাহা কতটুকু সত্য?
শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, আর যাহারা জানেন না তাহারা অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন যে, আমাদের এই সোনার বাংলার চাষীগণ বিঘাপ্রতি বার্ষিক যে পরিমাণ ধান্য জন্মাইতেছে, তাহার প্রায় সাত-আটগুণ পরিমাণ ধান্য জাপানের চাষীরা জন্মাইতেছে। হয়ত অনুসন্ধান করিলে ইহাও জানা যাইতে পারে যে, জাপানের এই চাষীরা অ-মুসলমান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, কাফের, যাহাদের ধর্মে ঈশ্বরের নামগন্ধও নাই। আমাদের মতে উহারা বে-ঈমান বা অ-বিশ্বাসী। তবুও উহারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে পূর্বের চেয়ে বেশী ফসল জন্মাইতেছে। আমাদের মতে উহারা বে-ঈমান হইলেও তাহাদের ক্ষেতের ফসল বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই।
কিছুদিন পূর্বে রাশিয়া-প্রত্যাগত বাংলাদেশের জনৈক নামজাদা ডাক্তার সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব বাংলায় প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারীর প্রকোপে প্রাণ হারায় — একথা সেদেশের ডাক্তারেরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। কারণ তাহারা একথা ভাবিতেও পারিতেছিলেন না যে, বর্তমান যুগেও কোন দেশে কলেরা বা বসন্তে ভুগিয়া অগণিত মানুষ প্রাণ হারায়। তবে কি একমাত্র বাংলার অধিবাসীদেরই ঈমান নাই? আর একমাত্র ইহাদের উপরই কি খোদার গজব বর্ষিত হয়? রাশিয়ানরা অধিকাংশই সাম্যবাদী (Socialist)। তাঁহারা দেব-দেবী বা আল্লাহ-নবীর ধার ধারেন না। তবু যাবতীয় কাজে তাঁহারা বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগ করিয়াই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিতেছেন।
যাহারা ঈমানের অভাবকে নানাবিধ অভাব-অনটনের জন্য দায়ী করেন, তাঁহারা একটু ভাবিলেই দেখিতে পাইতেন যে, ধনী ও গরীবের আয়-ব্যয়ের ধাপগুলি কোন কালেই এক নহে। গরীব চায় শুধু ভাত ও কাপড়। কিন্তু ধনী চায় তৎসঙ্গে বিলাস-ব্যসন। মানুষ সাধারণত অনুকরণপ্রিয়। তাই ধনীর বিলাসিতা বহুল পরিমাণে ঢুকিয়াছে গরীবের ঘরে। যাহার পিতার সম্পত্তি ছিল পাঁচ বিঘা জমি এবং পরিবারে ছিল তিনজন লোক, তাহার সংসারের নানা প্রকার খরচ নির্বাহ করিয়াও হয়ত কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত। আজও সে ঐ জমির আয় দ্বারা তিনজন লোকই প্রতিপালন করে, কিন্তু উদ্বৃত্ত যাহা থাকিত, তাহা ব্যয় করিতেছে সাবান, সুবাসিত তৈল, সিল্কের চাদর, ছাতা ও জুতায়। বিলাস-ব্যসনে যে অতিরিক্ত খরচ সে করিতেছে, তাহার হিসাব রাখে না, ভাবে ‘বরকত’ গেল কোথায়? একথা সে ভাবিয়া দেখে না যে, অমিতব্যয়িতা এবং বিলাসিতাই তাহার অভাব-অনটনের কারণ। অযথা ঈমানের অভাবকে কারণ বলিয়া দায়ী করে।
প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে যেখানে (অখণ্ড ভারতে) জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২৯ কোটি, বৃদ্ধি পাইয়া আজ সেখানে জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৬৮ কোটি। এই যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ৩৯ কোটি মানুষ, ইহারা খায় কি? লোকবৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যবৃদ্ধি না হইলে খাদ্য-খাদকের সমতা থাকিবে কিরূপে? লোকবৃদ্ধি যতই হোক, জমিবৃদ্ধির উপায় নাই। কাজেই অনাবাদী জমি আবাদ, উপযুক্ত সার প্রয়োগ, উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষাবাদ ছাড়া বর্তমানে খাদ্যবৃদ্ধির উপায় নাই। অথচ আমাদের দেশে কয়জন চাষী এ বিষয়ে সচেতন? আজও সরকারী বীজ ভাণ্ডারে ভাল বীজ বিকায় না। এমোনিয়া সালফেট ও বোনমিল বস্তা ছিঁড়িয়া পড়িয়া থাকে গুদামের মেঝেয়, রেড়ির খৈল পচিয়া থাকে গুদামে। পল্লী অঞ্চলে ইতস্তত ঝোপ-জঙ্গলের অভাব নাই। বসত বাড়ীর আনাচে-কানাচে জন্মিয়া থাকে ভাইট গাছ আর গুড়ি কচু। বেড়পুকুরে কচুরিপানা ঠাসা। বৃদ্ধি পাইয়াছে শুধু মশা, মাছি, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত আর ডাক্তারের খরচ। এই তো আমাদের অশিক্ষিত দেশের অবস্থা। বর্তমানে খাদ্যের অভাব ঘটিয়াছে তাহা সত্য। কিন্তু ইহা খাদ্য-খাদকের সমতার অভাবেই ঘটিয়াছে, ‘বে-ঈমান’ বা অবিশ্বাসের জন্য নয়।
ম্যালথুস (Malthus) তাঁহার ‘পপুলেশন’ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অনুপাত আছে, যে অনুপাত জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। তবে দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসাধারণের আহার-বিহার এবং রীতি-নীতির তারতম্যে সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে।
আমাদের দেশের জন্মহার অত্যধিক। জনসংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে — শিশু, বিধবা ও বহুবিবাহে। যে ছেলের ২০ বৎসর বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত, সে ছেলের ঐ বয়সে ছেলে-মেয়ে জন্মে দুই-তিনটি। আবার তিন বৎসর বয়সে যে মেয়ের বিবাহ হয়, বারো-তেরো বৎসর বয়সে সে হয় মেয়ের মা। কথায় বলে — ‘কচি ফলের বীজ ভাল না’। অপ্রাপ্তবয়ষ্ক পিতা-মাতার সন্তান উৎপাদনে পিতা-মাতা ও শিশু উভয়ই হয় স্বাস্থ্যহীন। পিতার বয়স ত্রিশ হইলে চুল পাকে, পঁয়ত্রিশে দাঁত নড়ে, চল্লিশে হয় কুঁজো, হাঁপানি ও প্রবাহিকায় পঞ্চাশেই ভবলীলা সাঙ্গ করে। এমতাবস্থায় বিধবা স্ত্রীর উপায় কি? কোন ছেলের ব্যথার ব্যারাম, কোন ছেলের জীর্ণজ্বর, ছোট মেয়েটি কোলে লয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা। এইরূপ স্বাস্থ্যহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দেশের অভাব দৈনন্দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। আর ইহার সাথে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অলসতা ও কুসংস্কার প্রভৃতি তো আছেই। সুখের বিষয় এই যে সরকারী নির্দেশে শিশু-বিবাহ বর্তমানে কমিয়াছে।
বহুবিবাহের প্রতিক্রিয়াও সমাজজীবনে কম নহে। ইহা শুধু বংশবিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। ইহার ফলে নানা প্রকার পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি হয়। বৈমাত্রেয় সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির ফলে উহাদের মধ্যে ফরায়েজের অংশ লইয়া মনোমালিন্য, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অবশেষে মামলা-মোকাদ্দমা ও উকিল-মোক্তার, আমলা-পেশকার ইত্যাদির হয় আয়বৃদ্ধি।
জন্মবৃদ্ধির সাথে সাথে মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যুতেও নিস্তার নাই, ইহাতেও খরচ আছে। প্রথমত জানাজা, কাফন ইত্যাদির খরচ তো আছেই, তদুপরি মোর্দাকে গোর-আজাব হইতে রক্ষা করিতে, পোলছিরাত পার করিতে, বেহেস্ত সহজলভ্য করিতে — প্রতি বৎসর রমজান মাসে মৌলুদ শরীফ, কোরান শরীফ খতম ইত্যাদি না-ই হোক, অন্ততপক্ষে কয়েকজন মোল্লা-মৌলবী ডাকিয়ে তসবিহ পড়াইয়া কিছুটা ডাল-চাল খরচ না করিলেই চলে না। মানুষের অভাববৃদ্ধির কারণাবলীর প্রতি চক্ষু মুদিয়া থাকিয়া উগ্রবিশ্বাসীরা ঈমানের অভাবকেই অভাব-অনটনের কারণ বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছে।
“এখন আর মানুষের মনে পূর্বের ন্যায় ঈমান নাই” — একথা বলিয়া যাঁহারা রোদন করেন, তাঁহারা একটু ভাবিয়া দেখিতে পারেন যে, বিশ্বাস গেল কোথায়? বিজ্ঞানমতে — পদার্থের ধ্বংস নাই, আছে শুধু পরিবর্তন। দেখা যায়, তদ্রূপ মানবমনের বিশ্বাসেরও লয় নাই, আছে শুধু পরিবর্তন। পূর্বে লোকে নানা প্রকার উপকথা, রূপকথায়ও বিশ্বাস করিত। কিন্তু এখন আর তাহা করে না। নানা প্রকার ভূতের গল্প, জ্বীন-পরীর কাহিনী, নানা প্রকার তন্ত্র-মন্ত্রে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেই আজকাল আর বিশ্বাস করেন না। তবে যে উহা সমাজে একেবারেই অচল, তাহা নহে। ‘রূপকথা’ লোকে রূপকথা বলিয়াই গ্রহণ করিতেছে, ‘সত্য’ বলিয়া মনে করিতেছে না। এক সময় উপন্যাসকে লোকে ইতিহাস মনে করিত। কিন্তু এখন আর তাহা করে না, ম্যাজিকের আশ্চর্য খেলাগুলি সকলেই আগ্রহের সহিত দেখে, কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না। তাই বলিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিশ্বাস মুছিয়া যায় নাই। যেমন কতক বিষয় হইতে বিশ্বাস উঠিয়া গিয়াছে, তেমন কতক বিষয়ে বিশ্বাস জন্মাইয়াছে, বিশ্বাসযোগ্য ‘বস্তু’ বা ‘বিষয়’-এর পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র।
বলা হয় যে, আল্লাহতা’লার অসাধ্য কোন কাজ নাই। বিশেষ বিশ্বাসী ভক্তদের অনুরোধে তিনি অসম্ভবকেও সম্ভব করেন। হযরত সোলায়মান নবী নাকি সিংহাসনে বসিয়া সপারিষদ শুন্যে ভ্রমণ করিতেন। তাই বলিয়া — ‘আল্লাহতা’লা ইচ্ছা করিলে জায়নামাজশুদ্ধ আমাকেও নিমেষের মধ্যে মক্কায় পৌঁছাইতে পারেন’ — এইরূপ বিশ্বাস কোন কোন পীর ছাহেবের আছে কি? থাকিলে একবারও তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কি? না দেখিয়াই বা উড়োজাহাজে চড়িবার কারণ কি? উড়োজাহাজে চড়িবার বিপদ আছে, ভাড়া আছে, আর সময়ও লাগে যথেষ্ট। তবুও উহার উপর জন্মিয়াছে বিশ্বাস।
অতীতে কোন কোন বোজর্গান হাঁটিয়াই নদী পার হইতে পারিতেন। যেহেতু তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, নদী পার করাইবেন আল্লাহতা’লা, নৌকা বা জলযানের প্রয়োজন নাই। আর বর্তমানে খোদার উপর বিশ্বাস নাই, নদী পার হইতে সাহায্য লইতে হয় নৌকার।
সুফীগণ নাকি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পৃথিবীর কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহা জানিতে ও দেখিতে পাইতেন। এখন কয়টি লোকে উহা বিশ্বাস করে? বর্তমানে বিশ্বাস জন্মিয়াছে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও এবং টেলিভিশনে।
শাহ ছাহেবদের ‘কালাম’-এর তাবিজে কৃমি পড়ে না, কৃমি পড়ে স্যান্টেনাইন সেবনে। মানত-শিন্নিতে জ্বর ফেরে না, জ্বর ফেরাইতে সেবন করিতে হয় কুইনাইন। লোকে বিশ্বাস করিবে কোনটি? নানাবিধ রোগারোগ্যের জন্য পীরের দরগাহ হইতে হাসপাতালকেই লোকে বিশ্বাস করে বেশী। গর্ভিনীর সন্তান প্রসব যখন অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে, তখন পানিপড়ার চেয়ে লোকে বেবী ক্লিনিকের (Baby Clinic) উপর ভরসা রাখে বেশী।
আজ মহাসমুদ্রের বুকে লোক যাতায়াত করে কোন বিশ্বাসে? সমুদ্রের গভীর জলের নীচে লোকে সাবমেরিন চালায় কোন বিশ্বাসে? মহাকাশ পাড়ি দেয় লোকে কোন বিশ্বাসে? যন্ত্রে বিশ্বাস আছে বলিয়াই মানুষ যন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছে। দ্রব্যগুণে বিশ্বাস আছে বলিয়াই লোকে কলেরা বসন্তের সময় দোয়া-কালামের পরিবর্তে ইনজেকশন ও টিকা লইতেছে।
পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিশ্বাস ধরাপৃষ্ঠ হইতে অবলুপ্ত হয় নাই, শুধু বিশ্বাসযোগ্য বিষয়-বস্তুর পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, যেখানে যে বিষয়ে মানুষের জ্ঞান জন্মিতেছে, সেইখানেই বিশ্বাস (ঈমান) দৃঢ়তর হইতেছে; আর যেখানে যে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে নাই, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয় হইতে ক্রমশ বিশ্বাস লোপ পাইতেছে। অর্থাৎ সন্দেহ জাগিতেছে। যে কথার বা যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রমাণ নাই, যে বিষয়ের কার্য-কারণ সম্পর্ক নাই বা যাহা বিবেকবিরোধী, বর্তমানে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই সে সকল ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না।
ধর্মজগতে এমন কতগুলি বিধি-নিষেধ, আচার-অনুষ্ঠান ও ঘটনাবলীর বিবরণ পাওয়া যায়, যাহার যুক্তিযুক্ত কোন ব্যাখ্যা সাধারণের বোধগম্য নহে। তাই সততই মনে কতগুলি প্রশ্ন উদয় হয় এবং সেই প্রশ্নগুলির সমাধানের অভাবে ধর্মের বিধি-বিধানের উপর লোকের শৈথিল্য ঘটে। ধর্মযাজকদের অধিকাংশের নিকটই সেই সকল প্রশ্নাবলীর সদুত্তর পাওয়া যায় না। অনেক সময় উত্তর দেওয়া দূরে থাক, শুধু প্রশ্ন করার জন্য উল্টা কাফেরী ফতোয়া দিতেও তাহাদের দেরী হয় না। অথচ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদী তাহাদের মতানুযায়ী পালন না করিলে তাহার উপর তাহারা সাধ্যমতো দল বাঁধিয়া অত্যাচার করিতেও ইতস্তত করে না। ধর্মের নাম করিয়া ধর্মবিরোধী কাজ করিতেও উহাদের বাধে না। পবিত্র কোরান যে — “লা ইকরাহা ফিদ্দীন”, অর্থাৎ ধর্মে জবরদস্তি নাই — সেদিকে উহারা ভ্রুক্ষেপ করে না। অধিকন্তু সরকারী আইন বাঁচাইয়া যতদূর ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় তাহা করিতেও ত্রুটি করে না। উপরন্তু রাজশক্তিকে হস্তগত করিয়া ধর্মের নামে অধর্মকে চালাইবার আকাশ-কুসুমও উহারা রচনা করিতেছে।
ধর্মরাজ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিলে সাধারণত মনে যে সকল প্রশ্নের উদয় হয়, আমরা এখন তাহার কতগুলি প্রশ্ন বিবৃত করিব এবং প্রশ্নগুলি কেন হইতেছে, তাহার হেতুস্বরূপ যথাযোগ্য ব্যাখ্যা প্রশ্নের সহিত সন্নিবেশিত করিব।
প্রথম প্রস্তাব
[আত্মা বিষয়ক]
১। আমি কে?
মানুষের আমিত্ববোধ যত আদিম ও প্রবল, তত আর কিছুই নাই। আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি বাঁচিয়া আছি, আমি মরিব ইত্যাদি হাজার হাজার রূপে আমি আমাকে উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু যথার্থ ‘আমি’ — এই রক্ত-মাংস-অস্থি-মেদ-মজ্জায় গঠিত দেহটিই কি ‘আমি’? তাহাই যদি হয় তবে মৃত্যুর পরে যখন দেহের উপাদানসমূহ পচিয়া-গলিয়া অর্থাৎ রাসায়নিক পরিবর্তনে কতগুলি মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হইবে, তখন কি আমার আমিত্ব থাকিবে না? যদি তাহাই হয় তবে আত্মাকে ‘আমি’ না বলিয়া ‘আমার’ — ইহা বলা হয় কেন? যখন কেহ দাবী করে যে দেহ আমার প্রাণ আমার এবং মন আমার, তখন দাবীদারটি কে?
২। প্রাণ কি অরূপ না সরূপ?
প্রাণ যদি অরূপ বা নিরাকার হয়, তবে দেহাবসানের পরে বিশ্বজীবের প্রাণসমূহ একত্র হইয়া একটি অখণ্ড সত্তা বা শক্তিতে পরিণত হইবে না কি? অবয়ব আছে বলিয়াই পদার্থের সংখ্যা আছে, নিরবয়ব বা নিরাকারের সংখ্যা আছে কি? আর সংখ্যা না থাকিলে তাহার স্বাতন্ত্র্য থাকে কি? পক্ষান্তরে প্রাণ যদি সরূপ বা সাকার হয়, তবে তাহার রূপ কি?
৩। মন ও প্রাণ কি এক?
সাধারণত আমরা জানি যে, মন ও প্রাণ এক নহে। কেননা উহাদের চরিত্রগত পার্থক্য বিদ্যমান। আমরা আমাদের নিজেদের উপলব্ধি হইতে জানিতে পাইতেছি যে, ‘মন’ প্রাণের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু ‘প্রাণ’ মনের উপর নির্ভরশীল নয়। মন নিষ্ক্রিয় থাকিলেও প্রাণের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু প্রাণ নিষ্ক্রিয় হইলে মনের অস্তিত্বই থাকে না। যেমন — ক্লোরোফরম প্রয়োগে মানুষের সংজ্ঞা লোপ ঘটে, অথচ দেহে প্রাণ থাকে, শ্বাসক্রিয়া, হৃৎক্রিয়া এমনকি পরিপাকক্রিয়াও চলিতে থাকে। অথচ তখন আর মনের কোন ক্রিয়াই প্রকাশ পায় না। গভীর সুনিদ্রাকালেও কোন সংজ্ঞা থাকে না, ইহা দৈনন্দিন ঘটনা। কিন্তু সংজ্ঞাহীন হইলেই দেহ নিষ্প্রাণ হয় না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রাণবিহীন মন থাকিতেই পারে না, কিন্তু মন বা সংজ্ঞাহীন প্রাণ অনেক সময়ই পাওয়া যায়, ইহাতে অনুমিত হয় যে, মন আর প্রাণ এক নহে। ইহাও অনুমিত হয় যে, সংজ্ঞা, চেতনা বা সুখ-দুঃখের অনুভূতি মনেরই, প্রাণের নয়। প্রাণ রাগ, শোক, ভোগ ও বিলাসমুক্ত। এক কথায় প্রাণ চিরনির্বিকার।
জীবের জীবন নাকি যমদূত (আজরাইল) হরণ করেন। কিন্তু তিনি কি প্রাণের সহিত মনকেও হরণ করেন? অথবা প্রাণ যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, মনকে তৎসঙ্গে থাকিতেই হইবে — এইরূপ কোন প্রমাণ আছে কি? নতুবা মনবিহীন প্রাণ পরকালের সুখ-দুঃখ ভোগ করিবে কিরূপে?
৪। প্রাণের সহিত দেহ ও মনের সম্পর্ক কি?
দেহ জড় পদার্থ। কোন জীবের দেহ বিশ্লেষণ করিলে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, লৌহ, ফসফরাস ইত্যাদি নানা প্রকার মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন অনুপাতে অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। পদার্থসমূহ নিষ্প্রাণ। কাজেই পদার্থসমূহের যথানুপাতে সংমিশ্রিত অবস্থাকেই প্রাণ বলা যায় না। পদার্থসমূহের যথানুপাতে সংমিশ্রণ এবং আরও কিছুর ফলে দেহে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায়। ঐ ‘আরও কিছু’কে আমরা মন বলিয়া থাকি। কিন্তু মানুষের দেহ, মন ও প্রাণে কিছু সম্পর্ক বা বন্ধন আছে কি? থাকিলে তাহা কিরূপ? আর না থাকিলেই বা উহারা একত্র থাকে কেন?
৫। প্রাণ চেনা যায় কি?
কোন মানুষকে ‘মানুষ’ বলিয়া অথবা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে আমরা তাহার রূপ বা চেহারা দেখিয়াই চিনিতে পাই, প্রাণ দেখিয়া নয়। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সকলকে রূপ দেখিয়াই চিনি, সম্বোধন করি, তাহাদের সাথে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম নিষ্পন্ন করি। প্রাণ দেখিয়া কাহাকেও চিনিবার উপায় নাই। তদ্রুপ — পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা ইত্যাদিকে আমরা উহাদের রূপ দিখিয়াই চিনিয়া থাকি। এই রূপ বা চেহারা দেহীর দেহেই প্রকাশ পাইয়া তাকে। যখন দেহের সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক থাকিবে না অর্থাৎ মৃত্যুর পরে দেহহীন প্রাণকে চিনিবার উপায় কি? বিভিন্ন ব্যক্তি বা জীবের মন, জ্ঞান ও দৈহিক গঠনে যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, উহাদের প্রাণেও কি তেমন বৈচিত্র্য আছে? অর্থাৎ বিভিন্ন জীবের প্রাণ কি বিভিন্নরূপ?
৬। আমি কি স্বাধীন?
‘আমি’ মনুষ্যদেহধারী মনপ্রাণবিশিষ্ট একটি সত্তা। প্রাণশক্তিবলে আমি বাঁচিয়া আছি, মনে নানা প্রকার কার্য করিবার স্পৃহা জাগিতেছে এবং দেহের সাহায্যে কার্যাবলী নিষ্পন্ন করিতেছি। আমি যে শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী, তাহা আমার কার্যাবলীর মধ্যেই প্রকাশ পাইতেছে।
কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই যে, আমি স্বাধীন কি-না। যদি আমি স্বাধীন হই অর্থাৎ আমার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ঈশ্বরের না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার ‘সর্বশক্তিমান’ নামের সার্থকতা কি? আর যদি আমি স্বাধীন না-ই হই, আমার কার্যাবলীর ফলাফলস্বরূপ পাপ বা পুণ্যের জন্য আমি দায়ী হইব কিরূপে?
৭। অশরীরী আত্মার কি জ্ঞান থাকিবে?
মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কোন একটির অভাব থাকিলে, ঐ ইন্দ্রিয়টির মাধ্যমে যে জ্ঞান হইতে পারিত,তাহা আর হয় না। যে অন্ধ বা বধির, সে আলো বা শব্দে জ্ঞান পাইতে পারে না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অভাবে জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। মৃত্যুতে মানুষের দেহ নষ্ট হয় এবং তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিও নষ্ট হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, মৃত্যুর পরে শরীর ও ইন্দ্রিয়বিহীন আত্মার জ্ঞান থাকিবে কি? থাকিলে তাহা কিরূপে থাকিবে?
৮। প্রাণ কিভাবে দেহে আসা-যাওয়া করে?
কেহ কেহ বলেন যাবতীয় জীবের বিশেষত মানুষের প্রাণ একই সময় সৃষ্টি হইয়া ‘ইল্লিন’ নামক স্থানে রক্ষিত আছে। তথা হইতে রমণীদের গর্ভের তৃতীয় কি চতুর্থ মাসে প্রাণ ভ্রূণে আবির্ভূত হয়। গর্ভস্থ শিশুর দেহে আল্লাহতা’লার হুকুমে প্রাণ নিজেই আসে, না কোন ফেরেস্তা প্রাণকে শিশুর দেহে ভরিয়া দিয়া যায়, তাহা জানি না; কিন্তু ধর্মাধ্যায়ীগণ ইহা নিশ্চিত করিয়াই বলেন যে, একটি জীবের দেহে একটি প্রাণই আমদানী হয়। ইহা কেহ কখনও বলেন না যে, একটি জীবের একাধিক প্রাণ থাকিতে পারে বা আছে। ‘পঞ্চপ্রাণ’ বলিয়া যে একটি বাক্য আছে, যথা — প্রাণ, আপ্রাণ, সমান, উদান ও ধ্যান—উহা হইল শরীরস্থ বায়ুর পাঁচটি অবস্থা মাত্র। প্রাণশক্তি একই।
সচরাচর এক গর্ভে মানুষ জন্মে একটি। কিন্তু বিড়াল, কুকুর, ছাগ ও শৃগালাদি প্রায়ই একাধিক জন্মিয়া থাকে। মানুষেরও যমজ সন্তান হওয়া চলতি ঘটনা, ক্বচিৎ চারি-পাঁচ বা ততোধিক সন্তান জন্মিবার কথাও শোনা যায়। ঐ সকল ক্ষেত্রে কি প্রতি গর্ভে একাধিক প্রাণ আমদানী হয়, না একটি প্রাণই বিভক্ত হইয়া বহুর সৃষ্টি হয়?
কেঁচো ও শামুকাদি ভিন্ন যাবতীয় উন্নত জীবেরই নারী-পুরুষ ভেদ আছে, ক্বচিৎ নপুংসকও দেখা যায়। কিন্তু জীবজগতে নারী ও পুরুষ, এই দুই জাতিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রতিটি জীব বা মানুষ জন্মিবার পূর্বেই যদি তাহার স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট প্রাণ সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই প্রাণেও লিঙ্গভেদ আছে কি? যদি থাকেই, তাহা হইলে অশরীরী নিরাকার প্রাণের নারী, পুরুষের চিহ্ন কি? আর যদি প্রাণের কোন লিঙ্গভেদ না থাকে, তাহা হইলে এক জাতীয় প্রাণ হইতে ত্রিজাতীয় প্রাণী জন্মে কিরূপে? লিঙ্গভেদ কি শুধু জীবের দৈহিক রূপায়ণ মাত্র? তাহাই যদি হয়, তবে পরলোকে মাতা-পিতা, ভাই-ভগিনী ইত্যাদি নারী-পুরুষভেদে থাকিবে কিরূপে? পরলোকেও কি লিঙ্গজ দেহ থাকিবে?
প্রকৃতির নিয়মানুসারে কোন জীবের দেহে প্রাণ না থাকিলে সে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। বরং নির্জীবদেহ জৈবধর্ম হারাইয়া জড় পদার্থের ধর্ম পায় এবং তাহা নানারূপ রসায়নিক পরিবর্তের ফলে রূপান্তর গ্রহণ করে। অর্থাৎ পচিয়া-গলিয়া নষ্ট হইয়া যায়। মাতৃগর্ভস্থ মানবশিশু যদি তিন-চারি মাস বয়সের সময়ে প্রাণপ্রাপ্ত হয়, তবে সে মাতা-পিতার মিলন মুহুর্তের পর হইতে নিষ্প্রাণ (ভ্রূণ) অবস্থায় বৃদ্ধি পায় কেন এবং পচিয়া-গলিয়া নষ্ট হইয়া যায় না কেন? প্রাণের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন কোন বৃক্ষের একটি হইতে দশটি শাখা কাটিয়া রোপন করিলে তাহা হইতে পৃথক পৃথক দশটি জীবিতবৃক্ষের উৎপত্তি হয়। এই রোপিত দশটি বৃক্ষের যে দশটি স্বতন্ত্র জীবন, উহা কোথা হইতে, কোন সময়, কিভাবে আসে? স্বর্গ হইতে কোন দূতের মারফতে, না পূর্ব বৃক্ষ হইতে?
সদ্য বধ করা গরু, মহিষ বা ছাগলাদির কাটা মাংস যাহারা স্বহস্তে নাড়া-চাড়া করিয়াছেন, তাহারা কেহ কেহ হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, কতগুলি খণ্ডিত মাংস আঘাতে সাড়া দেয়। যে জন্তুটিকে বধ করিবার পর উহার দেহ শত শত খণ্ডে খণ্ডিত করা হয়, উহার মাংসখণ্ডগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিয়া আঘাতে সাড়া দেয় বা স্পন্দিত হয় কেন? কোন রকম আঘাতে সাড়া দেওয়াটি জীবন বা জীবিতের লক্ষণ, কিন্তু মৃত প্রাণীর মাংসখণ্ডে জীবন কোথা হইতে আসে? কোন জীবের জীবন যমদূত হরণ করিয়া লওয়ার পরেও কি প্রাণের কিছু অংশ জীবদেহে থাকিতে পারে? আর থাকিলেও কি একটি প্রাণের শত শত খণ্ডে খণ্ডিত হওয়া সম্ভব?
জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রাণীদেহ কতগুলি জীবকোষ (Cell)-এর সমবায়ে গঠিত। জীবকোষগুলি প্রত্যেকে জীবন্ত। অর্থাৎ প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে জীবিত। সাপ, কেঁচো, টিকটিকি ইত্যাদির লেজ কাটিয়া ছিড়িয়া ফেলিলে, তাহা দেহ হইতে দূরে পড়িয়াও লাফাইতে থাকে। এক্ষেত্রে জন্তুটির একটি প্রাণ দুইস্থানে থাকিয়া নড়াচড়া করিতেছে না। লেজস্থিত জীবকোষগুলি স্বতন্ত্র জীবনের কিছু সময় বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তেমন স্বতন্ত্রভাবে মরিতেও পারে। মানুষের খোস, পাঁচড়া, দাদ ইত্যাদি এবং কতিপয় ক্ষতরোগ আরোগ্য হইলে রুগ্নস্থান হইতে যে মর্যমাস (মৃত চর্মের ফুস্কুড়ি) উঠিয়া থাকে, উহাই জীবকোষের স্বতন্ত্র মৃত্যুর নিদর্শন। ইহা ভিন্ন যে কোন জীবিত বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার মৃত্যুতেও জীবকোষের স্বতন্ত্র মৃত্যু সূচিত করে।
একটি জীবকোষ বিভাজন প্রণালীতে দুইটিতে, দুইটি হইতে চারিটি এবং তাহা হইতে আটটিতে পরিণত হয়। এইরূপ ক্রমান্বয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর সৃষ্টি হয়। মানুষের বেলায়ও একটি মাত্র ডিম্বকোষ (Egg cell) আর একটি জননকোষ (Germ cell) একত্র মিলিত হইয়া বিভাজন প্রণালীতে সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে বহু কোটি জীবকোষের সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়। একটি মানুষের প্রাণ বহু কোটি প্রাণের সমবায়ী শক্তি। আমরা উহার নাম দিতে পারি ‘মহাপ্রাণ’। কাজেই একটি জন্তুর দেহে প্রাণ ‘বহু’ কিন্তু মহাপ্রাণ ‘একটি’। জীবদেহের যাবতীয় জীবকোষের এককালীন মৃত্যুকে অর্থাৎ মহাপ্রাণের তিরোধানকে আমরা জীবের ‘মৃত্যু’ বলি এবং জীবদেহের কোন অংশের জীবকোষের মৃত্যুকে বলি ‘রোগ’।
উপরোক্ত ধর্মীয় ও জীবতত্ত্বীয় মতবাদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য কোনটি?
দ্বিতীয় প্রস্তাব
[ঈশ্বর বিষয়ক]
১। আল্লাহর রূপ কি?
জগতের প্রায় সকল ধর্মই একথা স্বীকার করে যে, ঈশ্বর অদ্বিতীয়, নিরাকার ও সর্বব্যাপী। কথা কয়টি অতীব সহজ ও সরল। কিন্তু যখন হিন্দুদের মুখে শোনা যায় যে, সৃষ্টি পালনের উদ্দেশ্যে ভববান মাঝে মাঝে সাকারও হইয়া থাকেন ও যুগে যুগে ‘অবতার’রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া লীলা প্রকাশ করেন এবং যখন খৃষ্টানদের নিকট শোনা যায় যে পরম সত্তা — ‘ভগবান, মশীহ, পরমাত্মা’ — এই ত্রিত্বে প্রকাশ পাইতেছে; আবার যখন মুসলিম ধর্মযাজকদের নিকট শোনা যায় যে আল্লাহতা’লা আরশে ‘কুরছি’র উপর বসিয়া রেজোয়ান নামক ফেরেস্তার সাহায্যে বেহেস্ত, মালেক নামক ফেরেস্তার সাহায্যে দোজখ, জেব্রাইলের সাহায্যে সংবাদ এবং মেকাইলকে দিয়া খাদ্য বন্টন ও আবহাওয়া পরিচালনা করেন — তখনই মন ধাঁধায় পড়ে, বুদ্ধি বিগড়াইয়া যায়। মনে প্রশ্ন জাগিতে থাকে — নিরাকার সর্বশক্তিমান ভগবানের সৃষ্টি পালনে সাকার হইতে হইবে কেন? অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মহত্ত্ব প্রকাশে ত্রিত্বের আবশ্যক কি? সর্বব্যাপী আল্লাহতা’লার স্থায়ী আসনে অবস্থান কিরূপ এবং বিশ্বজগতের কার্য পরিচালনার জন্য ফেরেস্তার সাহায্যের আবশ্যক কি?
২। খোদাতা’লা কি মনুষ্যভাবাপন্ন?
আল্লাহতা’লা দেখেন, শোনেন, বলেন ইত্যাদি শুনিয়া সাধারণ মানুষের মনে স্বতই প্রশ্ন জাগে — তবে কি আল্লাহর চোখ, কান ও মুখ আছে? কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আছে। তবে তাহা মানুষের মত নয়, কুদরতি। কিন্তু ‘কুদরতি’ বলিতে কিরূপ বুঝায়, তাহা তাঁহারা ব্যখ্যা করেন না। আবার যখন শোনা যায় যে, খোদাতা’লা অন্যায় দেখিলে ক্রুদ্ধ হন, পাপীদের ঘৃণা করেন, কোন কোন কাজে খুশী হন ও কোন কোন কাজে হন বেজার, তখন মানুষ ভাবে — খোদার কি মানুষের মতই মন আছে? আর খোদার মনোবৃত্তিগুলি কি মানুষেরই অনুরূপ? ইহারও উত্তর আসে যে, উহা বুঝিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। আবার যখন চিন্তা করা যায় যে, খোদাতা’লার জগত-শাসন প্রণালী বহুলাংশে একজন সম্রাটের মত কেন এবং তাঁহার এত আমলা-কর্মচারীর বাহুল্য কেন? উহার উত্তর পাওয়া যায় যে, সম্রাট হইলে তিনি অদ্বিতীয় সম্রাট, বাদশাহের বাদশাহ, ক্ষমতা তাঁহার অসীম।
উত্তর যাহা পাওয়া গেল, তাহাতে অসাধারণ যাহাদের মনীষা তাঁহারা হয়ত বুঝিলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ ইহাতে কিছু বুঝিতে পাইল কি?
৩। স্রষ্টা কি সৃষ্ট হইতে ভিন্ন?
ঈশ্বর যদি তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ হইতে ভিন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহার সর্বব্যাপিত্ব থাকিতে পারে না এবং ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব অক্ষুণ্ন থাকিলে কোন সৃষ্ট-পদার্থ এমনকি পদার্থের অণু-পরমাণুও ঈশ্বর-শূন্য হইতে পারে না। অর্থাৎ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই ঈশ্বরময়। মূল কথা — বিশ্ব ঈশ্বরময়, ঈশ্বর বিশ্বময়।
ধর্ম যদিও ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্বে সন্দেহ করে না, কিন্তু একথাও নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে না যে, জগতের যাবতীয় জৈব-অজৈব, পাক এবং নাপাক সকল বস্তুই ঈশ্বরে ভরপুর। বিশ্বাস যদি করিত, তবে নাপাক বস্তুকে ঘৃণা করিবার কারণ কি?
এখন এই উভয়সংকট হইতে ধর্মে বিশ্বাস বাঁচাইয়া রাখার উপায় কি?
৪। ঈশ্বর কি স্বেচ্ছাচারী, না নিয়মতান্ত্রিক?
‘নিয়মতন্ত্র’ হইল কোন নির্ধারিত বিধান মানিয়া চলা এবং উহা উপেক্ষা করাই হইল ‘স্বেচ্ছাচারিতা’। ঈশ্বর স্বেচ্ছাচারী হইলে তাঁহার মহত্ত্বের লাঘব হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক হইলে তিনি তাঁহার ভক্তদের অনুরোধ রক্ষা করেন কিরূপে?
সুপারিশ রক্ষার অর্থই হইল, আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করা। অর্থাৎ স্বয়ং যাহা করিতেন না, তাহাই করা। ঈশ্বর কি কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধ বা সুপারিশে আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবেন না?
৫। আল্লাহ ন্যায়বান না দয়ালু?
অন্যান্য ক্ষেত্রে যাহাই হউক না কেন, বিচারক্ষত্রে ‘ন্যায়’ ও ‘দয়া’র একত্র সমাবেশ অসম্ভব। কেননা দয়া করিলে ন্যায়কে উপেক্ষা করিতে হইবে এবং ন্যায়কে বজায় রাখিতে হইলে দয়ামায়া বিসর্জন দিতে হইবে।
বলা হয় যে, আল্লাহ ন্যায়বান এবং দয়ালু। ইহা কিরূপে সম্ভব? তবে কি তিনি কোন ক্ষেত্রে ন্যায়বান আর কোন ক্ষেত্রে দয়ালু?
৬। আলাহর অনিচ্ছায় কোন ঘটনা ঘটে কি?
বলা হয় যে, আল্লাহর অনিচ্ছায় কোন ঘটনা ঘটে না। এমনকি গাছের পাতাও নড়ে না। বিশেষত তাঁহার অনিচ্ছায় যদি কোন ঘটনা ঘটিতে পারে তাহা হইলে তাঁহার ‘সর্বশক্তিমান’ নামের সার্থকতা কোথায়? আর যদি আল্লাহর ইচ্ছায়ই সকল ঘটনা ঘটে, তবে জীবের দোষ বা পাপ কি?
৭। নিরাকারের সাথে নিরাকারের পার্থক্য কি?
‘আল্লাহ’ নিরাকার এবং জীবের ‘প্রাণ’ও নিরাকার। যদি উভয়ই নিরাকার হয়, তবে ‘আল্লাহ’ এবং ‘প্রাণ’ — এই দুইটি নিরাকারের মধ্যে পার্থক্য কি?
৮। নিরাকার পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় কিভাবে?
ধর্মযাজকদের নিকট শোনা যায় যে, বেহেস্তে বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ (নুর ও আলোরূপে) দর্শন দান করিবেন। যিনি চির অনন্ত, চির অসীম, তিনি কি চির-নিরাকার নহেন?
বিজ্ঞানীদের মতে — স্থূল অথবা সূক্ষ, যে রূপেই হউক না কেন, কোন রকম পদার্থ না হইলে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। আলো একটি পদার্থ। উহার গতি আছে এবং ওজনও আছে। নিরাকার আল্লাহ যদি তাঁহার ভক্তদের মনোরঞ্জনের জন্য নুর বা আলো রূপ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে হিন্দুদের ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশে অর্থাৎ অবতারে দোষ কি?
৯। স্থান, কাল ও শক্তি — সৃষ্ট না অসৃষ্ট?
এ কথা সত্য যে, ‘সৃষ্টিকর্তা’ বলিয়া যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি হইবেন এক ও অদ্বিতীয়। কিন্তু ধর্মজগতে তাঁহাকে চিত্রিত করা হইয়াছে বিবিধ রূপে এবং তাঁহার সংজ্ঞা ও সংখ্যা সব ক্ষেত্রে এক রকম নহে। বিশেষত ধর্মরাজ্যে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় অনেক ক্ষেত্রেই ‘ব্যক্তি’রূপে। বলা হয় যে, ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, অসীম ও নিরাকার; অথচ প্রত্যক্ষ না হইলেও পরোক্ষে তাঁহার চোখ, মুখ ও কান আছে — তাহার আভাস পাওয়া যায় অনেক ক্ষেত্রে। এমনকি তাঁহার পুত্র-কন্যা-পরিবারেরও বর্ণনা পাওয়া যায় কোন কোন ক্ষেত্রে।
সৃষ্টিকর্তা হইলেন — যিনি সৃষ্টি করেন বা করিয়াছেন। কোন সৃষ্ট পদার্থ স্রষ্টার চেয়ে বয়সে অধিক হইতে পারেনা, এমনকি সমবয়সীও না? কোন কুমার একটি হাঁড়ি তৈয়ার করিল, এক্ষেত্রে হাঁড়ি কখনও কুমারের বয়োজ্যেষ্ঠ বা সমবয়সী হইতে পারে না। অর্থাৎ কর্তার আগে কর্ম অথবা কর্তা ও কর্ম একই মুহুর্তে জন্মিতে পারে না, ইহাই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম।
কোন পদার্থের সৃষ্টিকাল যতই অতীত বা মহাতীত হউক না কেন, উহা কখনও অনাদি হইতে পারে না। যাহা ‘সৃষ্টি’ তাহা নিশ্চয় কোন এক সময়ে উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কিন্তু বিশ্বে এমন কোন বিষয় আছে, আমরা যাহার আদি, অন্ত, সীমা ও আকার কল্পনা করিতে পারি না। যেমন — স্থান, কাল ও শক্তি। বলা হইয়া থাকে যে, ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, অসীম ও নিরাকার, পক্ষান্তরে স্থান, কাল এবং শক্তিও অনাদি, অনন্ত, অসীম ও নিরাকার। যথাক্রমে এ বিষয় আলোচনা করিতেছি।
১) স্থান — বিশের দৃশ্যাদৃশ্য যাবতীয় পদার্থই কোন না কোন স্থানে অবস্থিত আছে। ‘স্থান’ (Space) পদার্থপূর্ণ অথবা পদার্থশূন্য, দুইই থাকিতে পারে। কিন্তু ‘স্থান’কে থাকিতেই হইবে।
বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই কোন না কোন সময়ে উৎপত্তি হইয়াছে। এমনকি পবিত্র বাইবেল গ্রন্থে সৃষ্টির দিন-তারিখও দেওয়া আছে। সে যাহা হউক, কোন কিছু বা সব কিছু সৃষ্টির পূর্বে — পদার্থশূন্য থাকিলেও যে ‘স্থান’ ছিল না, তাহা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং বলিতে হয় যে, ‘স্থান অনাদি’।
পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি সৃষ্টি হইয়া কোন ‘স্থান’-এ অবস্থান করিতেছে এবং উহারা বিলয় হইলেও ঐ স্থানসমূহ থাকিবে। কেননা, শুন্যস্থান কখনও বিলয় হইতে পারে না। সুতরাং বলিতে হয় যে, ‘স্থান অনন্ত’।
পরম বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলিয়াছেন, “বিশ্ব অসীম অথচ সসীম”। অর্থাৎ নক্ষত্র-নীহারিকাদির পার্থিব জগত সসীম, কিন্তু ‘স্থান’ অসীম। বিশ্বের ‘শেষ প্রান্ত’ বলিয়া এমন কোন সীমারেখা কল্পনা করা যায় না, যাহার বহিরভাগে আর ‘স্থান’ নাই। সুতরাং ‘স্থান অসীম’।
আমরা দেখিতে বা অনুভব করিতে পারি শুধু পদার্থকে, স্থানকে নয়। স্থান পদার্থের ন্যায় লাল, কালো, সবুজাদি রঙ, লম্বা-চওড়া ইত্যাদি আকৃতিবিশিষ্ট নয়। স্থানের কোন অবয়ব নাই। উহা আকৃতিহীন ও অদৃশ্য। অর্থাৎ নিরাকার।
২) কাল — কাল বা সময়কে আমরা দেখিতে পাই না, দেখিতে পাই শুধু ঘটনাকে। কেহ কেহ বলেন যে ‘কাল’ বা ‘সময়’ নামে কোন কিছু নাই, ‘কাল’ হইল ঘটনা পর্যায়ের ফাঁকমাত্র। সাধারণত কালকে আমরা তিনভাবে বিভক্ত করিয়া থাকি। যথা — ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, ‘বর্তমান’ নামে কোন কালই নাই। কেননা কাল সতত গতিশীল। যাহা গতিশীল তাহার স্থিরতা বা বর্তমানতা অসম্ভব। ভবিষ্যৎ হইতে কাল তীব্রগতিতে আসে এবং নিমেষে অতীতে চলিয়া যায়। এক সেকেণ্ডকে হাজার ভাগ করিলে যে সময়টুকু পাওয়া যায়, সেই সময়টুকু কাল দাঁড়াইয়া থাকে না ‘বর্তমান’ নামে আখ্যায়িত হইবার প্রত্যাশায়। বর্তমান হইল — অতীত এবং ভবিষ্যতের সন্ধিস্থল মাত্র। উহার কোন বিন্দুতেই কাল এতটুকু স্থিত বা বর্তমান থাকে না। তবে আমরা যে বর্তমান যুগ, বর্তমান বৎসর, বর্তমান ঘটনা ইত্যাদি বলিয়া থাকি, উহা হইল — অতীত এবং ভবিষ্যতের সংমিশ্রণ। যাক সে কথা।
ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কোন এক সময়ে কিন্তু ‘সময়’কে সৃষ্টি করিয়াছেন কোন সময়ে, তাহার কোন হদিস পাওয়া যায় না। এরূপ কল্পনা করা মোটেই কষ্টকর নয় যে, এমন একটি সময় ছিল যখন কোনরূপ সৃষ্টিই ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে যে ‘কাল’ ছিল না, তাহা কল্পনা করা যায় না। কাজেই বলিতে হয় যে, কাল ‘অনাদি’। পক্ষান্তরে — মহাপ্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হইবার পর — কাল আর থাকিবে না, তাহাও মানব কল্পনার বাহিরে। সুতরাং বলিতে হয় যে, কাল ‘অনন্ত’।
বিশ্বে, মহাবিশ্বে অথবা আরও বাহিরে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে কাল নাই। কালকে কোনস্থানে সীমিত রাখা যায় না। সুতরাং কাল ‘অসীম’। অধিকন্তু কাল ‘নিরাকার’ও বটে।
৩) শক্তি — ‘শক্তি বলিতে আমরা বুঝি যে, উহা কাজ করিবার ক্ষমতা। শক্তিকে জানিতে বেশী দূর যাইতে হয় না। কেননা উহা আমাদের নিজেদের মধ্যেই আছে, যাহার সাহায্যে আমরা উঠা-বসা, চলা-ফেরা ও নানাবিধ কাজকর্ম করিয়া থাকি। কিন্তু শুধু গায়ের শক্তিতেই সকল রকম কাজ করা যায় না, অন্যান্য রকম শক্তিরও দরকার। গায়ের শক্তিতে কোন কিছু দেখা বা শোনা যায় না, গায়ের জোর থাকা সত্ত্বেও অন্ধ বা বধির ব্যক্তিরা দেখে না বা শোনে না, উহার জন্য চাই দর্শন ও শ্রবণশক্তি। শুধু তাই নয়, আরও অনেক রকম শক্তি আমাদের দরকার এবং উহা আছেও। যেমন — বাকশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, স্পর্শশক্তি, ধীশক্তি, মননশক্তি ইত্যাদি এবং সর্বোপরি জীবনীশক্তি। আমাদের দেহের মধ্যে যেমন রকম-রকম শক্তি আছে, এমন প্রকৃতিরাজ্যেরও নানাবিধ শক্তি আছে; যেমন — তাপশক্তি, আলোকশক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি, রাসায়নিক শক্তি ইত্যাদি।
বস্তুজগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহার মধ্যে কোনরূপ শক্তি নাই। সামান্য একটিও দুর্বাপত্রেরও রোগ নিরাময় করিবার শক্তি আছে। মূল কথা এই যে, এই জগৎটিই শক্তির লীলাখেলা। অর্থাৎ — শক্তি জগৎময় এবং জগৎ শক্তিময়।
বিজ্ঞানী প্রবর আইনস্টাইন বলিয়াছেন যে, ‘পদার্থ’ শক্তির রূপান্তর মাত্র। শক্তি সংহত হইয়া হয় পদার্থের উৎপত্তি এবং পদার্থের ধ্বংসে হয় শক্তির উদ্ভব। কি পরিমাণ শক্তির সংহতিতে কি পরিমাণ পদার্থ এবং কি পরিমাণ পদার্থ ধ্বংসে কি পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হইতে পারে, তাহা তিনি অংকের সাহায্যে দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, একটি মটর পরিমাণ পদার্থকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করিতে পারিলে তাহা হইতে যে শক্তির উদ্ভব হইবে, তাহা দ্বারা বড় রকমের একখানা মালাবাহী জাহাজ চালানো যাইবে লণ্ডন হইতে নিউইয়র্ক পর্যন্ত। আইনস্টাইনের এই সূত্র ধরিয়াই অধুনা হইয়াছে পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, এই জগতে জৈবাজৈব সমস্ত পদার্থই শক্তির রূপান্তর। অর্থাৎ জগতের সব কিছু সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে ‘শক্তি’।
কোনরূপ কাজ করিতে হইলেই আগে চাই সেই কাজটি সমাধা করিবার মত শক্তি। অর্থাৎ শক্তি আগে ও কাজ পরে। এই জগত ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই সৃষ্টিকাজেও তাঁহার আবশ্যক হইয়াছিল শক্তির। যখন হইতে ঈশ্বর আছেন, তখন হইতে তাঁহার শক্তিও আছে। আমরা এমন একটি সময়কে কল্পনা করিতে পারি না, যখন ঈশ্বর ছিলেন অথচ তাঁহার শক্তি ছিল না। ঈশ্বর অনাদি। কাজেই শক্তিও ‘অনাদি’। পক্ষান্তরে আমরা এমন একটি সময়কে কল্পনা করিতে পারি না, যখন কোনরূপ পদার্থ না থাকিলেও শক্তি থাকিবে না। কাজেই মানিতে হয় যে, ‘শক্তি অনন্ত’।
কোন পদার্থ বা পদার্থের অণুপরমাণুও যেমন শক্তিবিহীন নয়, তেমন সৌরজগত, নক্ষত্র বা নীহারিকাজগত অথবা তাহারও বহির্দেশের কোথায়ও শক্তিবিরল জায়গা নাই। শক্তি কোন স্থানে সীমিত নয়। অর্থাৎ ‘শক্তি অসীম’।
তাপশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, চুম্বকশক্তি ইত্যাদি নানাবিধ শক্তির আমরা ক্রিয়া দেখিতেছি। কিন্তু কখনও শক্তিকে দেখিতে পাইতেছি না। আমরা প্রাণশক্তিবলে বাঁচিয়া আছি এবং নানারূপ কর্ম করিতেছি। কিন্তু প্রাণশক্তি দেখিতে পাইতেছি না। কেননা, শক্তির কোন আকার নাই, ‘শক্তি নিরাকার’।
এ যাবত যে সমস্ত আলোচনা করা হইল, তাহাতে মনে হয় যে, ঈশ্বর যেমন অনাদি, অনন্ত, অসীম ও নিরাকার, তেমনই স্থান, কাল ও শক্তি — ইহারা সকলেই অনাদি, অনন্ত, অসীম ও নিরাকার। এখন প্রশ্ন এই যে, ইহারা কি সৃষ্ট না অসৃষ্ট। অর্থাৎ ঈশ্বর কি ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, না অনাদিকাল হইতে ইহারা স্বভাবতই বিদ্যমান আছে? যদি বলা হয় যে, ইহারা স্বভাবতই বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে ইহারা ঈশ্বরের সৃষ্টি নহে; এবং যদি বলা হয় যে, ইহারা ঈশ্বরের সৃষ্টি — তবে পরমেশ্বর ‘স্থান’কে সৃষ্টি করিলেন কোন স্থানে থাকিয়া, ‘কাল’কে সৃষ্টি করিলেন কোন কালে এবং ‘শক্তি’কে সৃষ্টি করিলেন কোন শক্তির দ্বারা?
১০) সৃষ্টি যুগের পূর্বে কোন যুগ?
ধর্মীয় মতে, হঠাৎ পরমেশ্বরের খেয়াল হইল যে, তিনি সৃষ্টি করিবেন — জীব ও জগত। তিনি আদেশ দিলেন, ‘হইয়া যাও’ — অমনি হইয়া গেল জগত এবং পশু-পাখি, গাছপালা, কীট-পতঙ্গ ও মনষ্যাদি সবই। বিশ্বচরাচরের যাবতীয় সৃষ্টিকার্য শেষ হইতে সময় লাগিল মাত্র ছয়দিন[১]। কিন্তু অনাদিকাল নিষ্ক্রিয় থাকিয়া পরমেশ্বর হঠাত সক্রিয় হইলেন কেন, ধর্মযাজকগণ তাহা ব্যখ্যা করেন না।
জীব ও জগত সৃষ্টির পর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়কে মানুষ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উহার এক এক ভাগকে বলা হয় এক-একটি যুগ। হিন্দুশাস্ত্রমতে যুগ চারিটি। যথা — সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। উহাদের ব্যাপ্তিকা যথাক্রমে — সত্যযুগ ১৭,২৮,০০০, ত্রেতাযুগ ১২,৯৬,০০০, দ্বাপর ৮,৬৪,০০০, এবং কলি ৪,৩২,০০০ বৎসর। আলোচ্য যুগচতুষ্টয়ের মোট বয়সের পরিমাণ ৪৩,২০,০০০ বৎসর। কিন্তু কলি যুগটি শেষ হইতে এখনও প্রায় ৪,২৭,০০০ বৎসর বাকি[২]। সুতরাং আলোচ্য যুগচতুষ্টয়ের অতীত বয়স মাত্র ৩৮,৯৩,০০০ বৎসর [ইহা বিজ্ঞানীদের সর্বাধুনিক প্লিষ্টোসেন উপযুগটির সমানও নহে। এই উপযুগটির বর্তমান বয়স প্রায় ৫০ লক্ষ বৎসর]।
পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ মতে, জীব ও জগত সৃষ্টি হইয়াছে খৃ.পূ. ৪০০৪ সালে[৩] এবং বর্তমানে খৃ. ১৯৭২। সুতরাং এই মতে জগতের বর্তমান বয়স ৫৯৭৬ বৎসর। অর্থাৎ প্রায় ছয় হাজার বৎসর (ইহা হাস্যকররূপে অল্প)।
কাইপারাদি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, প্রায় ৫০০ কোটি বৎসর পূর্বে আমাদের সূর্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহারও ৫০০ কোটি বৎসর পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছিল আমাদের নক্ষত্র জগত। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে আমাদের পৃথিবীর বয়স ৪০০ কোটি বৎসর।[৪]
উক্ত চারিশত কোটি বৎসরকে বিজ্ঞানীগণ (ভূগর্ভস্থ স্তরসমূহের ক্রমানুসারে) কয়েকটি যুগ বা উপযুগে বিভক্ত করিয়াছেন। এখন হইতে ৫০ কোটি বৎসর পূর্বের যাবতীয় সময়কে একত্রে বলা হয় ‘প্রাক ক্যামব্রিয়ান মহাযুগ (Archaeo zoic)। এই যুগের প্রথম দিকে পৃথিবীতে কোনরূপ জীব বা জীবনের অস্তিত্ব ছিল না। এই যুগটি অতিবাহিত হইয়াছিল — জ্বলন্ত পৃথিবী নির্বাপিত হইয়া তরল ও কঠিন হইতে এবং উত্তাপ কমিয়া জল-বায়ু সৃষ্টি হইয়া প্রাণীদের যুগ (Placo Zoic) ৩১ কোটি বৎসর, মধ্যজীবীয় যুগ বা সরীসৃপদের যুগ (Meso Zoic) ১২ কোটি বৎসর ও নবজীবীয় যুগ বা স্তন্যপায়ীদের যুগ (Caino Zoic) ৭ কোটি বৎসর (এই যুগটি এখনও চলিতেছে)।[৫]
জীববিজ্ঞানীদের মতে, প্রাক ক্যামব্রিয়ান মহাযুগের শেষের দিকে পৃথিবীতে জীবন বা জীবের সূত্রপাত হইয়াছিল মাত্র এবং উহা ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপ পাইয়াছে নবজীবীয় যুগে। এই যুগেই হইয়াছে পশু, পাখী, মানুষ ইত্যাদি উন্নতমানের জীবের আবির্ভাব।
আলোচ্য যাবতীয় যুগের ব্যাপ্তিকাল কোন মতে মাত্র ছয় হাজার বৎসর এবং কোন মতে এক হাজার কোটি বৎসর। ধর্ম বা বিজ্ঞান, যে কোন মতেই হউক না কেন, সৃষ্টির পর হইতেই যুগ গণনা করা হইয়া থাকে। তাই সামগ্রিকভাবে ইহাকে আমরা বলিতে পারি ‘সৃষ্টি-যুগ’। এই সৃষ্টি যুগেই দেখা যায় সৌরজগত, নক্ষত্রজগত ইত্যাদির পরিচালন এবং জীবজগতের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণ ইত্যাদি পরমেশ্বরের যত সব কর্ম-তৎপরতা।
ঈশ্বর অনাদি এবং ‘কাল’ও অনাদি। কিন্তু যুগসমূহ অনাদি নয়, উহা সাময়িক। যখন হইতে ঈশ্বর আছেন, তখন হইতে কালও আছে। সেই ‘অনন্ত কাল’-এর সাথে কয়েক হাজার বা কোটি বৎসরের সময়ের তুলনাই হয় না। এমন এক কাল নিশ্চয়ই ছিল, যখন কোনরূপ সৃষ্টিই ছিল না। সেই ‘অনাদি কাল’কে আমরা বলিতে পারি ‘অনাদি যুগ’ বা ‘অসৃষ্ট-যুগ’। সে অনাদি-অসৃষ্ট যুগে পরমেশ্বর কি করিতেন?
১১। ঈশ্বর কি দয়াময়?
‘দয়া’ একটি মহৎ গুণ, এই গুণটির অধিকারীকে বলা হয় ‘দয়াবান’। মানুষ ‘দয়াবান’ হইতে পারে, কিন্তু ‘দয়াময়’ হইতে পারে না। কেননা মানুষ যতই ঐ গুণটির অধিকারি হউক না কেন, উহাতে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। আর ঈশ্বর ঐ গুণে পূর্ণ, তাই তাঁহার একটি নাম ‘দয়াময়’।
কোন ব্যক্তি যদি একজন ক্ষুধার্তকে অন্নদান ও একজন পথিকের মাল লুন্ঠন করে, একজন জলমগ্নকে উদ্ধার করে ও অন্য কাউকে হত্যা করে অথবা একজন গৃহহীনকে গৃহদান করে এবং অপরের গৃহ করে অগ্নিদাহ — তবে তাহাকে ‘দয়াময়’ বলা যায় কি? হয়ত ইহার উত্তর হইবে — ‘না’। কিন্তু উক্তরূপ কার্যকলাপ সত্ত্বেও ঈশ্বর আখ্যায়িত আছেন ‘দয়াময়’ নামে। এখন সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।
জীবজগতে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বিদ্যমান। যখন কোন সবল প্রাণী দুর্বল প্রাণীকে ধরিয়া ভক্ষণ করে, তখন ঈশ্বর খাদকের কাছে ‘দয়াময়’ বটে। কিন্তু তখন তিনি কি খাদ্য-প্রাণীর কাছেও দয়াময়? যখন একটি সর্প একটি ব্যাঙকে ধরিয়া আস্তে আস্তে গিলিতে থাকে, তখন তিনি সর্পটির কাছে দয়াময় বটে। কিন্তু ব্যাঙটির কাছে তিনি নির্দয় নহেন কি? পক্ষান্তরে তিনি যদি ব্যাঙটির প্রতি সদয় হন তবে সর্পটি অনাহারে মারা যায় না কি? ঈশ্বর এক জীবকে অন্য জীবের খাদ্য নির্বাচন না করিয়া নির্জীব পদার্থ অর্থাৎ সোনা, রূপা, লোহা, তামা, মাটি, পাথর ইত্যাদি নির্বাচন করিতে পারিতেন কি না? না পারিলে কেঁচোর খাদ্য মাটি হইল কিরূপে?
ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবেরা সকলেই তাঁহার দয়ার সমানাংশ প্রাপ্তির দাবীদার। কিন্তু তাহা পাইতেছে কি? খাদ্য সম্বন্ধে বলা যায় যে ঈশ্বর মানুষের জন্য চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ইত্যাদি অসংখ্য রকম খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং পশু-পাখীদের জন্য বরাদ্দ করিয়াছেন ঘাস-বিচালী, পোকা-মাকড় আর কুকুরের জন্য বিষ্ঠা। ইহাকে ঈশ্বরের দয়ার সমবন্টন বলা যায় কি?
কাহারও জীবন রক্ষা করা যদি দয়ার কাজ হয় এবং হত্যা করা হয় নির্দয়তার কাজ, তাহা হইলে খাদ্য-খাদক ব্যাপারে ঈশ্বর ‘সদয়’-এর চেয়ে ‘নির্দয়’ই বেশী। তবে কতগুণ বেশী, তাহা তিনি ভিন্ন অন্য কেহ জানে না, কেননা তিনি এক একটি জীবের জীবন রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অসংখ্য জীবকে হত্যা করিয়া থাকেন। কে জানে একটি মানুষের জীবনরক্ষার জন্য তিনি কয়টি মাছ, মোরগ, ছাগল ইত্যাদি হত্যা করেন? কে জানে তিনি একটি শৌল, গজাল, বোয়াল মাছ এবং একটি বক পাখীর জীবনরক্ষার উদ্দেশ্যে কয়টি চুনো মাছ হত্যা করেন? আমিষভোজী জীবদের প্রতি ঈশ্বরের এত অধিক দয়া কেন? তিনি কি হতভাগাদের ‘দয়াময়’ নহেন?
বলা হইয়া থাকে যে, মানুষ ঈশ্বরের সখের সৃষ্ট জীব। তাই মানুষের উপর তাঁহার দয়া-মায়াও বেশী। কিন্তু মানুষ ভেদে তাঁহার দয়ার তারতম্য কেন? ঈশ্বর দয়া করিয়া সকল মানুষকেই প্রাণদান করিয়াছেন এবং দান করিয়াছেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও সুখ-দুঃখের অনুভূতি সমান মাপে। অথচ মানুষের জীবিকা নির্বাহের কোন ব্যাপারেই ঈশ্বরের দয়ার সমবন্টন নাই কেন? কেহ সুরম্য হর্মে বাস করে সাততলায় এবং কেহবা করে গাছতলায়। কেহ পঞ্চামৃত (দুগ্ধ-দধি-ঘৃত-মধু-চিনি) আহার করে এবং কেহ জল-ভাতে শুধু লবণ ও লঙ্কাপোড়া পায় না কেন? কেহ লম্ফ-ঝম্ফ ও দৌড় প্রতিযোগিতায় রেকর্ড করে, কেহ মল্লযুদ্ধে পদক পায়; আবার অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গেরা রাস্তায় বসিয়া অন্যের পায়ে আঘাত পায়। ঈশ্বরের দয়াবন্টনে এরূপ পক্ষপাতিত্ব কেন? আর ‘ভাগ্য’ বলিয়া কিছু আছে কি-না। থাকিলে কাহারও ভাগ্যে চিরশান্তি নাই কেন? ভাগ্যের নিয়ন্তা কে?
কাহারও জীবন রক্ষা করা দয়ার কাজ বটে, কিন্তু কাহাকেও বধ করা দয়ার কাজ নহে। বরং উহা দয়াহীনতার পরিচয়। জগতে জীবের বিশেষত মানুষের জন্মসংখ্যা যত, মৃত্যুসংখ্যা তত। সুতরাং জন্ম ও মৃত্যুর ব্যাপারে ঈশ্বর যেই পরিমাণ সদয়, সেই পরিমাণ নির্দয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের সদয়তা ও নির্দয়তার পরিমাণ এক্ষেত্রে সমান।
উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কেহ কেহ মনে করেন যে, ঈশ্বর সদয়ও নহেন এবং নির্দয়ও নহেন। তিনি নিরাকার, নির্বিকার ও অনির্বচনীয় এক সত্তা। যদি তাহা নাই হয়, তবে পৃথিবীতে শিশুমৃত্যু, অপমৃত্যু, এবং ঝড়-বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাণহানিকর ঘটনাগুলির জন্য তিনিই কি দায়ী নহেন?
তৃতীয় প্রস্তাব
[পরকাল বিষয়ক]
১। জীবসৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?
কেহ কেহ বলেন, মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য হইল — আল্লাহর নাম ও গুণ কীর্তন করা। তাহাই যদি হয়, তবে ইতর জীব সৃষ্টির কারণ কি? তাহারাও যদি ঐ পর্যায়ে পড়ে, তাহা হইলে তাহাদেরও বিচারান্তে স্বর্গ বা নরকবাসী হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হইবে কি? বলা হয় যে, মানুষ ও ইতর জীবের মধ্যে জ্ঞানের বৈষম্য আছে, তাই পরকালেও উহাদের মধ্যে বৈষম্য থাকিবে। বৈষম্য আছে বটে, কিন্তু একবারেই জ্ঞানহীন কোন জীব আছে কি? অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে অতি বৃহৎ হস্তী অবধি প্রত্যেকেই ন্যুনাধিক জ্ঞানের অধিকারী। কাক, শৃগাল, বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদির বুদ্ধিবৃত্তির নিকট সময় সময় সুচতুর মানুষও হার মানে এবং বোলতা, ভীমরুল, মধুমক্ষিকা, উইপোকা ও বাবুই পাখীর গৃহ নির্মাণের কৌশলের কাছে মানুষের জ্ঞানগরিমা ম্লান হইয়া যায়। আবার মানুষের মধ্যেও এমন কতগুলি অসভ্য ও বোকা শ্রেণীর মানুষ দৃষ্ট হয়, যাহারা জ্ঞানের মাপকাঠিতে মনুষ্য পদবাচ্য নহে। তারারা সৃষ্ট হইল কোন উদ্দেশ্যে?
২। পাপ-পুণ্যের ডায়রী কেন?
ধর্মযাজকগণ বলিয়া থাকেন, মানুষের পাপ-পুণ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য প্রত্যেকটি মানুষের কাঁধে দুইজন করিয়া ফেরেস্তা বসিয়া আছেন। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, ঐ ফেরেস্তাদের রিপোর্ট অনুসারেই খোদাতা’লা মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচার করিবেন। বলা হয় যে, আল্লাহ সর্বদর্শী ও সর্বশক্তিমান। তবে মানুষের কৃত পাপ-পুণ্য তিনি কি নিজে দেখেন না? অথবা দেখিলেও মানুষের সংখ্যাধিক্যের জন্যই হউক অথবা সময়ের দীর্ঘতার জন্যই হউক, বিচারদিন পর্যন্ত উহা স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই কি?
৩। পরলোকের সুখ-দুঃখ শারীরিক, না আধ্যাত্মিক?
জীবের মৃত্যুর পর তাহার দেহটি রূপান্তরিত হইয়া পৃথিবীর কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থে পরিণত হয়। আবার ঐ সকল পদার্থের অণুপরমাণুগুলি নানা উপায়ে গ্রহণ করিয়াই হয় নুতন জীবের দেহগঠন। জীবদেহের ত্যাজ্য মসলা। আবার মৃত্যুর পর আমার এই দেহের উপাদানে হইবে লক্ষ লক্ষ জীবের দেহগঠন।
মনে করা যাক — কোন এক অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ডাক্তারকে দিয়া একটি পাঁঠার দেহের প্রতিটি অণু বা কোষ (Cell) কোন উপায়ে চিহ্নিত করা হইল, যাহাতে যে কোন স্থান হইতে উহাদিগকে চিনিয়া বাহির করা যায়। এখন যদি ঐ পাঁঠাটি কোন এক ভোজসভায় পাক করিয়া একশত লোককে ভোজন করান যায় এবং বাকি ত্যাজ্য অংশ শৃগাল, কুকুর, কাক, শকুন, পিপীলিকা ইত্যাদিতে খাইয়া ফেলে তাহা হইলে কিছুকাল পরে ঐ পাঁঠাটির দেহটি পুনর্গঠন করিতে কতগুলি জীবদেহ কর্তন (Operation) করিতে হইবে? চিহ্নিত অংশগুলিকে চিনিয়া বাহির করিতে পারিলেও যতগুলি প্রাণী ঐ পাঁঠাটির দেহ ভক্ষণ করিয়াছিল, ততগুলি প্রাণীর দেহ কর্তন না করিয়া কোনমতেই ঐ পাঁঠাটির দেহ পুনর্গঠন সম্ভব হইবে না। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রাণীবিশেষের দেহ অন্যান্য বহু প্রাণীর দেহ হইতে আহৃত পদার্থসমূহের সমষ্টির ফল। অর্থাৎ যে কোন একটি জীবের দেহ অন্যান্য বহু জীবের দেহ হইতে উদ্ভূত হইতেছে। এমতাবস্থায় পরকালে একই সময় যাবতীয় জীবের দেহ বর্তমান থাকা কি সম্ভব? যদি হয়, তবে প্রত্যেক দেহে তাহাদের পার্থিব দেহের সম্পূর্ণ পদার্থ বিদ্যমান থাকিবে কিরূপে? যদি না থাকে, তবে স্বর্গ-নরকের সুখ-দুঃখ কি আধ্যাত্মিক?
স্বর্গ-নরকের সুখ-দুঃখ ও গোর-আজাব সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ শোনা যায়, তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চলে না। শোনা যায় যে, মৃত্যুর পরে শবদেহকে কবরের ভিতরে পুনর্জীবিত করা হয় এবং ‘মনকির’ ও ‘নকির’ নামক দুইজন ফেরেস্তা আসিয়া প্রত্যেক মৃতকে তাহার সম্পর্কে প্রশ্ন করে। যাহারা পাপী, তাহারা প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না বলিয়া তাহাদের উপর ঐ ফেরেস্তাদ্বয় অমানুষিক অত্যাচার চালায়। গুর্জের (গদার?) আঘাতে দেহ ৭০ গজ নীচে প্রোথিত হইয়া যায়। আবার তাহারা উহাকে পুনরোত্তলন করিয়া লয়। দোজখ হইতে সুড়ঙ্গপথে আগুনের উত্তাপ আসিয়া পাপীদিগকে বিচারদিন পর্যন্ত জ্বালাইতে থাকে। অবশ্য পুণ্যবান ব্যক্তিগণ সুড়ঙ্গপথে বেহেস্তের মলয় বায়ু উপভোগ করিতে থাকেন।
দোজখের শাস্তির বর্ণনায় শোনা যায় যে, পাপীদিগকে পুঁজ, রক্ত, গরম পানি ইত্যাদি খাইতে দেওয়া হইবে, সূর্যের অত্যধিক উত্তাপে পাপীদের মস্তিষ্ক বিগলিত হইয়া যাইবে। চক্ষুর সাহায্যে পাপী যে পাপ করিয়াছে — যেমন যে পাপী পরস্ত্রী দর্শন করিয়াছে, তাহার চক্ষুকে শাস্তি দেওয়া হইবে। এইরূপ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিও, যাহাদের সাহায্যে কোন প্রকার পাপ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত পাপের জন্য ঐ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শাস্তি হইয়া থাকিবে।
বেহেস্তের সুখের বর্ণনায় শোনা যায় যে, পুণ্যবানগণ নানারকম সুমিষ্ট সুস্বাদু ফল আহার করিবেন, নেশাহীন মদিরা পান করিবেন, হুরীদের সহবাস লাভ করিবেন — এক কথায়, প্রত্যেক পুণ্যবান ব্যক্তি মধ্যযুগের এক একজন সম্রাটের ন্যায় জীবনযাপন করিবেন।
ঐ সকল বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, পারলৌকিক সুখ-দুঃখ ভোগ ও অন্যান্য কার্যকলাপ কোনটিই আধ্যাত্মিক অর্থে বর্ণিত হয় নাই, বরং দৈহিক অর্থেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল ব্যাপার সকলই যে দৈহিক, এ কথারও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা চলে না। এই দুই প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে গ্রহণযোগ্য কোনটি?
৪। গোর আজাব কি ন্যায়সঙ্গত?
বলা হইয়া থাকেন যে, খোদাতা’লাই একমাত্র পাপ-পুণ্যের বিচারক। মৃত্যুর পর সকল জীব বিচারদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে এবং প্রমাণাদি গ্রহণপূর্বক বিচারের পরে পাপী দোজখে এবং পুণ্যবান বেহেস্তে যাইবে। কিন্তু একথাও বলা হইয়া থাকে যে, মৃতকে কবরস্থ করার পরই মনকির ও নকির ফেরেস্তাদ্বয় আসিয়া নানারূপ প্রশ্ন করিবেন এবং সন্তোষজনক জবাব না পাইলে তাঁহারাই শাস্তি দেওয়া আরম্ভ করিবেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, পাপীদের প্রতি গোর আজাব কেন, খোদাই যদি পাপ-পুণ্যের বিচার করেন এবং বিচারের পরেই যদি পাপীর নরক এবং পুণ্যবানের স্বর্গসুখ ভোগ করিতে হয়, তবে বিচারের পূর্বে পাপী ও পুণ্যবান ন্যায়বিচারক আল্লাহর কাছে একই রকম ব্যবহার আশা করিতে পারে না কি? যদি বলা হয় যে, ঐ গোর আজাব ভোগ পাপীর পাপকর্মেরই ফল, খোদার হুকুমের শাস্তি, — তাহা হইলে বিচারদিনে বিচারের প্রহসন করার প্রয়োজন কি? আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা। মৃত্যুর পর হইতেই তিনি পাপীকে নরক ও পুণ্যবানকে স্বর্গসুখ ভোগ করাইতে পারেন না কি?
গোর আজাবের বর্ণনা পড়িলে বুঝা যায় যে, উহা একমাত্র ভূগর্ভেরই আজাব, ভূ-পৃষ্ঠের নহে। সচরাচর দেখা যায় যে, আকস্মিক দুর্ঘটনায় বহুলোক মারা যায়, যাহাদের লাশ কবরস্থ নয় না। উহারা জলে-স্থলে ইতস্তত পড়িয়া থাকিয়া শিয়াল-কুকুর ও কাক-শকুনের ভক্ষ্য হয়। উহাদের গোর আজাব হয় না কি? হইলে কিরূপ হয়?
ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানাদি (Semite) জাতিরাই লাশ মাটিতে পুঁতিয়া রাখে, অন্যান্য জাতিরা ইহা করে না। তাহারা কেহ লাশ জলে ভাসাইয়া, কেহ মাঠে ফেলিয়া রাখে, কেহ পর্বতের চূড়ায় রাখিয়া দেয়, কেহ গাছের শাখায় ঝুলাইয়া রাখে এবং কেহবা আগুলেন জ্বালাইয়া দেয়। এইভাবে যে সকল মানুষ পরজগতের যাত্রী হয়, তাহাদের গোর আজাব হয় না কি? যদি হয়, তবে কিরূপে? আর যদি না হয়, তবে লাশকে কবরে রাখিয়া লাভ কি?
কঠিন বা সহজ যেভাবেই হউক, গোর আজাবের সময়সীমা — লাশকে কবরস্থ করার পর হইতে কেয়ামত (মহাপ্রলয়) পর্যন্ত। মনে করা যাক যে, কোন একজন পাপী মরণান্তে লক্ষ বৎসর গোর আজাব ভোগের পর কেয়ামত হইল, অর্থাৎ সে ব্যক্তি একলক্ষ বৎসর গোর আজাব ভোগ করিল। আবার ঐ ব্যক্তির সমান পাপে আর এক ব্যক্তি মারা গেল কেয়ামতের দুই দিন পূর্বে। এ ক্ষেত্রে ঐ উভয় ব্যক্তির গোর আজাব ভোগের পরিমাণ সমান হইল কি?
৫। পরলোকের স্বরূপ কি?
‘পরকাল’ থাকিলে পরলোক বা পরজগত নিশ্চয়ই থাকিবে। কিন্তু পরকাল সম্বন্ধে দাবীটি যত অধিক জোরালো এবং পরিষ্কার, পরজগত বিষয়ে বিবরণটি তত অধিক ঘোরালো বা অস্পষ্ট। ইহজগতে মানুষের স্থিতিকাল নিতান্তই অল্প, বড়জোর ৬০, ৭০ কিংবা ১০০ বৎসর। মানুষ এই সামান্য সময়ের জন্য পৃথিবীতে বাস করিতে আসিয়া তাহার বহুমুখী জ্ঞানপিপাসা মিটাইবার জন্য আকাশ, পাতাল, সাগর, পাহাড় সর্বত্রই বিচরণ ও পর্যবেক্ষণ করিতেছে। এমনকি পদার্থের অণুকে দেখিয়া এখন পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া তাহার শক্তি পরীক্ষা ও ব্যবহার করিতেছে। আর তাহার অনন্তকালের আবাস যে পরজগত, তাহা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা একান্তই ভাসা-ভাসা।
ধর্মগুরুদের আধ্যাত্মিক পর্যটনের বিবরণ হইতে পরজগতের একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদের বিবরণ মতে পরজগত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা — হাশর মাঠ, বেহেস্ত ও দোজখ। ইহারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। যেহেতু হাশরের মাঠ হইতে যাত্রা করিয়া দোজখে যাওয়া যায় এবং পোলছিরাত পার হইয়া বেহেস্তেও যাওয়া যায়। পৃথিবীতে ইহার একটি রূপক ব্যবহার করা যাইতে পারে। মনে করা যাক — আরব সাগর একটি অগ্নিসমুদ্র (দোজখ)। ইহার উপর দিয়া বোম্বাই হইতে এডেন পর্যন্ত একটি পুল আছে। এখন ভারতবর্ষ যদি হয় হাশরের মাঠ, তাহা হইলে আরবদেশ হয় বেহেস্ত। অবস্থানটি এইরূপ নয় কি?
সে যাহা হউক, পরজগত যে কোন এক সৌরজগতের অধীন, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় হাশর মাঠের প্রাকৃতিক বর্ণনায়। কথিত হয় যে, হাশর ময়দানে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে পাপীদের মস্তিষ্ক বিগলিত হইবে এবং বেহেস্তে সুস্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত হইবে। ইহাতে মনে হয় যে, হাশরের মাঠ ও দোজখ, সেখানের বিষুবীয় অঞ্চলে হইবে এবং বেহেস্ত হইবে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত।
পরজগতের আয়তন ইহজগতের তুলনায় কতগুণ বড় বা ছোট এবং হাশর মাঠের সীমা-চৌহদ্দি কি তাহা জানি না। তবে বেহেস্ত-দোজখ সীমিত। যেহেতু সংখ্যায় বেহেস্ত ৮টি এবং দোজখ ৭টি। যাহা সংখ্যা দ্বারা সূচিত হয়, তাহা সমান হইতে বাধ্য। কেননা এক একটি বেহেস্ত বা দোজখ আয়তনে যত বিশালই হউক না কেন, একটির শেষসীমা নির্ধারিত না হইলে আর একটির অবস্থান অসম্ভব। কাজেই যে কোন একটির সীমা নির্ধারিত হইলে সব কয়টির সীমা যে নির্দিষ্ট, তাহা অনিবার্য। তাই প্রশ্ন হইতেছে যে, বেহেস্ত, দোজখ এবং হাশর মাঠের বহির্ভাগে কোন দেশ থাকিবে কি? থাকিলে — সে দেশে কোন বাসিন্দা থাকিবে কি না?
শোনা যায় যে, পরলোকে সূর্য থাকিবে এবং সে উত্তাপ প্রদান করিবে। তবে কি আলো প্রদান করিবে না? যদি করে, তাহা হইলে কি পরলোকেও দিনরাত্রি হইবে? যদি হয়, তবে তাহা কি রকম হইবে? অর্থাৎ সূর্য দৌড়াইবে, না ইহজগত বা পৃথিবীর মত পরজগত ঘুরিবে, না অনন্তকাল শুধু দিনই থাকিবে?
৬। ইহকাল ও পরকালে সাদৃশ্য কেন?
পরকালের অন্তর্গত কবর, হাশর, বেহেস্ত, দোজখ ইত্যদির যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহার প্রত্যেকটি বর্ণনার বিষয়বস্তুই যেন এই পৃথিবীর বিষয়বস্তুর অনুকরণ বা সংস্করণ। যথা — (কবরে) সওয়াল বা প্রশ্ন, গুর্জ বা গদা, স্নিগ্ধ সুমীরণ, উত্তপ্ত বায়ু প্রভৃতি; (হাশর ময়দানে) তামার পাত, সূর্যের তাপ, সাক্ষ্য-জবানবন্দী, দাঁড়ি-পাল্লা, বিচার ইত্যাদি; (বেহেস্তে) সুমিষ্ট ও সুস্বাদু ফল, সুপেয় জল, দুধ, মধু, সুন্দরী রমণী ইত্যাদি এবং (দোজখে) অগ্নি, পুঁজ, গরম জল, পোল, সাঁড়াশী ইত্যাদির যাবতীয় পারলৌকিক বর্ণনাসমূহের আদ্যন্ত পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, পরলোকের সবকিছুই যেন এই পৃথিবী হইতে গৃহীত, কিছুটা পরিবর্ধিত ও কিছুটা পরিবর্তিত। পরলোকে কি কিছুই অভিনব থাকিবে না?
৭। স্বর্গ-নরক কোথায়?
এক কবি বলিয়াছেন—
কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেই সুরাসুর।
কবিকল্পিত ঐ স্বর্গ-নরক এই জগতেই। তবে উহা আধ্যাত্মিক, মানুষের মনোরাজ্যেই উহার অবস্থান। ইহা ভিন্ন পৃথিবীতে আর এক রকম স্বর্গের কথা শোনা যায়, উহা মানুষের শান্তির আবাস।
হিন্দুশাস্ত্র আলোচনায় জানা যায় যে, স্বর্গ দেশটি দেব-দেবীগণের বাসস্থান। ওখানে চিরবসন্ত বিরাজিত এবং শোক-তাপ, জরা-মৃত্যু ওখানে নাই। ওখানে নন্দন কানন, পারিজাত বৃক্ষ, সুরভি গাভী, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব প্রভৃতি সুখ সাধনের সামগ্রী সমস্তই বিদ্যমান আছে এবং স্বর্গবাসীদের কামনা-বাসনা মিটাইবার জন্য ওখানে অপ্সরা, কিন্নরী, গন্ধর্ব ইত্যাদি দেহবিলাসিনীও আছে।
উক্ত দেবপুরী বা স্বর্গদেশ দুর্গম, দুরারোহ ও অতিউচ্চে অবস্থিত। হিন্দুমতে উহা সুমেরু পর্বতের উপরে অবস্থিত। বস্তুত উহা পর্বতের অংশবিশেষ।[৬] অসাধারণ শারীরিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন না হইলে ওখানে কেহই পৌছিতে পারিত না। ওখান হইতে নীচু সমতল ভূমিকে বলা হইত ‘মর্ত্য’। সাধারণ মানুষ এই মর্ত্যলোকেই বাস করিত। শুধু দেবতারাই স্বর্গে ও মর্ত্যে যাতায়াত করিতে পারিতেন, সাধারণ মানুষ তাহা পারিত না।
মহাভারত পাঠে জানা যায় যে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির পদব্রজে সশরীরে স্বর্গে আরোহন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গগমনের গতিপথ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, ঐ স্বর্গটি কৈলাসপুরী ভিন্ন আর কোথায়ও নহে এবং হিমালয় পর্বতের একাংশে উহা অবস্থিত ছিল।[৭] ধর্মপুত্র ওখানে পৌছিতে পারিয়াছিলেন, না পথেই মারা গিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু তৎপর বিখ্যাত পর্বতারোহী তেনজিং ও হিলারী বাদে বোধহয় আর কোন মানুষ ওখানে যায় নাই।
মর্ত্যবাসী মানুষের ওখানে যাতায়াত নাই বলিয়া, দেবতারা ঐ স্বর্গে এখনও বাঁচিয়া আছেন, না মারা গিয়াছেন এবং ঐ স্বর্গটি আবাদী আছে, না জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে — বর্তমানে তাহার কোন খবর নাই। ঐ স্বর্গটি বা স্বর্গীয় দেব-দেবীগণ বর্তমান থাকিলে ইদানিং পর্বতারোহীদের সামনে পড়িতেন।
রামায়ণ পাঠে জানা যায় যে, লংকাধিপতি রাবণ মর্ত্য হইতে স্বর্গে আরোহণ করিয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করিয়া ‘ইন্দ্রজিৎ’ আখ্যা পাইয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, যে কোন মর্ত্যবাসী গায়ের জোরেই ঐ স্বর্গে যাইতে পারিত। অতঃপর লংকেশ্বর মর্ত্যবাসীগণ যাহাতে স্বর্গে উঠিতে পারে তাহার জন্য মর্ত্য হইতে স্বর্গ পর্যন্ত একটি সিঁড়ি তৈয়ার করিবার পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু রামের হাতে তাঁহার অকালমৃত্যু হওয়ায় উহা তিনি কার্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহাতে মনে হয় যে, রাবণরাজ দেবপুরী বা স্বর্গ অর্থাৎ হিমালয় পর্বতে আরোহণোপযোগী একটি সহজ পথ আবিষ্কারের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।
মুসলমানদের পুরাণকাহিনী অনেক ক্ষেত্রে তৌরিত কেতাব তথা বাইবেলের অনুসারী। তবে কোন কোন স্থানে নামধামের সামান্য অদলবদল দেখা যায়। যেমন — ইভ = হাওয়া, সর্প = শয়তান, জ্ঞানবৃক্ষ = গন্দম, এদন উদ্যান = বেহেস্ত ইত্যাদি।
তৌরিতে যে স্থানকে ‘এদন উদ্যান’ বলা হইয়াছে, মুসলমানগণ ঐ স্থানকেই ‘বেহেস্ত’ এবং ঐ স্থানের ঘটনাবলীকেই বেহেস্তের ঘটনাবলী বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন।
হজরত আদমের আদি বাসস্থান সম্বন্ধে তৌরিতের বিবরণটি এইরূপ — ‘আর সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্বদিকে এদনে এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন এবং সেই স্থানে আপনার নির্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমি হইতে সর্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্যদায়ক বৃক্ষ এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে ‘জীবন বৃক্ষ’ উৎপন্ন করিলেন। আর উদ্যানে জলসেচনার্থে এদন হইতে এক নদী নির্গত হইল। উহা তথা হইতে বিভিন্ন হইয়া চতুর্মুখ হইল। প্রথম নদীর নাম পীশোন, ইহা সমস্ত হবিলাদেশ বেষ্টন করে, তথায় স্বর্ণ পাওয়া যায় আর সেই দেশের স্বর্ণ উত্তম। দ্বিতীয় নদীর নাম গীহোন, ইহা সমস্ত কুশদেশ বেষ্টন করে। তৃতীয় নদীর নাম হিদ্দেকল, ইহা অশুরিয়া দেশের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হয়। চতুর্থ নদীর নাম ফরাৎ।”[৮]
তৌরিতের উক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, পীশোন গীহোন, হেদ্দেকল ও ফরাত — এই নদী চারিটির উৎপত্তির এলাকার মধ্যে ঐ সময় ‘এদন’ নামে একটি জায়গা ছিল এবং ঐ এদনস্থিত একটি সুরম্য বাগানে আদমের বাসস্থান ছিল। এদন জায়গাটি বোধ হয় যে, বর্তমান তুরস্ক দেশের পূর্বভাগে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। তৌরিত গ্রন্থে লিখিত নদী ঐ অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া, পীশোন ও গীহোন নামক নদীদ্বয় কৃষ্ণ সাগর ও কাস্পিয়ান সাগরে এবং হিদ্দেকল ও ফরাত নামক নদীদ্বয় একত্র হইয়া পারস্যোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ঐ এদন উদ্যানে বাস করাকে বলা হয় ‘আদমের বেহেস্তবাস’ এবং এদন উদ্যানকে বলা হয় ‘বেহেস্ত’।
বর্তমান কালের বহুল প্রচারিত ‘বেহেস্ত-দোজখ’ নাকি কোটি কোটি বৎসর পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত উহা ব্যবহার করা হয় নাই। শোনা যায় যে, কেয়ামতের পর বিচারান্ত উহাতে লোক ভর্তি করা হইবে। আবার শোনা যায় যে, এস্রাফিল ফেরেস্তার শিঙ্গার ফুঁকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টিই লয় হইয়া যাইবে, স্বয়ং আল্লাহ ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না। তাহাই যদি হয় তবে বেহেস্ত-দোজখ লয় হইবে কিনা। যদি সঞ্চারের পূর্বেই উহা লয় হইয়া যায়, তবে কেয়ামতের পূর্বে আল্লাহ উহা সৃষ্টি করিলেন কেন, আর যদি না হয়, তবে উহা কি আল্লাহর সৃষ্টির বাহিরে অবস্থিত? অধিকন্তু কেয়ামতের পর বিচারান্তেই যদি উহাতে লোক ভর্তি করা হয়, তবে এতোধিককাল পূর্বে উহা সৃষ্টির সার্থকতা কি?
বহুপূর্বকালে পাশ্চাত্যের এক বড় শহরের নিকট একটি স্থানের নাম ছিল নাকি ‘গেহেন্না’। শহরের যাবতীয় ময়লা, রাশি রাশি আবর্জনা ও মৃত লাশ ওখানে ফেলিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হইত এবং অপরাধীগণকে ওখানে নিয়া নানারূপ শাস্তি দেওয়া হইত বা পোড়াইয়া মারা হইত। তৎকালীন লোকে ঐ জায়গাটিকে নোংরা বলিয়া ঘৃণা ও বীভৎস বলিয়া অতিশয় ভয় করিত, কোন লোক ওখানে স্বেচ্ছায় যাইত না। বরং কোন ব্যক্তি কোনরূপ অসৎ কাজ করিলে লোকে তাহাকে এই বলিয়া শাসাইত যে, সে গেহেন্না যাইবে। অথবা বলিত, ‘তুমি কি গেহেন্না যাইতে চাও?’ ইত্যাদি।
উক্ত ‘গেহেন্না’ শব্দটি ভাষান্তরে — গেহেন্নাম, জেহেন্নাম (ইংরেজী g অক্ষরটির ‘জ’ উচ্চারণ) এবং আরবী ভাষায় উহা হইয়াছে নাকি ‘জাহান্নাম’।
বৈদিক মতে স্বর্গকে মনে করা হয় অতি উচ্চে বা ঊর্ধে অবস্থিত স্থান। তাই স্বর্গের এক নাম ‘ঊর্ধলোক’। আবার ক্বচিৎ ইহার বিপরীত মতও শোনা যায়। কোন কোন ধর্মযাজক বলেন যে, পুন্যবানদের কবরের সঙ্গে বেহেস্তের এবং পাপীদের কবরের সঙ্গে দোজখের (সুড়ঙ্গপথে) যোগাযোগ হয়। ইহাতে মনে হয় যে, বেহেস্ত-দোজখ ভূগর্ভেই অবস্থিত। বাস্তবিকই কি তাহাই?
বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, ভূ-পৃষ্ঠের গড় উত্তাপ ২০° সেন্টিগ্রেড বা ৬৮° ফারেনহাইট এবং ৩০ মাইল নিম্নের তাপমাত্রা ১২০০° সে বা ২২০০° ফা। এই উত্তাপে অনায়াসে পাথরাদি গলিয়া যাইতে পারে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও লাভাক্ষরণ সেখান হইতেই হইয়া থাকে। নিম্নদিকে ক্রমশ উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়া কেন্দ্রের দিকে তাপমাত্রা দাঁড়ায় ৬০০০° সে।[৯] ইহা সূর্যের বহিরাবরণের তাপের সমান। ইহাতে বুঝা যায় যে, ভূ-গর্ভে নরকাগ্নি থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু স্বর্গীয় উদ্যানসমূহ কোন জায়গায়?
স্বর্গ ও নরকের আধ্যাত্মিক, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিবরণ যাহাই হউক, বর্তমানে উহার যে কল্পচিত্র দেখানো হয়, তাহার কোনরূপ ভৌগোলিক সত্তা আছে কি?
চতুর্থ প্রস্তাব
[ধর্ম বিষয়ক]
১। আল্লাহ মানুষের পরিবর্তন না করিয়া হেদায়েতের ঝঞ্ঝাট পোহান কেন?
আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি ইচ্ছা করিলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যদি ইহাই হয় যে, মানুষ তাঁহার এবাদত-বন্দেগী করিবে, তাহা হইলে তিনি সমস্ত মানবকে দিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য পালন করাইতে পারেন না কি? পারিলে তাহা না করিয়া তিনি মানুষের দ্বারা মানুষ হেদায়েতের ঝঞ্ঝাট পোহান কেন? ইহাতে কি আঁহার আসল উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত ঘটিতেছে না? হযরত ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদ (দ.)-কে কোন মানুষ হেদায়েত করে নাই, করিয়াছেন আল্লাহতা’লা। কিন্তু নমরুদ, শাদ্দাদ, ফেরাউন, আবু জাহেল ইত্যাদি কাফেরদিগকে তিনি হেদায়েত করিলেন না কেন? তিনি কি স্বেচ্ছায় হেদায়েত করিলেন না, না, করিতে পারিলেন না?
২। ভাগ্যলিপি কি অপরিবর্তনীয়?
যদিও মানুষ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞ, তবু কর্মফলে বিশ্বাস আছে বলিয়াই সে জগতের সকল রকম কাজকর্ম করিয়া যাইতেছে। সমাজ ও রাষ্ট্র কর্মফলকে ভিত্তি করিয়াই গঠিত হইয়াছে এবং ‘কর্মফল আছে’ বলিয়াই উহারা টিকিয়া আছে। রাষ্ট্র ও সমাজ মানুষকে শিক্ষা দিতেছে — কর্ম কর, ফল পাইবে। কিন্তু ধর্ম শিক্ষা দিতেছে উহার বিপরীত। ধর্ম বলিতেছে — কর্ম করিয়া যাও, ফল অদৃষ্টে (তকদীরে) যাহা লিখিত আছে তাহাই পাইবে। এক্ষেত্রে মানুষ কর্ম করিল বটে, কিন্তু ফল রহিল ভগবানের কাছে ভাগ্যলিপিতে নিবদ্ধ। মানুষ জানিল না যে, সে তাহার কাজের ফল পাইবে কি না। কর্মফলের নিশ্চয়তা থাকিলে সন্দিগ্ধ মনেও কাজ করা চলে। যেহেতু তাহাতে মানুষ ভাবিতে পারে যে, হয়ত সে তাহার কাজের ফল পাইতেও পারে। কিন্তু ধর্ম বলে — কর্ম যা কিছুই কর না কেন, ফল নির্ধারিত যাহা আছে, তাহাই পাইবে, একটুও এদিক ওদিক হইবে না। তাহাই যদি হয়, অর্থাৎ কর্মের দ্বারা ভাগ্যলিপি পরিবর্তিত না হয়, তবে কর্ম করিয়া লাভ কি? বিশেষত মানুষের কৃত ‘কর্মের দ্বারা ফলোৎপন্ন’ না হইয়া যদি ঈশ্বরের নির্ধারিত ‘ফলের দ্বারা কর্মোৎপত্তি’ হয়, তবে ‘সৎ’ বা ‘অসৎ’ কাজের জন্য মানুষ দায়ী হইবে কেন?
মনে করা যাক — কোন এক ব্যক্তির ভাগ্যলিপিতে লেখা আছে যে, সে ‘নারকী’। এখন সে নির্ধারিত ঐ ফলোৎপাদক কার্য, যথা — চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা ইত্যাদি করিবে না কি? যদি করে, তবে তাহা সে কাহার ইচ্ছায় করে? নিজের ইচ্ছায়, না, ভগবানের ইচ্ছায়? আর যদি সে কোন পাপ-কর্ম না করিয়া পুণ্য-কর্মই করে, তবে তাহার ভাগ্যলিপির ‘নারকী’ শব্দটি কাটিয়া, ‘স্বর্গবাসী’ এই শব্দটি লেখা হইবে কি? যদি না-ই হয়, তবে হেদায়েতের তম্বিটি কি লৌকিক? আর যদি হয়, তবে ভবিষ্যৎজান্তা ভগবান এই পরিবর্তনের সংবাদ পূর্বাহ্নে জানিয়া প্রথমবারেই অকাট্য তালিকা প্রস্তুত করেন নাই কেন?
ভাগ্যলিপি অপরিবর্তনীয় হলে স্বয়ং ভগবানও উহা মানেন কি না! যদি না মানেন, তবে তিনি উহা লিখিয়াছিলেন কেন? আর যদি মানেন, তবে তিনি লিপি প্রস্তুতির সময় স্বাধীন হইলেও বর্তমানে স্বাধীন হন কিরূপে? ভগবানের বর্তমান কর্তব্য কি শুধু তালিকা দেখিয়া জীবকূলকে দিয়া কার্য করান? তাহাই যদি হয়, তবে বিশ্বস্রষ্টার আশু কর্তব্য কি কিছু নাই?
৩। আদমের পাপ কি?
আলেমগণ বলিয়া থাকেন যে, আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইল এই যে, আল্লাহ তাঁহার দ্বারা পৃথিবী মানুষপূর্ণ করিবেন এবং শেষ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ (দ.)-এর দ্বারা ইসলাম প্রচার করাইবেন। এই সমস্ত পরিকল্পনাই নাকি ভাগ্যলিপির অন্তর্ভুক্ত। আদমকে বেহেস্তে তাঁহাকে গন্দম খাইতে যে নিষেধ করা হইয়াছিল, সে নিষেধ কি খোদাতা’লার আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল? আদম গন্দম খাইয়া প্রকারান্তরে আল্লাহর ইচ্ছাই পূর্ণ করিলেন; যে কাজ ভাগ্যলিপির অনুকূল এবং আল্লাহর ইচ্ছাকে পূর্ণ করে, তাহাতে পাপ কি? পক্ষান্তরে আদম যদি গন্দম না-ই খাইতেন, তাহা হইলে মাহফুজের (লিপিফলকের) যাবতীয় লিপিই বরবাদ হইত না কি? অর্থাৎ পৃথিবীতে মানবসৃষ্টি, বেহেস্ত, দোজখ, হাশর ময়দান ইত্যাদির পরিকল্পনা সমস্তই মাঠে মারা যাইত না কি?
৪। শয়তান কি?
শয়তানের সহিত কোন মানুষের প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলেও তাহার নামটির সাথে যথেষ্ট পরিচয় আছে। ‘শয়তান’ — এই নামটি এত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে যে, হাটে, মাঠে, কোর্ট-কাছারীতে, দোকান, স্কুল-কলেজ, ওয়াজের মাহফিল ইত্যাদির সর্বত্র এবং নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, এমনকি অনেক হিন্দুও ‘শয়তান’ নামটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ এমনও বলিয়া থাকেন যে, “ব্যাটা ভারী শয়তান”।
‘শয়তান’ কথাটির ধাতুগত অর্থ যাহাই হউক, উহাকে সমাজের যাবতীয় দুষ্কর্মের কারক হিসাবেই লোকে ব্যবহার করিতেছে।
ধর্মাধ্যায়ীগণ বলিয়া থাকেন যে, শয়তান পূর্বে ছিল ‘মকরম’ বা ‘ইবলিস’ নামক বেহেস্তবাসী একজন প্রথম শ্রেণীর ফেরেস্তা এবং অতিরিক্ত মুসল্লি। মকরম সেখানে খোদাতা’লার হুকুমমত আদমকে সেজদা না করায় ‘শয়তান’ আখ্যা পাইয়া চিরকাল মানুষকে অসৎ কাজের প্ররোচনা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়া পৃথিবীতে আসে এবং সে অদ্যাবধি নানাবিধ উপায় অসৎ কাজে প্ররোচনা বা দাগা দিয়া বেড়াইতেছে।
আদম ও বিবি হাওয়াকে দাগা দিয়াছিল শয়তান একা। কিন্তু আদমের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শয়তানেরও হইতেছে? না হইলে দাগাকাজ সুচারুরূপে চলে কি রকম?
কেহ কেহ বলেন যে, শয়তানেরও বংশবৃদ্ধি হয় এবং উহা হয় মানুশের চেয়ে দশগুণ বেশী। কারণ প্রতিগর্ভে সাধারণত মানুষ জন্মে একটি, আর শয়তান জন্মে দশটি করিয়া। তাহাদের নাম হয় যথাক্রমে — জলিতন, ওয়াছিন, নফছ, আওয়াম, আফাফ, মকার, মছুদ, দাহেম, ওল-হান ও বার। ইহারা ক্ষেত্রবিশেষে থাকিয়া বিশেষ বিশেষ দাগাকার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। অধিকন্তু ইহাদের মানুষের মত মরণ নাই। কেয়ামতের দিন মানবজাতি যখন লয় পাইবে তখন ইহাদের মৃত্যু ঘটিবে।
জন্ম-মৃত্যুর ঠোকাঠুকিতেও বর্তমানে পৃথিবীতে মানুষ টিকিয়া আছে প্রায় তিনশ’ কোটি। আর মানুষের চেয়ে দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়া অমর শয়তানের সংখ্যা কত? আদম হইতে আজ পর্যন্ত যত লোক জন্মিয়াছে, তাহারা যদি সকলেই জীবিত থাকিত, তাহা হইলে লোকসংখ্যা যত হইত, বোধ হয় যে, কোন ভাষার সংখ্যা দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যাইত না। পৃথিবীতে বর্তমান শয়তানের সংখ্যা তাহারই দশগুণ বেশী নয় কি? ইহাতে মনে হয় যে, পৃথিবীর জলে, স্থলে ও বায়ুমণ্ডলে শয়তান গিজগিজ করিতেছে এবং প্রতিটি মানুষের পিছনে লাখ লাখ শয়তান দাগা দিয়া বেড়াইতেছে।
এত অসংখ্য শয়তান মানবসমাজকে পাপের পথে অহরহ প্ররোচিত করিতেছে, কিন্তু শয়তানের সংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পাইলেও অসৎকাজের মাত্রা ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে না, বরং মানবিক জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সাথে অসৎকাজের মাত্রা ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। এখনও দেখা যাইতেছে যে, স্কুল, কলেজ ও মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা অব্যাহত আছে। বরং হিসাব করিলে দেখা যায় যে, শিক্ষিতের সংখ্যা ও শিক্ষায়তনের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। ন্যায়নিষ্ঠ সাধুপুরুষদের সংখ্যাও নগণ্য নহে। লণ্ডন শহরে নাকি এমন দোকানও আছে, যেখানে বিক্রেতা নাই। অথচ ক্রেতাগণ উচিত মূল্য দিয়াই জিনিসপত্র ক্রয় করিতেছে। আবার কোন রকম হারান জনিস প্রাপ্ত হইয়াও কেহ তাহা আত্মসাৎ করে না। বরং লণ্ডন ট্রান্সপোর্টের লষ্ট প্রপার্টি অফিসে উহা জমা দিয়া থাকে, সেখান হইতে জিনিসের মালিক তাহা ফেরত পাইয়া থাকে।[১০] সেখানে কি শয়তান কম?
ধর্মপ্রচারকদের বর্ণনা শুনিয়া মনে হয় যে, ফেরেস্তাগণ সবাই নপুংসক। মকরমও তাহাই, ‘লানত’ বা অভিশাপ প্রাপ্তির সময়ও মকরম একাই ছিল এবং নপুংসক ছিল। তৎপর তাহার বংশবৃদ্ধির জন্য লিঙ্গভেদ হইল কখন? শুধু ইহাই নহে, শয়তানের বংশবৃদ্ধি সত্য হইলে, প্রথমত তাহার ক্লীবত্ব ঘুচাইয়া পুংলিঙ্গ গঠনান্তে একটি স্ত্রী-শয়তানেরও আবশ্যক ছিল। বাস্তবিক কি শয়তানেরও স্ত্রী আছে? আর না থাকিলেই বা তাহার বংশবৃদ্ধির উপায় কি?
‘শয়তানের দাগা’ বলিতে কি শুধু রোজা-নামাজের শৈথিল্যই বুঝায়, না চুরি, ডাকাতি, বদমায়েশী, নরহত্যা ইত্যাদিও বুঝায়? যদি যাবতীয় অসৎকার্য শয়তান কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হয়, তবে জাতিভেদে অসৎ কাজের মাত্রাভেদ হয় কেন? অর্থাৎ, যে কোন দেশের সম্প্রদায়সমূহের জনসংখ্যার অনুপাতে অপরাধী বা কারাবাসীর সংখ্যা হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হইয়া সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের মধ্যে কারাবাসীর সংখ্যাধিক্য কেন?
জীবজগতে দেখা যায় যে, মাংসাশীগণ উগ্রস্বভাববিশিষ্ট এবং নিরামিষাশীরা শান্ত। গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস-মোরগ, কবুতর, ইত্যাদি প্রাণী মাংসাশী নহে, ইহারা শান্ত। অথচ ব্যাঘ্র, সিংহ, শৃগাল, কুকুর, কাক, চিল ইত্যাদি প্রাণীকুল মাংসাশী এবং উগ্রস্বভাববিশিষ্ট। এ কথাও, স্বীকার্য যে স্বভাবের উগ্রতায় নানা প্রকার অঘটন ঘটিয়া থাকে। ইহাও দেখা যায় যে, মানব সমাজের ভিতর যে জাতি অতিরিক্ত মাংসাশী, সেই জাতির মধ্যেই অতিরিক্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নরহত্যা অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল গর্হিত কাজের উৎপাদক কি শয়তান, না মাংস আর উত্তেজক মসল্লা?
বলা যাইতে পারে যে, কোন কোন দেশের মানুষ মাংসাশী হইয়াও বেশ শান্ত-শিষ্ট ও সংযমী। ইহার কারণ এই নয় যে, সে দেশে শয়তানের উপদ্রব কম বা সে দেশের মাংসে উত্তেজনাশক্তি নাই। ইহার কারণ এই যে, এইরূপ কোন নিরক্ষাঞ্চলের অধিবাসী নহে। অধিকাংশই হিমাঞ্চলের বাসিন্দা। দেশের শীতলতাই তাহাদের স্বভাবের উগ্রতা প্রশমিত করিয়া রাখে।
সুধীগণ বলেন যে, মানুষের মধ্যে ছয়টি আধ্যাত্মিক শত্রু আছে। উহারা ‘ষড়রিপু’ নামে পরিচিত। যথা — কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। ইহাদের তাড়নায় মানুষ নানাবিধ অসৎ কাজ করিয়া থাকে। যে কোন উপায়ে হউক, ইহাদিগকে দমন করিতে পারিলে মানুষ নিষ্পাপ হইতে পারে।
মনোবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সভ্যতার ঊষালোক পাইবার পূর্বে আহার-বিহারে মানুষ ও ইতর জীবের মনোবৃত্তির বিশেষ পার্থক্য ছিল না। সে সময়ের মানুষের মন ছিল কৃত্রিমতাহীন, সরল ও স্বাধীন। তখন মানুষ তাহার যে কোন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে পারিত। তখন প্রবৃত্তিই ছিল মানুষের মনের যথাসর্বস্ব। জ্ঞান উন্মেষের সাথে সাথে মানুষ প্রথমে দলবদ্ধ ও পরে সমাজবদ্ধ হইয়া বসবাস করিতে শুরু করে। এই দল বা সমাজকে রক্ষা করিতে আবশ্যক হইল ত্যাগ ও সংযমের। আদিতে এই ‘ত্যাগ’ ও সংযম’ ছিল স্বেছাধীন। ক্রমে যখন সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন তাহার দল বা সমাজের বন্ধন দৃঢ় করার জন্য সংযমকে বাঁধিল নীতি ও নিয়মের শৃংখলে। ইহাতে মানুষের সেই স্বাধীন প্রবৃত্তিগুলিকে ‘সু’ ও ‘কু’ — এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ‘সু’ প্রবৃত্তিগুলিকে স্বাধীনই রাখা হইল, কিন্তু ‘কু’ প্রবৃত্তিগুলিকে করা হইল কারারুদ্ধ। কারাবাসী কুপ্রবৃত্তিগুলি মনের অন্ধকার কারাকক্ষে ঘুমাইয়া রহিল। মনের যে অংশে এই রুদ্ধপ্রবৃত্তি বাস করে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাহাকে বলা হয় ‘অচেতন মন’ বা ‘নির্জ্ঞান মন’ (Unconscious Mind)।
মানুষ তাহার জাতিগত জীবনের হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন ‘অচেতন মন’ স্বরূপ মূলধন (উত্তরাধিকার সূত্রে) লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ যে সকল অশুভ কামনা সমাজের নীতি, ধর্মের বিধান ও রাষ্ট্রের শাসনের ভয়ে চরিতার্থ করিতে পারে না, তাহাও ক্রমে বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবিয়া গিয়া অচেতন মনে স্থান লয়। অচেতন মনে রুদ্ধপ্রবৃত্তিগুলিকে যে শক্তি অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহাকে কারারক্ষী (Censor) বলা হয়। কারাবন্দী কুপ্রবৃত্তিগুলি সময় সময় জাগ্রত হইয়া কারারক্ষীকে ফাঁকি দিয়া বাহিরে আসে এবং সুপ্রবৃত্তিগুলির সহিত মেলামেশা করিয়া তাহাদিগকে বিপথে চালিত করে। ইহা হইতে মানব সমাজের যত কিছু বিড়ম্বনা। মানুষের যাবতীয় অশুভচিন্তা ও অসৎকাজের উদ্যোক্তা এই ‘অচেতন মন’।
এতদ্বিষয় পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, যাবতীয় অসৎকাজের উদ্যোক্তা মানুষের অভ্যন্তরীণ রিপুসমূহ, বাহিরের কিছু নয়। তবে কি মানুষের ‘কু’ প্রবৃত্তিগুলিকেই ‘শয়তান’ বলা হয়, না মানবদেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট ‘শয়তান’-এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায়?
৫। উপাসনার সময় নির্দিষ্ট কেন?
দেখা যায় যে, প্রায় সকল ধর্মেই কোন কোন উপাসনার জন্য বিশেষ বিশেষ সময় নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে ঐ সকল উপাসনা করিলে বিশ্বপতি কেন উহা মঞ্জুর করিবেন না, তাহার কোন হেতু পাওয়া যায় না।
ইসলামিক শাস্ত্রে প্রত্যহ পাঁচবার নামাজের ব্যবস্থা আছে। এই পাঁচবার নামাজের প্রত্যকেবারের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আদেশ আছে, আবার কোন কোন সময়ে নামাজ নিষেধ।
পৃথিবী আবর্তনের ফলে যে কোন স্থিরমুহুর্তে বিভিন্ন দ্রাঘিমার উপর বিভিন্ন সময় সূচিত হয় এবং প্রতি মুহুর্তেই কোন না কোন স্থানে নির্দেশিত উপাসনা চলিতে থাকে। অথচ সূর্য উদয়, সূর্য অস্ত এবং মধ্যাহ্নে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ (হারাম)। ইহার তাৎপর্য কি? এখানে যখন সূর্যোদয় হইতেছে, তখন এখান হইতে পশ্চিমে কোনখানে সূর্যোদয় হয় নাই এবং এস্থান হইতে পূর্বদিকে পূর্বেই সূর্যোদয় হইয়াছে। এখানে যখন নামাজ পড়া হারাম, ঠিক সেই মুহুর্তেই অন্যত্র হারাম নহে। উদাহারণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বরিশালে যখন সূর্যোদয় হইতেছে, তখন কলিকাতায় হয় নাই এবং চট্রগ্রামে কিছু পূর্বেই সূর্যোদয় হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বরিশালে যখন নামাজ পড়া হারাম, তখন কলিকাতা বা চট্রগ্রামে হারাম নহে। তাহা হইলে নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা নিষিদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য কিছু আছে কি?
নামাজের নিষিদ্ধ সময় সম্বন্ধে যে কথা, ওয়াক্ত সম্বন্ধে সেই একই কথা। পৃথিবীর কোনস্থানেই ওয়াক্ত নহে — এরূপ কোন স্থির মুহুর্ত আছে কি? যদি না থাকে, অর্থাৎ প্রতি মুহুর্তেই যদি পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে নামাজ পড়া চলিতে থাকে, তবে নামাজের সময় নির্ধারণের তাৎপর্য কি?
এক সময় পৃথিবীকে স্থির ও সমতল মনে করা হইত। তাই পৃথিবীর সকল দেশে বা সকল জায়গায় একই রকম সময় সূচিত হইবে, বোধহয় যে এরূপ মনে করিয়া ঐসকল বিধি-নিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পৃথিবী গোল ও গতিশীল।
পৃথিবীর গোলত্বহেতু যে কোন স্থানে বিশেষত সাগর বা মরুভূমিতে দাঁড়াইয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলে নিজেকে ভূ-পৃষ্ঠের কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া ভ্রম হয়। মনে হয় যে, এই কারণেই আরববাসীগণ পবিত্র মক্কা শহরকে পৃথিবীর (ভূ-পৃষ্ঠের) কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া ভাবিতেন এবং ওখানের সকাল-সন্ধ্যাকেই ‘সকল দেশের সকাল-সন্ধ্যা’ বলিয়া মনে করিতেন। এই ভ্রমাত্মক ধারণার ফলে যে সকল সমস্যের উদ্ভব হইয়াছে তাহার কিছু আলোচনা করা যাক।
মনে করা যাক — কোন ব্যক্তি বেলা দেড়টার সময় জোহর নামাজ আদায় করিয়া বিমানযোগে প্রতি ঘণ্টায় তিন হাজার মাইল বেগে চট্রগ্রাম হইতে পবিত্র মক্কা যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি দেখেন যে, ওখানে তখন দুপুর হয় নাই। ওয়াক্ত হইলে ঐ ব্যক্তির আর একবার জোহর নামাজ পড়িতে হইবে কি?
প্রতি ঘণ্টায় ১০৪১ মাইল বেগে পশ্চিম দিকে বিমান চালাইলে (আপাতদৃষ্টিতে) সূর্যকে গতিহীন বলিয়া দেখা যাইবে। অর্থাৎ আরোহীদের কাছে প্রাতঃ, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্ন কিছুই হইবে না; সূর্য যেন স্থিরভাবে একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবে। এমতাবস্থায় আরোহীদের নামাজ ও রোজার উপায় কি?
পৃথিবীর শুধু বিষুবীয় অঞ্চলেই বৎসরের কোন কোন সময় দিন ও রাত্রির পরিমাণ প্রায় সমান হয় না, ব্যবধান অল্প থাকে। কিন্তু উহা হইতে যতই উত্তর বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, দিন ও রাত্রির সময়ের ব্যবধান ততই বাড়িতে থাকে। মেরু অঞ্চলের নিকটবর্তী কোন কোন দেশে বৎসরের কোন কোন সময়ে দিন এত বড় হয় যে ‘সন্ধ্যা’ ও ‘ভোর’এর মাঝখানে কোন রাত্রি নাই। সেখানে এশার নামাজের উপায় কি?
মেরু অঞ্চলে বৎসরে মাত্র একটি দিবা ও একটি রাত্রি হয় অর্থাৎ ছয় মাসকাল একাদিক্রমে থাকে দিন এবং ছয় মাসকাল রাত্রি। ওখানে বৎসরে হয়ত পাঁচবার (পাঁচ ওয়াক্ত) নামাজ পড়া যায়, কিন্তু একমাস রোজা রাখা যায় কি রকমে?
৬। নাপাক বস্তু কি আল্লাহর কাছেও নাপাক?
পৃথিবীর দ্রব্যাদির মধ্যে কতক দ্রব্য ধর্মীয় বিধানে নাপাক (অপবিত্র)। কিন্তু সে সকল কি আল্লাহর কাছেও নাপাক? যদি তাহাই হয়, তবে তাহা তিনি সৃষ্টি করিলেন কেন? আর যদি না হয়, তবে নাপাক অবস্থায় তাঁহার গুণগান করিলে তাহা তিনি অগ্রাহ্য করিবেন কেন? বলা হয় যে, আল্লাহ সর্বত্র বিদ্যমান। যদি তাহাই হয়, তবে নাপাক বস্তুর ভিতরে আল্লাহর অবস্থিতি নাই কি?
৭। উপাসনায় দিগনির্ণয় কেন?
সাকার-উপাসকগণ তাঁহাদের আরাধ্য দেবতার দিকে মুখ করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। যেমন কালী দেবীকে স্থাপন করা হয় দক্ষিণমুখী করিয়া এবং দুর্গাদেবীকে পশ্চিমমুখী। তাই পুজারীকে বসিতে হয় যথাক্রমে উত্তর ও পূর্বমুখী হইয়া। কিন্তু এই দিগনির্ণয় কেন, তাহা আমরা জানি না। বলা হইয়া থাকে যে, আল্লাহ নিরাকার এবং সর্বব্যাপী। তাহাই যদি হয়, তবে নিরাকার উপাসনায় ‘কেবলার’ আবশ্যক কি এবং হাত তুলিয়া মোনাজাত কেন? ইহাতে আল্লাহর দিগবিশেষে স্থিতির সংকেত হয় কি না?
৮। ফেরেস্তা কি?
আমরা শুনিয়া থাকি যে, আল্লাহ নিরাকার। কিন্তু নিরাকারমাত্রই আল্লাহ নহে। বিশ্বব্যাপী ঈথরও (Ether) নিরাকার। কিন্তু ঈথরকে কেহ ঈশ্বর বলে না। কেননা আকারবিহীন হইলেও ঈথরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং উহাদের মধ্যে পদার্থের গুণও পাওয়া যায়। বিশেষত ঈথর নিরাকার হইলেও চেতনাবিহীন। পদার্থ যতই সূক্ষাতিসূক্ষ হউক না কেন, উহার অস্তিত্ব এবং স্থিতি আছে। এমন কোন পদার্থ জগতে পাওয়া যায় নাই, যাহার অস্তিত্ব যন্ত্র বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাহিরে।
শোনা যায় যে, ‘ফেরেস্তা’ নামক এক জাতীয় জীব আছে এবং উহারা স্বর্গ-মর্ত্য সর্বত্র, এমনকি মানুষের সহচররূপেও বিচরণ করে। অথচ মানুষ উহাদের অস্তিত্বের সন্ধান পায় না। উহারা কি কোন পদার্থের তৈয়ারী নয়? যদি হয়, তবে কোন অদৃশ্য বস্তুর দ্বারা তৈয়ারী? তাহা কি ঈথর হইতেও সূক্ষ? হইলে তাহা কি? আর যদি কোন পদার্থের তৈয়ারী না হয়, তবে কি তাহারা নিরাকার?
আল্লাহ নিরাকার, চেতনাবিশিষ্ট ও কর্মক্ষম এক মহাশক্তি। পক্ষান্তরে নিরাকার, চেতনাবিশিষ্ট ও কর্মক্ষম আর একটি সত্তাকে ‘ফেরেস্তা’ বলিয়া স্বীকার করিলে আল্লাহ অতুলনীয় থাকেন কিরূপে?
কেহ কেহ বলেন যে, ফেরেস্তারা নুরের তৈয়ারী। ‘নুর’ বলিতে সাধারণত বুঝা যায় যে, আলো বা রশ্মি। সাধারণ আলো অদৃশ্য নয়, উহা দৃশ্যমান পদার্থ। কিন্তু বিশ্বে এমন কতকগুলি বিশেষ আলো বা রশ্মি আছে, যাহা চক্ষে দেখা যায় না। যেমন — আলফা রশ্মি, কসমিক রশ্মি ইত্যাদি। বিজ্ঞানীগণ নানা কৌশলে ইহাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ইহাদের গুণাগুণও প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীগণ উহার কোন রকম রশ্মির দ্বারা তৈয়ারী ফেরেস্তার সন্ধান পাইতেছেন না। ফেরেস্তারা কোন জাতীয় রশ্মির (নুরের) দ্বারা তৈয়ারী?
৯। ফেরেস্তার কাজ কি?
পবিত্র কোরান ও বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় জানা যায় যে, স্বয়ং খোদাতা’লার হুকুমেই সব সৃষ্টি হইয়া গেল। সৃষ্টিকার্য সম্পাদনে আল্লাহ কোন ফেরেস্তার সাহায্য লন নাই। যিনি সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি তাহা রক্ষা বা পরিচালনাও করিতে পারেন। কিন্তু বিশ্বসংসারের নানাবিধ কার্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও খোদাতা’লা অসংখ্য ফেরেস্তা সৃষ্টি করিলেন কেন? শোনা যায় যে, ফেরেস্তাগণের নিজ ইচ্ছামত কোন কাজ করিবার ক্ষমতা নাই। যদিও বিভিন্ন কাজ করিবার জন্য বিভিন্ন ফেরেস্তা নিযুক্ত আছেন, তথাপি তাঁহারা আল্লাহর আদেশ ভিন্ন কোন কাজই করিতে পারেন না। বিশ্বের যাবতীয় কার্য নির্বাহের জন্য প্রত্যেক ফেরেস্তাকেই যদি আল্লাহর হুকুম দিতে হয়, তবে তাঁহার ব্যস্ততা কমিল কি?
কথিত হয় যে, অসংখ্য ফেরেস্তার মধ্য প্রধান ফেরেস্তা চারিজন। যথা — জেব্রাইল, মেকাইল, এস্রাফিল ও আজ্রাইল। ইহাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।
ক) জেব্রাইল — এই ফেরেস্তা নাকি পয়গম্বরদের নিকট খোদাতা’লার আদেশ পৌঁছাইতেন। হজরত মোহাম্মদ (দ.) দুনিয়ার শেষ পয়গম্বর। তাঁহার বাদে নাকি আর কোন নবী জন্মিবেন না। কাজেই জেব্রাইল ফেরেস্তাও আর দুনিয়ায় আসিবেন না। তবে কেহ বলেন যে, নির্দিষ্ট কয়েকবার আসিবেন। সে যাহা হউক, জেব্রাইল ফেরেস্তা বর্তমানে কোনো কাজ করেন কি?
মনোবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সম্মোহন বিদ্যা (Hypnotism) আয়ত্ত করিতে পারিলে তদ্বারা দূরদূরান্তে অবস্থিত কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে মানসিক ভাবের আদান-প্রদান করা যায়। উহাকে টেলিপ্যাথি (Telepathy) বলে। সর্বশক্তিমান খোদাতা’লা এই টেলিপ্যাথির নিয়মে নবীদের সাথে নিজেই কথাবার্তা বলিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি ফেরেস্তা সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মারফতে নবীদের কাছে আদেশ পাঠাইয়াছেন কেন এবং হজরত মুসার সঙ্গেই বা স্বয়ং কথা বলিলেন কেন?
খ) মেকাইল — শোনা যায়, মেকাইল ফেরেস্তা নাকি মানুষের রেজেক বা খাদ্য বন্টন করেন। ‘খাদ্যবন্টন’ বলিতে সাধারণত মানুষের খাদ্যই বুঝায়। কিন্তু অন্যান্য প্রাণী যথা — পশু, পাখী, কীট-পতঙ্গ ও বিভিন্ন জাতীয় জীবাণুদের খাদ্যবন্টন করেন কে, অর্থাৎ মেকাইল ফেরেস্তা, না স্বয়ং খোদাতা’লা? অন্যান্য প্রাণীদের খাদ্যবন্টন যদি স্বয়ং খোদাতা’লাই করেন, তবে মানুষের খাদ্যবন্টন তিনি করেন না কেন? আর যদি যাবতীয় জীবের খাদ্যই মেকাইল বন্টন করেন, তবে জগতের অন্য কোন প্রাণীকে নীরোগ দেহে শুধু উপবাসে মরিতে দেখা যায় না, অথচ মানুষ উপবাসে মরে কেন? আর মেকাইল ফেরেস্তা যদি শুধু মানুষের খাদ্যবন্টন করেন, তবে মানুষের মধ্যে খাদ্যবন্টনে এতোধিক পার্থক্য কেন? হয়ত কেহ নিয়মিত পঞ্চামৃত (দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, চিনি) আহার করেন, অন্যত্র কেহ জলভাতে শুধু লবণ ও লংকাপোড়া পায় না। মেকাইলের এই পক্ষপাতিত্ব কেন?
মেকাইল ফেরেস্তা নাকি বিশ্বপতির আবহাওয়া বিভাগও পরিচালনা করেন। কিন্তু এই বিভাগেও তাঁহার যোগ্যতা বা নিরপেক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। অতীতকালে যাহাই হইয়া থাকুক না কেন, বর্তমানে ব্যাপকভাবেই পৃথিবীতে খাদ্যসংকট দেখা দিয়াছে এবং বিভিন্ন দেশের নেতাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ দেশের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত পতিত জমি আবাদ কার্যে মনোযোগ দিয়াছেন। কিন্তু সসীম ক্ষমতার জন্য সকল ক্ষেত্রে কৃতকার্য হইতে পারিতেছেন না। অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন মেকাইল ফেরেস্তার অসাধ্য কিছুই নাই। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রদেশের সঙ্গে যদি সাহারা মরুপ্রদেশের তাপ বিনিময় করিয়া যথারীতি বৃষ্টিপাত ঘটান যাইত, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ একর জমি চাষাবাদ ও ফসল উৎপাদনের যোগ্য হইত এবং তাহাতে দুনিয়ার খাদ্যসংকট কতকাংশে কমিয়া যাইত। মেকাইল ফেরেস্তা উহা করিতে পারেন কি না। যদি পারেন, তবে উহা তিনি করেন না কেন?
শোনা যায়, আরবদেশ বিশেষত মক্কা শহর নাকি খোদাতা’লার খুব প্রিয় স্থান। কেননা দুনিয়ার প্রায় যাবতীয় পয়গম্বর আরব দেশেই জন্মিয়াছিলেন এবং শেষ পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ (দ.) পবিত্র মক্কা শহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই আরবদেশে বৃষ্টিপাত ও চাষাবাদ নাই বলিলেই চলে। কিন্তু খোদাতা’লার অপ্রিয় দেশ ভারতবর্ষে বিশেষত আসামের চেরাপুঞ্জিতে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয় কেন?
ভারত-বাংলার কথাই ধরা যাক। ‘কাশী’ হিন্দু জাতির একটি তীর্থস্থান ও নানাবিধ দেব-দেবীর প্রতিমার যাদুঘর এবং চট্রগ্রামে মুসলিম বারো আওলিয়ার দরগাহ। এই কাশীর উপর না হইয়া চট্রগ্রামের উপর এতধিক ঝড়-বন্যা (Cyclone) হয় কেন? দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে তাপ, বায়ু প্রবাহ, মেঘ-বৃষ্টির অত্যধিক পরিমাণে বৈষম্য আছে। ইহার কারণ কি ঐ সকল অঞ্চল ও তাহার নিকটবর্তী সাগর-পাহাড়ের ভৌগোলিক অবস্থান, না মেকাইলের পক্ষপাতিত্ব?
গ) এস্রাফিল — এই ফেরেস্তা নাকি শিঙ্গা (বাঁশী) হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। খোদাতা’লার হুকুমে যখন শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন, তখনই মহাপ্রলয় (কেয়ামত) হইবে এবং পুনঃ যখন খোদাতা’লার হুকুমে ফুঁক দিবেন, তখন হাশর ময়দানাদি পুনঃ সৃষ্টি হইবে।
আদিতে খোদাতা’লার হুকুমেই বিশ্ব-সৃষ্টি হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার হুকুমে ধ্বংস হইতে পারিবে না কেন? যদি পারে, তবে এস্রাফিলের শিঙ্গা ফুঁকিবার আবশ্যক কি? আবার — প্রথমবারে বিশ্বসৃষ্টি খোদাতা’লার হুকুমে হইতে পারিল, কিন্তু মহাপ্রলয়ের পরে পুনঃ হাশর ময়দানাদি সৃষ্টির জন্য শিঙ্গার ফুঁক লাগিবে কেন?
শোনা যায় যে, অনন্ত অতীতকাল হইতে এস্রাফিল ফেরেস্তা শিঙ্গা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন এবং শেষ দিন (কেয়ামত) পর্যন্ত দাড়াইয়া থাকিবেন। অথচ এত অধিককাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন মাত্র দুইটি। কেয়ামতের নির্দিষ্ট তারিখটি আল্লাহ জানেন না কি? জানিলে এস্রাফিল ফেরেস্তাকে এতকাল পূর্বে শিঙ্গা হাতে দিয়া দাঁড় করিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি?
ঘ) আজ্রাইল — ‘যমদূত’ জীবের জীবন হরণ করেন, এই কথাটি হিন্দুদের বেদে বর্ণিত আছে এবং উহারই ধর্মান্তরে নামান্তর ‘আজ্রাইল ফেরেস্তা’। আজ্রাইল ফেরেস্তা যে মানুষের জীবন হরণ করেন তাহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা শোনা যায় ধর্মপ্রচারকদের কাছে। কিন্তু উহাতে মৃত্যু সম্পর্কে অনেক প্রশ্নই অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। গরু, ঘোড়া, বাঘ, মহিষাদি পশু, কাক, শকুনাদি পাখী, হাঙ্গর-কুমীরাদি জলজ জীব ও কীট-পতঙ্গাদির জীবন হরণ করাও কি আজ্রাইলের কাজ? নানাজাতীয় জীবদেহের ভিতরে ও পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডলে এত অধিক অতিক্ষুদ্র জীবাণু বাস করে যে, তাহার সংখ্যা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই জানেন। বিশেষত ঐ সকল জীবের পরমায়ুও খুব বেশী নয়, কয়েক মাস হইতে কয়েক ঘণ্টা বা মিনিট পর্যন্ত। উহাদের জীবনও কি আজ্রাইল হরণ করেন?
আম, জাম, তাল, নারিকেলাদি উদ্ভিদের জন্ম-মৃত্যু আছে বলিয়া লোকে বহুকাল পূর্ব হইতেই জানিত। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, শুধু তাহাই নহে, উদ্ভিদেরও ক্ষুধা, পিপাসা, সুখ-দুঃখ, স্পর্শানুভূতি, এমনকি শ্রবণশক্তিও আছে। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় যন্ত্র দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গাছের নিকট গান-বাজনা হইলে উহাদের মন প্রফুল্ল হয়। সুতরাং উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীবের ‘জীবন’-এ কোন পার্থক্য নাই। এই গাছের জীবন হরণ করেন কে? ইহা ভিন্ন অতিক্ষুদ্র এক জাতীয় উদ্ভিদ আছে, উহাকে ‘বীজাণু’ বলা হয়। ইহারা উপযুক্ত পরিবেশ পাইলে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করে। যেমন — (জলে) শেওলা, বাইছা, (স্থলে) ব্যাঙের ছাতা, সিঁধুল ইত্যাদি। ইহাদের জন্ম এবং মৃত্যু আছে। ইহাদের জীবন হরণ করেন কে?
এমন অনেক জাতের জীবাণু বা বীজাণু আছে যাহারা জীবদেহে বিশেষত মানুষের দেহে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ রোগ সৃষ্টি করে। উহাদের আকার এতই ক্ষুদ্র যে, রোগীর দেহের প্রতি ফোঁটা রক্তে লক্ষ লক্ষ জীবাণু ও বীজাণু থাকে এবং যথাযোগ্য ঔষধ প্রয়োগে অল্প সময়ের মধ্যেই উহারা মারা যায়। উহাদের জীবন হরণ করেন কে?
মানুষ ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় জীবের জীবন যদি আল্লাহতা’লার আদেশেই উড়িয়া যায়, তবে মানুষের জন্য যমদূত কেন? আর বিশ্বজীবের যাবতীয় জীবন যদি আজ্রাইল একাই হরণ করেন, তবে তাঁহার সময় সংকুলান হয় কিরূপে? আজ্রাইলের কি বংশবৃদ্ধি হয়? অথবা আজ্রাইলের সহকারী (Assistant) আজ্রাইল আছে কি? থাকিলে — তাহারা কি এককালীন সৃষ্টি হইয়াছে, না জগতে জীববৃদ্ধির সাথে সাথে নূতন নূতন আজ্রাইল সৃষ্টি হইতেছে?
সর্বশেষ প্রশ্ন এই যে, যমদূতই যদি জীবের হরণ করেন, তবে ‘কারণে মরণ’ হয় কেন? অর্থাৎ রোগ, দুর্ঘটনা ইত্যাদি কোন ‘কারণ ব্যতীত জীবের মৃত্যু হয় না কেন?
প্রকাশ আছে যে, আলোচ্য ফেরেস্তা চতুষ্টয় ভিন্ন আরও চারিজন ফেরেস্তা আছেন, যাঁহারা প্রত্যেক মানুষের সহিত সংশ্লিষ্ট। উহারা হইলেন — কেরামান ও কাতেবীন এবং মনকির ও নকির। উহাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।
ঙ) কেরামান ও কাতেবীন — ধর্মযাজকগণ বলিয়া থাকেন যে, মানুষের সৎ ও অসৎ কাজের বিবরণ লিখিয়া রাখিবার জন্য প্রত্যেক মানুষের কাঁধের উপর ‘কেরামান’ ও ‘কাতেবীন’ নামক দুইজন ফেরেস্তা বসিয়া আছেন। উহাদের একজন লেখেন সৎকাজের বিবরণ এবং অপরজন অসৎ কাজের বিবরণ। এই ফেরেস্তাদ্বয়ের লিখিত বিবরণ দেখিয়া মানুষের পাপ ও পুণ্যের বিচার হইবে।
মাতৃগর্ভ হইতে ভুমিষ্ঠ হইয়াই কোন শিশু পাপ-পুণ্যের অধিকারী হয় না কেননা তখন তাহাদের ন্যায় বা অন্যায়ের কোন জ্ঞান থাকে না। বলা হইয়া থাকে যে, নাবালকত্ব উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোন মানুষের উপর নামাজ ও রোজা ফরজ হয় না।
মানুষ সাবালক হইবার নির্দিষ্ট কোন তারিখ নাই। শৈশব উত্তীর্ণ হইয়া কৈশোর পদার্পণ ও কৈশোর পার হইয়া যৌবনে পদার্পণ, ইহার কোনটিই একদিনে হয় না। মানুষ সাবালক হইবার বয়স — কেহ বলেন ১২ বৎসর, কেহ বলেন নারীর ১৪ ও পুরুষের ১৮ বৎসর ইত্যাদি। এমতাবস্থায় কেরামান ও কাতেবীন ফেরেস্তাদ্বয় মানুষের কাঁধে আসেন কোন সময়? শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরমুহুর্তে না সাবালক হইবার পর? শিশুর জন্মমুহুর্তের পর হইতে আসিলে ফেরেস্তাদ্বয়কে বেশ কয়েক বৎসর কর্মহীন অবস্থায় বসিয়া দিন কাটাইতে হয়। পক্ষান্তরে মানুষ সাবালক হইবার সুনির্দিষ্ট কোন তারিখ নাই। ঐ বিষয়ে ঈশ্বরানুমোদিত সার্বজনীন কোন তারিখ আছে কি?
শোনা যায় যে, ফেরেস্তারা নাপাক ও দুর্গন্ধময় স্থানে থাকেন না বা উহা পছন্দ করেন না। তাই ফেরেস্তাদের মনোরঞ্জনের জন্য কেহ কেহ পাক সাফ থাকেন ও খোশবু ব্যবহার করেন। ধর্মীয় মতে অমুসলমান মানুষ মাত্রেই নাপাক। যেহেতু উহারা যথারীতি ওজু-গোসল করে না, হারাম দ্রব্য ভক্ষণ করে, এমনকি কেহ কেহ মলত্যাগ করিয়া জলশৌচও করে না। আবার ডোম, মেথর ইত্যাদি অস্পৃশ্য জাতি নাপাক ও দুর্গন্ধেই ডুবিয়া থাকে। উহাদের কাঁধে ফেরেস্তা থাকেন কি না?
যে কোন মানুষের মৃত্যুর পর তাহার কাঁধের ফেরেস্তাদের কার্যকাল শেষ হইয়া যায়। অতঃপর তাহারা কি করেন? অর্থাৎ কোন ঊর্ধ্বতন ফেরেস্তা বা আল্লাহতা’লার নিকট তাঁহার নথিপত্র বুঝাইয়া দিয়া অবসর জীবন যাপন করেন, না নিজ জিম্মায় কাগজপত্র রাখিয়া উহার হেফাজতে দিন কাটান, না অন্য কোন মানুষের কাঁধে বসিয়া নতুন কাজ শুরু করেন?
শোনা যায় যে, ফেরেস্তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই এবং থাকিলেও তাহা আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ জানে না। উহাদের মধ্য হইতে শুধুমাত্র কেরামান ও কাতেবীন ফেরেস্তাদ্বয় ব্যতীত আর কোন ফেরেস্তার সহিত মানুষের ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা নাই। বাকিদের মধ্যে মাত্র আজ্রাইল ফেরেস্তা কাছে আসেন একদিন, তাহা অন্তিমকালে এবং মনকির ও নকির ফেরেস্তাদ্বয় কাছে আসেন একদিন, তাহা মৃত্যুর পরে কবরে। কিন্তু কেরামান ও কাতেবীন ফেরেস্তাদ্বয় মানুষের চিরসহচর। হাঁটিতে, বসিতে, ভোজনে, শয়নে সবসময়ই উহারা মানুষের পার্শ্বচর। বিশেষত উহাদের অবস্থান মানুষের চক্ষু ও কর্ণ হইতে চারি-পাঁচ ইঞ্চির বেশী দূরে নয়। অথচ মানুষ উহাদের গতিবিধি দেখিতে শুনিতে অথবা অস্তিত্বই অনুভব করিতে পারে না। ইহার কারণ কি?
মানুষের কার্যবিবরণী ফেরেস্তাগণ যে ভাষাতেই লিখুন না কেন, উহাতে কালি, কলম ও কাগজ বা অনুরূপ অন্য কিছু আবশ্যক। আলোচ্য বিবরণগুলি যদি বাস্তব হয়, তবে উহা লিখিবার উপকরণও হওয়া উচিত পার্থিব। অথচ মানুষ উহার কোন কিছুরই সন্ধান পায় না। উহার বাস্তবতার কোন প্রমাণ আছে কি? যদি না থাকে, তাহা হইলে — যখন ফেরেস্তারা অদৃশ্য, কালি অদৃশ্য, কলম এবং কাগজও অদৃশ্য, তখন বিবরণগুলিও ঐরূপ নয় কি?
চ) মনকির ও নকির — কথিত হয় যে, মানুষ কবরস্থ হইবার কিছুক্ষণ পরই ‘মনকির’ ও ‘নকির’ নামক দুইজন ফেরেস্তা আসিয়া মৃতকে পুনর্জীবিত করেন ও তাহাকে ধর্ম-বিষয়ে কতিপয় প্রশ্ন করেন। সদুত্তর দিতে পারিলে তাহার সুখের অবধি থাকে না। কিন্তু তাহা না পারিলে তাহার উপর হয় নানারূপ শাস্তি। গুর্জের (গদার) আঘাতে ৭০ গজ মাটির নীচে প্রোথিত হইয়া যায়, আবার ঐ ফেরেস্তাদ্বয় নখর দ্বারা তুলিয়া তাহাকে পুনরাঘাত করিতে থাকেন এবং সুড়ঙ্গপথে দোজখের আগুন আসিয়া পাপাত্মা মৃতকে জ্বালাইতে থাকে ইত্যাদি।
কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে সচরাচর মৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই কবরস্থ করা যায়। ঐ সময়ের মধ্যে মৃতদেহের মেদ, মজ্জা ও মাংসাদির বিশেষ কোন বিকৃতি ঘটে না। এই সময়ের মধ্যেই যদি সে পুনর্জীবন লাভ করিয়া সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, তবে তাহার সে নবজীবন হয় বিগত জীবনের অনুরূপ। কেননা দেখা যায় যে, সর্পাঘাত, উগ্র মাদকদ্রব্য সেবন, ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ, কতিপয় রোগ, গভীর নিদ্রা ইত্যাদিতে মানুষের সংজ্ঞালোপ ঘটে। এইরূপ সংজ্ঞাহীনতা কয়েক ঘন্টা হইতে কয়েক দিন, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সপ্তাহকাল স্থায়ী হইতে দেখা যায়। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সংজ্ঞাপ্রাপ্তির পর কাহারও পূর্বস্মৃতি লোপ পাইতে দেখা বা শোনা যায় নাই। কেননা মগজস্থিত কোষসমূহে (Cells) বিকৃতি না ঘটিলে কোন মানুষের স্মৃতি বা জ্ঞানের ভাবান্তর ঘটে না। তাই কাহারো ভাষারও পরিবর্তন ঘটে না।
হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও মস্তিষ্ক — দেহের এই তিনটি যন্ত্রে সুষ্ঠু ক্রিয়ার যৌথ ফলই হইল জীবনীশক্তি। উহার যে কোন একটি বা দুইটির ক্রিয়া সাময়িক লোপ পাওয়াকে ‘রোগ’ বলা হয়। কিন্তু ঐ তিনটির ক্রিয়া একযোগে লোপ পাওয়া বলা হয় ‘মৃত্যু’। শরীর বিজ্ঞানীগণ দেখিয়াছেন যে, উক্ত যন্ত্রত্রয়ের একটি বা দুইটি নিষ্ক্রিয় হইলে, কৃত্রিম উপায়ে পুনঃসক্রিয় করা যায়। তাই তাঁহারা আশা করেন যে, কোন ব্যক্তির ঐ তিনটি যন্ত্রই নিষ্ক্রিয় (মৃত্যু) হইলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত সক্রিয় (পুনর্জীবিত) করা সম্ভব হইবে। তাহাই যদি হয়, তবে কোন মৃত বাঙ্গালী পুনর্জীবিত হইলে সে কি ফরাসী ভাষায় কথা বলিবে, না, বাংলা ভাষায়?
পৃথিবীতে প্রায় ৩৪২৪টি বোধগম্য ভাষা আছে এবং অধিকাংশ মানুষই মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা জানে না। কাজেই কোন মৃতকে পুনর্জীবিত করা হইলে, অধিকাংশই তাহার মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় কথা বলিবার বা বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। এমতাবস্থায় মনকির ও নকির ফেরেস্তাদ্বয় মৃতকে প্রশ্ন করেন কোন ভাষায় — ফেরেস্তী ভাষায়, না মৃতের মাতৃভাষায়?
কেহ কেহ বলেন যে, হাশর ময়দানাদি পারলৌকিক জগতের আন্তর্জাতিক ভাষা হইবে ‘আরবী’, বোধহয় ফেরেশতাদেরও। হাশর ময়দানাদি পরজগতেও যদি পার্থিব দেহধারী মানুষ সৃষ্টি হয়, তবে তাহা হইবে এক অভিনব দেহ। কাজেই তাহাদের অভিনব ভাষার অধিকারী হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু মৃতের কবরস্থ দেহ অভিনব নয়, উহা ভূতপূর্ব। এক্ষেত্রে সে অভিনব (ফেরেস্তী বা আরবী) ভাষা বুঝিতে বা বলিতে পারে কিভাবে?
পক্ষান্তরে, যদি ফেরেস্তারা আঞ্চলিক ভাষায়ই প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন ৩৪২৪টি ভাষাভাষী ফেরেস্তা আবশ্যক। বাস্তবিক কি তাহাই?
ধর্মীয় বিবরণ মতে, পারলৌকিক ঘটনাবলীর প্রায় সমস্তই মানুষের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বাহিরে। কিন্তু ‘গোর আজাব’ — এই ঘটনাটি যদিও পরলোকের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি উহার অবস্থান ইহলোকে অর্থাৎ এই পৃথিবীতেই। বিশেষত উহা মানুষের বাসস্থান হইতে বেশী দূরেও নয়। বড় বড় শহরের গোরস্থানগুলি ছাড়া গ্রামাঞ্চলের কবরগুলি প্রায়ই থাকে বাসস্থানের কাছাকাছি এবং উহার গভীরতাও বেশী নয়, মাত্র ফুট তিনেকের মত। ওখানে বসিয়া ফেরেস্তা ও পুনর্জীবিত ব্যক্তির মধ্যে যে সকল কথাবার্তা, মারধোর, কান্নাকাটি ইত্যাদি কাণ্ডকারখানা হয়, অতি নিকটবর্তী মানুষও তাহা আদৌ শুনিতে পায় না কেন?
দেখা যাইতেছে যে, হত্যা সম্পর্কিত মামলাদিতে কোন কোন ক্ষেত্রে মৃতকে কবর দেওয়ার তিন-চারদিন বা সপ্তাহকাল পরে কবর হইতে তুলিয়া নেওয়া হয় এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু যত বড় দুর্দান্ত ব্যক্তির লাশই হউক না কেন, কোন ডাক্তার উহার গায়ে গুর্জের আঘাতের দাগ বা আগুনে পোড়ার চিহ্ন পান নাই। অধিকন্তু খুব লক্ষ্য করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মুর্দাকে যেইভাবে কবরে রাখা হইয়াছিল, সেইভাবেই আছে, একচুলও নড়চড় হয় নাই। বিশেষত কবরের নিম্নদিকে ৭০ গজ গর্ত বা কোন পার্শ্বে (দোজখের সঙ্গে) সুড়ঙ্গ নাই। ইহার কারণ কি? গোর আজাবের কাহিনীগুলি কি বাস্তব, না অলীক?
এ কথা সত্য যে, কোন মানুষকে বধ করার চেয়ে প্রহার করা সহজ এবং সবল ব্যক্তির চাইতে দুর্বল ব্যক্তি বধ করা সহজ। রেল, জাহাজ, বিমান ইত্যাদির আকস্মিক দুর্ঘটনায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে এক মুহুর্তে শত শত সুস্থ ও সবল মানুষ বধ করেন আজ্রাইল ফেরেস্তা একা। আর রুগ্ন, দুর্বল ও অনাহারক্লিষ্ট মাত্র একজন মানুষকে শুধু প্রহার করিবার জন্য দুইজন ফেরেস্তা কেন? পক্ষান্তরে শুধুমাত্র মৃতকে প্রশ্ন করিবার জন্য দুইজন ফেরেস্তার আবশ্যকতা কিছু আছে কি?
জেব্রাইল, মেকাইল, এস্রাফিল ইত্যাদি নামগুলি উহাদের ব্যক্তিগত নাম (Proper Noun)। কিন্তু কেরামান, কাতেবিন, মনকির ও নকির — এই নামগুলি উহাদের ব্যক্তিগত নাম নয়, সম্প্রদায় বা শ্রেণিগত নাম (Common Noun)। বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ জীবিত আছে।* (* মূল পাণ্ডুলিপির রচনা কাল ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ) তাহা হইলে সমস্ত মানুষের কাঁধে কেরামান আছে ৩০০ কোটি এবং কাতেবিন ৩০০ কোটি, জানিনা মনকির ও নকির ফেরেস্তাদ্বয়ের সংখ্যাও ঐরূপ কিনা। সে যাহা হউক, উহাদের ব্যক্তিগত কোন নাম আছে কি? না থাকিলে উহাদের কোন বিশেষ ফেরেস্তাকে আল্লাহ তলব দেন কি প্রকারে?
১০। দূরত্বহীন যাতায়াত কি সম্ভব?
শোনা যায় যে, স্বর্গীয় দূত জেব্রাইল আল্লাহর আদেশ মত নবীদের নিকট অহি (বাণী) লইয়া ‘আসিতেন’ এবং তাহা নাজেল (অর্পণ) করিয়া চলিয়া ‘যাইতেন’। ‘আসা’ ও ‘যাওয়া’ — এই শব্দ দুইটি গতিবাচক এবং গতির আদি ও অন্তের মধ্যে দূরত্ব থাকিতে বাধ্য। আল্লাহতা’লা নিশ্চয়ই নবীদের হইতে দূরে ছিলেন না। তবে কি জেব্রাইলের ‘আসা’ ও ‘যাওয়া’ দূরত্বহীন? আর দূরত্ব থাকিলে তাহার পরিমাণ কত (মাইল)?
১১। মেয়ারাজ কি সত্য, না স্বপ্ন?
শোনা যায় যে, হজরত মোহাম্মদ (দ.) রাত্রিকালে আল্লাহর প্রেরিত ‘বোরাক’ নামক এক আশ্চর্য জানোয়ারে আরোহন করিয়া আকাশভ্রমণে গিয়াছিলেন। ঐ ভ্রমণকে ‘মেয়ারাজ’ বলা হয়। তিনি নাকি কোটি কোটি বৎসরের পথ অতিক্রম করিয়া আরশে পৌঁছিয়া আল্লাহর সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ তাঁহাকে ইসলামের দুইটি মহারত্ন ‘নামাজ ও ‘রোজা’ উপহার দিয়াছিলেন। ঐ রাত্রে তিনি বেহেস্ত-দোজখাদিও পরিদর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। ইহাতে নাকি তাঁহার সময় লাগিয়াছিল কয়েক মিনিট মাত্র।
কথিত হয় যে, মেয়ারাজ গমনে হজরত (দ.)-এর বাহন ছিল — প্রথম পর্বে ‘বোরাক’ ও দ্বিতীয় পর্বে ‘রফরফ’। উহারা এরূপ দুইটি বিশেষ জানোয়ার, যাহার দ্বিতীয়টি জগতে নাই। বোরাক — পশু, পাখী ও মানব এই তিন জাতীয় প্রাণীর মিশ্ররূপের জানোয়ার। অর্থাৎ তাহার ঘোড়ার দেহ, পাখীর মত পাখা এবং রমণীসদৃশ মুখমণ্ডল। বোরাক কোন দেশ হইতে আসিয়াছিল, ভ্রমণান্তে কোথায় গেল, বর্তমানে কোথায়ও আছে, না মারা গিয়াছে, থাকিলে — উহার দ্বারা এখন কি কাজ করান হয়, তাহার কোন হদিস নাই। বিশেষত একমাত্র শবে মেয়ারাজ ছাড়া জগতে আর কোথাও ঐ নামটিরই অস্তিত্ব নাই। জানোয়ারটি কি বাস্তব না স্বাপ্নিক?
হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন পৃথিবীতে অনেক আছে। খৃ.পূ. তিন হাজার বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে নির্মিত মিশরের পিরামিডসমূহ আজও অক্ষত দেহে দাঁড়াইয়া আছে। হজরতের মেয়ারাজ গমন খুব বেশীদিনের কথা নয়, মাত্র খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকের ঘটনা। ঘটনাটি বাস্তব হইলে — যে সকল দৃশ্য তিনি মহাশুন্যে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন (আরশ ও বেহেস্ত-দোজখাদি), তাহা আজও সেখানে বর্তমান থাকা উচিত। কিন্তু আছে কি? থাকিলে তাহা আকাশ-বিজ্ঞানীদের দূরবীনে ধরা পড়েনা কেন?
মেয়ারাজ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিতে হইলে প্রথম জানা আবশ্যক যে, হজরত (দ.)-এর মেয়ারাজ গমন কি পার্থিব না আধ্যাত্মিক; অর্থাৎ দৈহিক, না মানসিক। যদি বলা হয় যে, উহা দৈহিক, তবে প্রশ্ন আসে — উহা সম্ভব হইল কিভাবে?
আকাশবিজ্ঞানীদের মতে — সূর্য ও গ্রহ-উপগ্রহরা যে পরিমাণ স্থান জুড়িয়া আছে, তাহার নাম সৌরজগত, সূর্য ও কোটি কোটি নক্ষত্র মিলিয়া যে পরিমাণ স্থান জুড়িয়া আছে তাহার নাম নক্ষত্রজগত বা নীহারিকা এবং কোটি কোটি নক্ষত্রজগত বা নীহারিকা মিলিয়া যে স্থান দুখল করিয়া আছে, তাহার নাম নীহারিকাজগত। বিজ্ঞানীগণ দেখিয়াছেন যে, বিশ্বের যাবতীয় গতিশীল পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎ ও আলোর গতি সর্বাধিক। উহার সমতুল্য গতিবিশিষ্ট আর জগতে নাই। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬ হাজার মাইল। আলো এই বেগে চলিয়া এক বৎসরে যতটুকু পথ অতিক্রম করিতে পারে, বিজ্ঞানীগণ তাহাকে বলেন ‘এক আলোকবৎসর’।
বিশ্বের দরবারে আমাদের এই পৃথিবী খুবই নগণ্য এবং সৌরজগতটিও নেহায়েত ছোট জায়গা। তথাপি এই সৌরজগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আলোক পৌঁছিতে সময় লাগে প্রায় ১১ ঘণ্টা। অনুরূপভাবে নক্ষত্রজগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আলোক পৌঁছিতে সময় লাগে প্রায় ৯৭৫ হাজার বৎসর এবং নীহারিকাজগতের এক পান্ত হইতে অপর প্রান্তের দূরত্ব প্রায় ৪০০০ কোটি আলোকবৎসর[১১] এই যে বিশাল স্থান ইহাই আধুনিক বিজ্ঞানীদের পরিচিত দৃশ্যমান বিশ্ব। এই বিশ্বের ভিতরে বিজ্ঞানীরা বেহেস্ত, দোজখ বা আরশের সন্ধান পান নাই। হয়ত থাকিতে পারে ইহার বহির্ভাগে, অনন্ত দূরে। হজরত (দ.)-এর মেয়ারাজ গমন যদি বাস্তব হয়, অর্থাৎ তিনি যদি সশরীরে একটি বাস্তব জানোয়ারে আরোহণ করিয়া সেই অনন্তদূরে যাইয়া থাকেন, তবে কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যে আলোচ্য দূরত্ব অতিক্রম করা কিভাবে সম্ভব হইল? বোরাকের গতি সেকেণ্ডে কত মাইল ছিল?
বোরাকের নাকি পাখাও ছিল। তাই মনে হয় যে, সেও আকাশে (শুন্যে) উড়িয়া গিয়াছিল। শুন্যে উড়িতে হইলে বায়ু আবশ্যক। যেখানে বায়ু নাই, সেখানে কোন পাখী বা ব্যোমযান চলিতে পারে না। বিজ্ঞানীগণ দেখিয়াছেন যে, প্রায় ১২০ মাইলের উপরে বায়ুর অস্তিত্ব নাই।[১২] বায়ুহীন মহাশুন্যে বোরাক উড়িয়াছিল কিভাবে?
নানা বিষয় পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, হজরত (দ.)-এর মেয়ারাজ গমন (আকাশ ভ্রমণ) সশরীরে বা বাস্তবে সম্ভব নহে। তবে কি উহা আধ্যাত্মিক বা স্বপ্ন?
এ কথায় প্রায় সকল ধর্মই একমত যে, ‘সৃষ্টিকর্তা সর্বত্র বিরাজিত’। তাহাই যদি হয়, তবে তাঁহার সান্নিধ্যলাভের জন্য দূরে যাইতে হইবে কেন? আল্লাহতা’লা ঐ সময় কি হযরত (দ.)-এর অন্তরে বা তাঁহার গৃহে, মক্কা শহরে অথবা পৃথিবীতেই ছিলেন না?
পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলিয়াছেন — “তোমরা যেখানে থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন” (সুরা হাদিদ — ৪)। মেয়ারাজ সত্য হইলে এই আয়াতের সহিত তাহার কোন সঙ্গতি থাকে কি?
১২। কতগুলি খাদ্য হারাম হইল কেন?
বিভিন্ন ধর্মমতে কোন কোন খাদ্য নিষিদ্ধ এবং কোন কোন দ্রব্য স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল বলিয়া স্বাস্থ্যবিজ্ঞানমতেও ভক্ষণ নিষিদ্ধ। যে সকল দ্রব্য ভক্ষণে স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে, তাহা নিষিদ্ধ হইলে বুঝা যায় যে, কেন উহা নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু যে খাদ্য ভক্ষণে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা নাই, এমন খাদ্য নিষিদ্ধ (হারাম) হইল কেন?
১৩। এক নেকী কতটুকু?
স্থান, কাল, বস্তু ও বিভিন্ন শক্তি পরিমাপের বিভিন্ন মাপকাঠি বা বাটখারা আছে। যথা — স্থান বা দূরত্বের মাপকাঠি গজ, ফুট, ইঞ্চি, মিটার ইত্যাদি; সময় পরিমাপের ইউনিট ঘন্টা, মিনিট ইত্যাদি; ওজন পরিমাপে মণ, সের; বস্তু পরিমাপে গণ্ডা, কাহন; তাপ পরিমাপে ডিগ্রি; আলো পরিমাপে ক্যাণ্ডেল পাওয়ার; বিদ্যুৎ পরিমাপে ভোল্ট, আম্পিয়ার ইত্যাদির ব্যবহার হয়। অর্থাৎ কোন কিছু পরিমাপ করিতে হইলেই একটি ইউনিট বা একক থাকা আবশ্যক। অন্যথায় পরিমাপ করাই অসম্ভব।
কোন কোন ধর্মপ্রচারক বলিয়া থাকেন যে, অমুক কাজে ‘দশ নেকী’ বা অমুক কাজে ‘সত্তুর নেকী’ পাওয়া যাইবে। এ স্থলে ‘এক নেকী’-এর পরিমাণ কতুকু এবং পরিমাপের মাপকাঠি কি?
১৪। পাপের কি ওজন আছে?
মানুষের মনের সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ঘৃণা, স্নেহ, হিংসা, দ্বেষ, অহংকার ইত্যাদি কোন পদার্থ নহে, ইহারা মনের বিভিন্ন বৃত্তি মাত্র। ব্যক্তিভেদে এসবের তারতম্য লক্ষিত হয়। কাজেই বলিতে হয় যে, ইহাদেরও পরিমাণ আছে। কিন্তু পরিমাপক কোন যন্ত্র নাই। কারণ ইহারা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। যাহা কিছু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতার বাহিরে, সেই সমস্ত তৌলযন্ত্র বা নিক্তি দ্বারা মাপিবার চেষ্টা বৃথা।
মনুষ্যকৃত ‘ন্যায়’ ও ‘অন্যায়’ আছে এবং ইহারও তারতম্য আছে। কাজেই ইহারও পরিমাণ আছে। কিন্তু উহা পরিমাপ করিবার মত কোন যন্ত্র অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।
‘অন্যায়’-এর পরিমাপক কোন যন্ত্র না থাকিলেও বিচারপতিগণ অন্যায়ের পরিমাণ নির্ধারণকরত অন্যায়কারীকে যথোপযুক্ত শাস্তির বিধান করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে বিচারকগণ নানা প্রকার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণপূর্বক অন্যায়ের পরিমাণ নির্ধারণ করেন, কোনরূপ যন্ত্র ব্যবহার করেন না বা করিতে পারেন না।
কঠিন ও তরল পদার্থ ওজন করিবার জন্য নানা প্রকার তৌলযন্ত্র ও বাটখারা আছে। বর্তমান যুগে তৌলযন্ত্রের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছে। লণ্ডন শহরের বৃটিশ ব্যাঙ্কে একটি তৌলযন্ত্র আছে। তদ্বারা নাকি একবারে একশত আশি মণ সোনা, রূপা বা অনুরূপ অন্যান্য দ্রব্যাদি ওজন করা চলে। ঐ নিক্তিটি এমন সুকৌশলে গঠিত যে, মাত্র এক আনার একখানা ডাকটিকিটের ওজনে উহার কাঁটা দশ ইঞ্চি হেলিয়া পড়ে। তৌলযন্ত্রের এরূপ উন্নতি হইলেও — তাপ, আলো, কাল, দূরত্ব, বিদ্যুৎ ইত্যাদি উহা দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। যেহেতু ইহারা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, যাহা কিছু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতার বাহিরে, তাহা তৌলযন্ত্র বা নিক্তি দ্বারা মাপিবার চেষ্টা বৃথা।
‘অন্যায়’-এর নামান্তর পাপ বা অন্যায় হইতেই পাপের উৎপত্তি। সে যাহা হউক, কোনরূপ তৌলযন্ত্র বা ‘নিক্তি’ ব্যবহার করিয়া পাপের পরিমাণ ঠিক করা যায় কিরূপে?
১৫। ইসলামের সাথে পৌত্তলিকতার সাদৃশ্য কেন?
আমরা শুনিয়া থাকি যে, সুসংস্কৃত ইসলামের কুসংস্কারের স্থান নাই। বিশেষত নিরাকার-উপাসক হইতে সাকার-উপাসকগণই অত্যধিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। যদিও বেদ বিশেষভাবে পুতুল-পূজা শিক্ষা দেয় নাই, তথাপি পরবর্তীকালে পুরাণের শিক্ষার ফলে বৈদিক ধর্ম ঘোর পৌত্তলিকতায় পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বৈদিক বা পৌত্তলিক ধর্মের সহিত ইসলাম ধর্মের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার ভাষা ও রূপগত পার্থক্য থাকিলেও ভাবগত পার্থক্য নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় বাদ দিলেও নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে উভয়ত সাদৃশ্য দেখা যায়। যথা —
১। ঈশ্বর এক — একমেবাদ্বিতীয়ম (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)।
২। বিশ্ব-জীবের আত্মাসমূহ এক সময়ের সৃষ্টি।
৩। মরণান্তে পরকাল এবং ইহকালের কর্মফল পরকালে ভোগ।
৪। পরলোকের দুইটি বিভাগ — স্বর্গ ও নরক (বেহেস্ত-দোজখ)।
৫। স্বর্গ সাত ভাগে এবং নরক সাত ভাগে বিভক্ত। (কেহ কেহ বলেন যে, ইহা ভিন্ন আর একটি স্বর্গ আছে, উহা বাদশাহ সাদ্দাদের তৈয়ারী।)
৬। স্বর্গ বাগানময় এবং নরক অগ্নিময়।
৭। স্বর্গ ঊর্ধদিকে অবস্থিত।
৮। পুণ্যবানদের স্বর্গপ্রাপ্তি এবং পাপীদের নরকবাস।
৯। যমদূত (আজ্রাইল ফেরেস্তা) কর্তৃক মানুষের জীবন হরন।
১০। ভগবানের স্থায়ী আবাস ‘সিংহাসন’ (আরশ)।
১১। স্তব-স্তুতিতে ভগবান সন্তুষ্ট।
১২। মন্ত্র (কেরাত) দ্বারা উপাসনা করা।
১৩। মানুষ জাতির আদি পিতা একজন মানুষ — মনু (আদম)।
১৪। নরবলি হইতে পশুবলির প্রথা প্রচলন।
১৫। বলিদানে পুণ্যলাভ (কোরবানী)।
১৬। ঈশ্বরের নামে উপবাসে পুণ্যলাভ (রোজা)।
১৭। তীর্থভ্রমণে পাপের ক্ষয় — কাশী-গয়া (মক্কা-মদিনা)।
১৮। ঈশ্বরের দূত আছে (ফেরেস্তা)।
১৯। জানু পাতিয়া উপাসনায় বসা।
২০। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত (সেজদা)।
২১। করজোড়ে প্রার্থনা (মোনাজাত)।
২২। নিত্যউপাসনার নির্দিষ্ট স্থান — মন্দির (মসজিদ)।
২৩। মালা জপ (তসবিহ পাঠ)।
২৪। নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা করা — ত্রিসন্ধ্যা (পাঁচ ওয়াক্ত)।
২৫। ধর্মগ্রন্থপাঠে পুণ্যলাভ।
২৬। কার্যারম্ভে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ—নারায়ণং সমস্কৃত্যং নৈবষ্ণব নরোত্তমম (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম)।
২৭। গুরুর নিকট দীক্ষা (তাওয়াজ্জ)।
২৮। স্বর্গে গণিকা আছে — গন্ধর্ব কিন্নরী, অপ্সরা (হুর-গেলমান)।
২৯। উপাসনার পূর্বে অঙ্গ ধৌত করা (অজু)।
৩০। দিগনির্ণয়পূর্বক উপাসনায় বসা বা দাঁড়ান।
৩১। পাপ-পুণ্য পরিমাপে তৌলযন্ত্র ব্যবহার (মিজান)।
৩২। স্বর্গগামীদের নদী পার হওয়া — বৈতরণী (পোলছিরাত) ইত্যাদি।
ঐ সমস্ত ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিধি-নিষেধেও অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যথা—মিথ্যা বলিবে না, চুরি করিবে না, মাতা-পিতার সেবা করিবে ইত্যাদি।
উপরোক্ত যে সকল বিষয়ে উভয়ত সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সকল বিষয়ে চিন্তা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, হয়ত ইসলাম হইতে বিষয়গুলি পৌত্তলিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন, নচেৎ পৌত্তলিকদের নিকট হইতে ইসলাম উহা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, পূর্ববর্তীগণের নিকট হইতেই পরবর্তীগণ গ্রহণ করিয়াছে। পরবর্তী কাহারা?
১৬। আরবের বৈশিষ্ট কি?
ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক গঠন ভেদে বিভিন্ন দেশের মাটি, জল, বায়ু ও তাপের পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য হেতু উষ্ণ মণ্ডল, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল ও হিম মণ্ডলের জীবজন্তু ও গাছপালার আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। এই জন্য পর্বত, মরুভূমি, সমভূমি ও মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহের বাসিন্দাদের আকৃতি ও প্রকৃতি একরূপ হয় না। এমনকি একই ফলের দুইটি বীজ দুই দেশে রোপিত হইলে উভয় দেশে উৎপন্ন ফলের স্বাদ একরকম হয় না। কিন্তু ইহা যে প্রকৃতির নিয়ম মতই হইতেছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহাও বুঝা যায় যে, কেন সাহারা মরু অঞ্চলে আদৌ বৃষ্টি না হইয়া আসামের চেরাপুঞ্জিতে এত অধিক বৃষ্টিপাত হয়।
পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, কোন দেশের উপর বৃষ্টিবর্ষণ নির্ভর করে তথাকার পর্বত ও সমুদ্রের অবস্থানের উপর। কিন্তু কোন দেশের উপর খোদাতা’লার ‘রহমত বর্ষণ’ নির্ভর করে কিসের উপর? সকল দেশের উপর কি আল্লাহতা’লার রহমত সমান মাপে বর্ষিত হইয়া থাকে? যদি তাহাই হয়, তবে লক্ষাধিক পয়গম্বর প্রায় সবাই আরব দেশে জন্মিলেন কেন? সে যুগের আরব দেশের আবহাওয়া, উচ্চতা, মাটির উপাদান, ভৌগোলিক অবস্থান ও পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির অনুরূপ কি কোন দেশই পৃথিবীতে ছিল না?
হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে, পয়গম্বরী জিনিসটি প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) নহে। সাধারণত কোন দেশ যখন অন্যায়, অত্যাচার, কদাচার, নীতিগর্হিত কাজ ইত্যাদি ঈশ্বর-বিরোধিতায় পাপে ভরপুর হইয়া উঠিত, তখন সেই সকল দেশের পাপ-পঙ্ক দূর করিয়া ইহ-পরকালের শান্তি স্থাপনের জন্যহ আল্লাহতা’লা ঐ দেশে এক একজন লোককে পয়গম্বরী প্রদান করিতেন।
উপরোক্ত মত সত্য হইলে — যে সকল দেশে একেশ্বরবাদের পরিবর্তে বহু দেব-দেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল এবং যে সকল দেশের আচার, ব্যবহার, চালচলন ও খাদ্যাদি নিতান্ত জঘন্য আকারে ছিল, সেই সকল পাপপূর্ণ দেশে কোন পয়গম্বর না হওয়ার কারণ কি? বিশেষত চিরপৌত্তলিকতার দেশ ভারতবর্ষে একজন নবীও জন্মিলেন না কেন? ভারতের গুনাহগার বান্দাদের জন্য কি আল্লাহর দরদ কম?
প্রসঙ্গত এখানে আর একটি বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে। শোনা যায় যে, নবীদের সংখ্যা নাকি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। উহাদের মধ্যে এক লক্ষ তেইশ হাজার নয় শত আটানব্বই জন নবীই জন্মিয়াছিলেন হজরত ঈসা নবী জন্মিবার আগে, অর্থাৎ ৪০০৪ বৎসরের মধ্যে (বাইবেলের বিবরণমতে হজরত আদম হইতে হজরত ঈসার জন্ম পর্যন্ত সময় ৪০০৪ বৎসর)।[১৩] তাহা হইলে ওদেশে ঐ সময়ে প্রতি বৎসর গড়ে নবী জন্মিয়াছিলেন প্রায় ৩১ জন। আর উহা অসম্ভবও নহে। কেননা নবীদের বিবরণে জানা যায় যে, হয়ত কোন নবীর বাবা, দাদা, এবং পুত্র-পৌত্রাদিও নবী ছিলেন। আবার কখনও ভাইয়ে-ভাইয়ে এবং শ্বশুর-জামাতাও নবিত্ব পাইয়াছিলেন। কিন্তু হজরত ঈসা নবী জন্মিবার পর নবীদের জন্মহার কমিয়া ৫৭০ বৎসরে জন্মিলেন মাত্র একজন, অতঃপর কেয়ামত পর্যন্ত নাকি একেবারেই বন্ধ।
নবীদের আবির্ভাব হ্রাস বা বন্ধ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে এইরূপ মনে হয় যে, হয়ত পাপীর সংখ্যা বা পাপের পরিমাণ আগের চেয়ে হ্রাস পাইয়াছে, নতুবা এ যুগের পাপীদের উপর বীতস্পৃহ হইয়া আল্লাহ তাঁহার হেদায়েত বন্ধ করিয়াছেন; অথবা সভ্যতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি হেতু ‘বাস্তববাদ’-এর আবির্ভাবের ফলে ‘ভাববাদ’-এর অবসান ও ভাববাদীর তিরোধান ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে — এ যুগে কোন নবী না হওয়ার আসল কারণ কোনটি?
হিন্দুগণ বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবী যখন নানারূপ পাপভারে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত, তখন পৃথিবীর পাপভার লাঘব করিবার জন্য স্বর্গবাসী দেবগণ সময় সময় মর্ত্যে অবতীর্ণ হইতেন। এইভাবে একা বিষ্ণুই — মৎস, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি — এই দশরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহারা হিন্দুদের মতে — পথভ্রষ্ট মানবের পথপ্রদর্শক ও ঐশ্বরিকবাণী বাহক। মুসলমানদের যেমন ‘পয়গম্বর’, তেমন হিন্দুদের মতে দেবগণের এক একটি ‘অবতার’। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অবতারসমূহের একটিও ভারতবর্ষের বাহিরে — চীনে বা জাপানে হয় নাই।
উপরোক্ত বিবরণগুলি কি শাস্ত্রকারদের দেশপ্রেমের নিদর্শনস্বরূপ স্বদেশের মহত্ত্বকীর্তন, না বহির্জগত সম্বন্ধে অজ্ঞতা?
১৭। বার-এর মহত্ত্ব কি?
রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি নাম কয়টি পণ্ডিত, মূর্খ, যুবক, বৃদ্ধ সকলেরই মুখস্ত। কিন্তু একই রূপের দিনগুলির মাসে ৩০টি অথবা বৎসরে ৩৬৫টি নাম না হইয়া মাত্র ৭টি নাম কেন হইল এবং কোথা হইতে এই নামগুলি আসিল, তাহা অনেকেই ভাবেন না।
রবি, সোম ইত্যাদি সবগুলিই গ্রহাদির নাম। মানব সভ্যতার মধ্যযুগে, জ্যোতির্বিদ্যার শৈশবে, সভ্য মানব সমাজের কাজের সুবিধার জন্য সম্ভবত কোন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত অসংখ্য ও অনন্ত দিনগুলির ৭টি নামকরণ করিয়া থাকিবেন।
গরু, ঘোড়া বা মানুষের স্বকীয় রূপে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কাজেই উহাদের দেখিয়া চেনা যায়। কিন্তু কাক বা কোকিল সনাক্ত করা সহজ নয়, যেহেতু উহারা সবই একরঙা। স্বাদ, গন্ধ বা বর্ণে সাদৃশ্যযুক্ত পদার্থ অনেক আছে। তাই ডাক্তার কবিরাজগণ ঔষধের শিশি বা মোড়কের গায়ে লেবেল আঁটিয়া দেন। বারের সাতটি নামও যেন একরঙা দিনের গায়ে সাতটি লেবেল।
সে যুগের জ্যোতিষীগণ জ্যোতিষ্কদের শ্রেণীবিভাগ বোধহয় এইরূপ করিয়াছিলেন যে, যে সকল জ্যোতিষ্ক অচল তাহারা ‘নক্ষত্র’ এবং যেগুলি সচল তাহারা ‘গ্রহ’। তাই রবি ও সোম ‘সাত বার’-এর তালিকাভুক্ত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহ নহে। পক্ষান্তরে আমাদের এই পৃথিবী গ্রহ হইলেও ইহার কোন নাম সাত বারের তালিকায় নাই। মাটি-পাথরের তৈয়ারী নিরালোক পৃথিবীটি যে একটি গ্রহ, তাহা বোধহয় সে যুগের জ্যোতিষীগণ জানিতেনই না, জানিলে — ধরা বা মেদিনী ইত্যাদি একটি নাম সাত বারের সহিত যোগ হইয়া সাত বারের স্থলে ‘আট বার’ হইত।
সে যাহা হউক — রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি — এই নামগুলি কেন এইরূপ সাজানো হইয়াছে, তাহার কোন হেতু খুজিয়া পাওয়া যায় না। সাধারণত ঐ নামগুলিকে চারি প্রকারে সাজানো যাইতে পারে। প্রথমত (সহজদৃষ্ট) আয়তন অনুযায়ী। অর্থাৎ বৃহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতম এবং ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম গণনা করা। দ্বিতীয়ত দূরত্ব অনুযায়ী। সৌরজগতের কেন্দ্রের নিকটতম হইতে দূরতম এবং দূরতম হইতে নিকটতমকে গণনা করা। কিন্তু প্রচলিত সাত বারের নামগুলি কোন নিয়মের ভিত্তিতেই সাজানো নাই। এখন দেখা যাক যে, উক্ত চারিটি নিয়মের ভিত্তিতে ঐ নামগুলি সাজাইলে ‘সাত বার’ কি রূপে দাঁড়ায়।
ক) বৃহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতম (সহজদৃষ্ট)
রবি, সোম, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও বুধ
খ) ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম
বুধ, শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র, সোম ও রবি।
গ) নিকটতম হইতে দূরতম
রবি, বুধ, শুক্র, সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি।
ঘ) দূরতম হইতে নিকটতম
শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সোম, শুক্র, বুধ ও রবি।
এতদ্ব্যতীত অধুনা ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো ও ভালকান নামে আরও চারিটি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্বের আবিষ্কৃত গ্রহগুলির নাম যদি দিন বা ‘বার’-এর নাম বলিয়া লোকসমাজে চলিতে পারে, তবে নব আবিষ্কৃত গ্রহদের নামের দোষের কি? ন্যায়বিচারের স্বার্থে ইহাদের নামও সাত বারের সহিত যোগ হইয়া ‘এগার বার’ হওয়া উচিত নয় কি?
ধর্মপ্রচারকদের নিকট শোনা যায় যে, প্রত্যেক ‘বার’-এর গুণাগুণ ভিন্ন এবং কোন কোন বার ভগবানের নিকট খুবই প্রিয়। বারবিশেষে স্বর্গের দ্বার খোলা এবং নরকের দ্বার বন্ধ থাকে। কতিপয় ধর্মে বিশেষ সাপ্তাহিক উপাসনাও প্রচলিত আছে। যথা—ইহুদী ধর্মে, খৃষ্টান ধর্মে রবিবার এবং ইসলাম ধর্মে শুক্রবার। এই সকল উপাসনায় নাকি পুণ্যও খুব বেশী।
সাত বারের নামগুলি মানুষেরই দেওয়া এবং উহা মানুষের কল্পনার সৃষ্টি। ঐ নামগুলি গ্রহ-উপগ্রহের নাম না হইয়া পশু-পাখীর নামও হইতে পারিত। বর্তমান যুগে দূর হইয়াছে নিকট এবং পর হইতেছে বন্ধু। দূর-দূরান্তে অবস্থিত মানুষ এখন অনেক বিষয়েই একাত্মবোধের প্রমাণ। রাষ্ট্রসঙ্ঘ-এর বদৌলতে কোন আন্তর্জাতিক বিধান প্রবর্তন করা আর অসম্ভব নহে। মানব সমাজ যদি একমত হইয়া সাত বারের বিশৃঙ্খল নামগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নবাষ্কৃত গ্রহদের নাম যোগ করিয়া, গ্রহদের আয়তন বা দুরত্ব, যে কোন একটির ভিত্তিতে সাজাইয়া একটি নূতন সংশোধিত বারের তালিকা প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেন, তাহা হইলে সাপ্তাহিক উপাসনা চলিবে কোন ‘বার’-এ? সংশোধিত বারে উপাসনা করিলে ভগবান তাহা মঞ্জুর করিবেন কি?
১৮। চাঁদের ফজিলত কি?
বিজ্ঞানীগণ বলিয়া থাকেন যে, সূর্যের প্রজ্জলিত বাষ্পীয় দেহের ছিন্ন অংশে পৃথিবীর সৃষ্টি এবং পৃথিবীর ঘূর্ণায়মান গতির ফলে কেন্দ্রাপসারণী শক্তির (Centrifugal force) প্রভাবে বিচ্ছিন্ন অংশে চন্দ্রের জন্ম হইয়াছে। এই মতে চন্দ্র, সূর্য এবং পৃথিবীর দেহের মৌলিক উপাদান একই। বিশেষত চন্দ্র জলবায়ুশূন্য একটি দেশ মাত্র। চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় ২,৩৭,০০৮ মাইল দূরে থাকিয়া পায় সাড়ে ঊনত্রিশ দিনে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।[১৪] একবার প্রদক্ষিণের সময়কে এক চান্দ্রমাস বলা হয় এবং বারো চান্দ্রমাসে ধরা হয় এক চান্দ্র বৎসর।
বারোবার চন্দ্রের উদয়কে ‘এক বৎসর’ বলিয়া কে প্রথম গণনা করিয়াছিলেন, জানিনা। বোধ হয় যে, অতীতকালের কোন জ্যোতিষীই হইবেন। তিনি ইচ্ছা করিলে আট, দশ বা বিশ-পঁচিশ মাসেও চান্দ্র বৎসর গণনা করিতে পারিতেন। কেননা পৃথিবী তাহার স্বীয় কক্ষের কোন বিন্দু হইতে যাত্রা করিয়া একবার সূর্য প্রদক্ষিণান্তে পুনঃকক্ষের সেই বিন্দুতে পৌঁছিতে যে সময়টুকু লয়, তাহাই এক সৌর বৎসর। সৌর বৎসর হইবার একটি স্থির মুহুর্ত বা বিন্দু আছে। কিন্তু চান্দ্র বৎসর শেষ হইবার সেরূপ কোন বাঁধন নাই, উহা কাল্পনিক। তাই চান্দ্র মাস ও বৎসর প্রকৃতির ষড়ঋতুকে তুচ্ছ করিয়া আপন খেয়ালমত চলিয়া যায়। সে যাহা হউক, প্রত্যেক মাসের চন্দ্রই যদি পূর্বচন্দ্রের পুনরোদয় হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন বার উদিত চন্দ্রের ফজিলত (গুণাগুণ) ভিন্ন ভিন্ন হয় কিরূপে? আকাশে চন্দ্র মাত্র একটি এবং তাহার নূতন উদয়ের সংখ্যা হইল অনন্ত, ‘বারচাঁদ’ বলা হয় কেন?
বলা যাইতে পারে যে, চন্দ্র একটি বস্তুপিণ্ড, তাহার কোন ফজিলত নাই। কিন্তু কোন কোন সময়ের ফজিলত আছে। লোকে চন্দ্রকে দেখিয়া সেই সময়কে চিনিয়া লয় মাত্র।
মানুষ অতীতের কোন ঘটনার স্মৃতিকে চিত্র, লেখা, আখ্যায়িকা ইত্যাদিরূপে রক্ষা করিতে পারে এবং রঙ্গমঞ্চে তাহার কতকটা পুনরাভিনয় করাও চলে। কিন্তু ‘কাল’ বা সময়ের পুনরাভিনয় করা যায় কি? অতীতের কোন পুণ্যমুহুর্ত বা পুবিত্রদিনকে যে ‘বার্ষিক পবিত্রদিন’ বলিয়া মনে করা হয়, তাহাতে কি কালের পুনরাবৃত্তি হয়, না ঘটনার নামের পুনরুক্তি হয় মাত্র?
হয়ত কেহ বলিবেন যে, অতীতকালের পুনরাগমন না হইলেও অতীত ঘটনার স্মৃতিরক্ষার সার্থকতা আছে। তাহা না থাকিলে জগতে শত শত স্মৃতিদিবস উদযাপিত হয় কেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, স্মৃতিদিবস উদযাপনের সার্থকতা আছে অটে, কিতু ইহা সৌরবৎসরের হিসাব মতেই আছে, চান্দ্রবৎসরের নহে। কেন, তাহা বলিতেছি।
স্মৃতি বা বিস্মৃতি মনের ধর্ম। সুতরাং যে কোন ‘স্মৃতিদিবস’ বা বার্ষিক অনুষ্ঠান মানসিক ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে কোন অনুষ্ঠানের আদি ঘটনাকারী বা তৎসহযোগীদের মনে যে ভাবাবেগ জন্মিয়াছিল, পরবর্তীকালে তদনুবর্তীদের মনে সেইরূপ ভাবের পুনরোদয় করিবার বা করাইবার প্রচেষ্টাই স্মৃতিবার্ষিক অনুষ্ঠান। কিন্তু সেই আদি ঘটনা ঘটিবার সময়ের ঘটনাকারী বা তৎসহযোগীদের মনোভাবের পর্যায়ে পরবর্তীকালের মানুষের মনকে পৌঁছাইতে হইলে পূর্বরূপ প্রাকৃতিক অবস্থারও আবশ্যক।
জীব প্রকৃতির দাস, মানুষও তাহাই। প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যে বা ঋতু পরিবর্তনে জীবের স্বাস্থ্যগত ও শারীরিক পরিবর্তন হয়, ফলে মনোরাজ্যেরও পরিবর্তন হয়। তাই প্রতি বৎসর বসন্তে কোকিল গান গায়, বর্ষাকালে ভেক ডাকে, ফুলবাগানে মৌসুমী ফুল ফোটে। ইহা যেন উহাদের বার্ষিক মহোৎসব। যুগ যুগ ধরিয়া উহারা উহাদের মহোৎসব পালন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে উহাদের মনে প্রেরণ জাগায় কে? উহাদের তো কোন খাতাপত্র বা লিপিপঞ্জি নাই।
পৃথিবী তাহার স্বীয় কক্ষের যেই যেই অংশে অবস্থানকালে কোকিল গান গায়, গাছে গাছে আম পাকে, ডোবায় ডোবায় ভেক ডাকে — একবার আবর্তনের পর পুনঃ কক্ষের সেই সেই অংশে পৃথিবী পৌছিলে, আবার কোকিল গাহিবে, আম পাকিবে এবং ভেক ডাকিবে; তা ঋতু বা মাসের নাম আমরা যাহাই রাখি না কেন। বসন্ত ঋতুকে শরৎ ও ফাল্গুন মাসকে ভাদ্র বলিলেও কোকিল নির্দিষ্ট সময়েই ডাকিবে। তেমনই আষাঢ় মাসকে পৌষ মাস বলিলেও ভেক ঐ সময়ই ডাকিবে। ফল কথা এই যে, কাল বা সময়ের পুনরাগমন না হইলেও সৌর বৎসরে স্বভাবের বা ঋতুর পুনরাগমন হয় এবং তাহাতে জীবের মনোভাবের পুনরাবৃত্তি হয়। চান্দ্র বৎসরের কোন মাসবিশেষের সাথে জীবের মনোরাজ্যের কোন সম্পর্ক আছে কি?
চান্দ্র বৎসর ও সৌর বৎসরে প্রায় ১১ দিনের পার্থক্য হইয়া পড়ে। অর্থাৎ সৌর বৎসর শেষ হইবার প্রায় ১১ দিন পূর্বে চান্দ্র বৎসর শেষ হইয়া যায়। কাজেই তিন বৎসরে প্রায় একমাস ও ছয় বৎসরে প্রায় দুই মাস পার্থক্য হয়। অর্থাৎ একটি ঋতুই পার হইয়া যায়। উপরোক্ত হিসাবমতে এই বৎসর যে অনুষ্ঠান হইল বসন্তে, আঠার বৎসর পর (চান্দ্র বৎসরের হিসাবমতে) তাহা দাঁড়াইবে হেমন্তে। এই রকম প্রাকৃতিক পরিবর্তনযোগ্য ঈদ, কোরবানী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে চাঁদ নির্ণয়ের সার্থকতা কি?
প্রায় সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিই অনুষ্ঠিত হয় চান্দ্রমাসের হিসাব মোতাবেক। কিন্তু হিন্দুগণ উহা পুরাপুরি মানেন না। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, চান্দ্রবৎসর ও সৌরবৎসরে প্রায় এগারো দিনের পার্থক্য হইয়া পড়ে। সৌরবৎসরের সহিত হিন্দু চান্দ্রবৎসরের মোটামুটি মিল রাখিবার জন্য হিন্দুগণ কয়েক বৎসর পর পর বিশেষ একটি চান্দ্রমাসকে গণনা হইতে বাদ দেন। কাজেই চান্দ্রবৎসর ও প্রচলিত (সৌর) বৎসরের মধ্যে প্রায় মিল হইয়া পড়ে।
এই রকম অধিমাসকে ‘মল-মাস’ বলা হয়। এই মাসটিকে হিন্দুরা মাসের মধ্যেই ধরেন না। কোন যাগযজ্ঞ, পূজা-হোম বা শুভকার্য হিন্দুরা এই মাসে করেন না।
ইংরেজদের ‘বড়দিন’ ইত্যাদি উৎসব সৌর বৎসরের হিসাবমতেই হইয়া থাকে এবং প্রতি বৎসরেই একট বাঁধা তারিখে হয়। কিন্তু হিন্দুদের দুর্গাপূজা ইত্যাদি সেইরূপ বাঁধা তারিখে হয় না বটে, তবে ‘মল-মাস’-এর ব্যবস্থার ফলে উহার ব্যবধান এক মাসের বেশী হইতে পারে না। অর্থাৎ চিরকাল একই মাস বা একই ঋতুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। কিন্তু মুসলিম জাহানের যে কোন ধর্মানুষ্ঠান অবিরাম ঘুরিয়া বেড়ায় এবং ছত্রিশ বৎসরে পুরা সৌর বৎসরটিকে একবার আবর্তন করিয়া পূর্বস্থানে (সময়ে) ফিরিয়া আসে।
আধুনিককালের প্রায় সব দেশে যাবতীয় পর্ব বা বার্ষিক অনুষ্ঠানাদি সৌর বৎসরের হিসাবানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, চান্দ্র বৎসরের নয়। আমাদের ‘স্বাধীন বাংলা’ রাষ্ট্রের জন্ম ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর মোতাবেক ২৭শে শাওয়াল মাস। ঐ তারিখে জাতীয় মুক্তিবাহিনীর কাছে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ করার বাণী শ্রবণে যে উদ্যম-উৎসাহে বঙ্গবাসীদের মন নৃত্য করিয়াছিল, তাহা ডিসেম্বর মাসের তান-মন-লয় যোগেই করিয়াছিল। বৎসরের অপর কোন মাসেই প্রকৃতিবীণা ঐরূপ সুর বাজিবে না এবং মন নাচিলেও ঐরূপে নাচিবে না। তাই ‘স্বাধীন বাংলা’ রাষ্ট্রের জন্মবার্ষিকী মহোৎসব প্রতি বৎসর ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে হইতেছে। কিন্তু ২৭শে শাওয়াল তারিখে উহা হইবার কোন যুক্তি আছে কি?
১৯। শবেবরাতের ফজিলত কি?
‘শবেবরাত’ বা ভাগ্যের রজনী মুসলমানদের একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান। কথিত হয় যে, ঐ রাত্রে খোদাতা’লার গুণগান করিলে পরবর্তী এক বৎসরের রুজী-রোজগারে বরকত হয় ও ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। এককথায় জীবন যাপন সুখের হয়। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া অনেকেই উহা পালন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, এই অনুষ্ঠান যাহারা পালন করেন এবং যাহারা করেন না, তাহাদের মধ্যে খাওয়া-পরা বা সুখ-শান্তিতে কোনই পার্থক্য নাই; বরং এমনও দেখা যায় যে, যাহারা করেন না তাঁহারাই অত্যধিক সমৃদ্ধিশালী। মুসলিম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন মহামান্য আগা খাঁ। তিনি কি শবেবরাতের নামাজ পড়িতেন?
হিন্দুদের ঐরূপ অনেক অনুষ্ঠান পালন করিতে দেখা যায়। ‘লক্ষ্মীপূজা’ এই জাতীয় একটি অনুষ্ঠান। হিন্দুমতে লক্ষ্মীদেবী সম্পদ বিতরণের মালিক। তাই তাঁহার পূজা করিলে তিনি প্রসন্না হইয়া তাঁহার ভক্তকে বেশী পরিমাণ ধনরত্ন দান করেন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া হিন্দুগণ লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, চারি আনা পয়সা খরচ করিয়া লক্ষ্মীদেবীর প্রতিমা কিনিতে না পারিয়া কেষ্ট সাধু (লেখকের প্রতিবাসী) ছেলেবেলা হইতেই কলাগাছের লক্ষ্মী সাজাইয়া তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল, আর এখন তাহার পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও কলাগাছ ছাড়িয়া প্রতিমা কিনিবার তওফিক হইল না। অথচ আমেরিকার ফোর্ড সাহেব (Henry Ford) লক্ষ্মীপূজা না করিয়াও সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হইলেন।
হিন্দুধর্মের আর একটি অনুষ্ঠান সরস্বতী পূজা। তিনি নাকি মানুষের বিদ্যাদাত্রী দেবী। তাঁহার পূজা করিলে তিনি সদয় হইয়া তাঁহার ভক্তকে অসীম বিদ্যা দান করেন। অথচ দেখা যাইতেছে যে, সাত বৎসর পর্যন্ত সরস্বতী দেবীর পূজা দিয়াও গোপাল চাঁদ (লেখকের প্রতিবাসী) বর্ণমালা আয়ত্ত করিতে পারিল না, আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরস্বতী পূজা না দিয়াও কবিসম্রাট হইলেন।
‘শবেবরাত’ ঐ শ্রেণীর একটি অনুষ্ঠান নয় কি?
২০। কসুফ ও খসুফ কি?
খুব বেশী দিনের কথা নয়। কলম্বাস সাহেব সদলবলে আমেরিকা পৌঁছিলে একদা তাঁহাদের খাদ্যের অভাব হয়। তাঁহারা ভাবিলেন — মহাবিপদের কথা। অজানা অচেনা দেশ, কোথায় কি খাদ্য পাওয়া যায় না যায়, তাহার ঠিক নাই। কলম্বাস সাহেব মনে মনে এক ফন্দি আঁটিলেন। ঐদিন ছিল সূর্যগ্রহণ। তিনি জানিতেন, অসভ্যরা সূর্যগ্রহণকে অতিশয় ভয় করে। কেননা তাহারা মনে করে যে, সূর্য হঠাৎ নিভিয়া গেলে তাপ এবং আলোর অভাবে তাহারা শীত ও অন্ধকারে মরিয়া যাইবে। কলম্বাস সাহেব আমেরিকার কয়েকজন আদিম (অসভ্য) অধিবাসীকে ডাকিয়া ইশারায় বুঝাইয়া বলিলেন, “আমরা দেবতার বংশধর! আমাদের খাদ্যের অভাব হইয়াছে, তোমরা আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া দাও; নচেৎ আমরা সূর্যকে নিভাইয়া দিব। তাহা হইলে তোমরা শীত ও অন্ধকারে না খাইয়া মরিবে।” প্রথমত অসভ্যরা উহা গ্রাহ্য করিল না। কিন্তু কিছু সময় পর যখন দেখিল যে, সত্যই সূর্য নিভিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন উহারা নানারকম খাদ্য আনিয়া দিতে লাগিল এবং বিচিত্র ভঙ্গিতে কলম্বাসের স্তবস্তুতি করিয়া ইশারায় বলিতে লাগিল — তোমরা সূর্যকে মুক্ত করিয়া দাও, আমাদিগকে বাঁচাও, আমরা আজীবন তোমাদের অনুগত থাকিব। কলম্বাস সাহেব দেখিলেন যে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তখন তিনি অসভ্যদের ইশারায় জানাইলেন — তোমরা শান্ত হও, আমরা অচিরেই সূর্যকে মুক্ত করিয়া দিতেছি। কিছুক্ষণ বাদে যখন সূর্য মুক্ত হইল, তখন অসভ্যরা ভাবিল — তাইত। শ্বেতাঙ্গরা সত্যই দেবতার বংশধর। ইহাদের নিয়মিত ভোগ দিয়া স্তবস্তুতি করিতে হইবে। সেইদিন হইতে কলম্বাস সাহেব যতদিন আমেরিকায় ছিলেন, তাহার মধ্যে আর কখনও তাঁহার খাদ্যের অভাব হয় নাই।
এতদ্দেশের লোকও অতি প্রাচীনকাল হইতে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণকে অমঙ্গলসূচক বলিয়া ভয় করিত এবং এখনও অনেকে করে। তাই হিন্দুদের মধ্যে গ্রহণের সময় মন্ত্রপাঠ, শঙ্খ ও ঘন্টাবাদন, হুলুধ্বনি, কুম্ভমেলায় যাওয়া ও গঙ্গাস্নানের রেওয়াজ আছে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতরেও চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় ‘কসুফ’ ও ‘খসুফ’ নামক নামাজ পড়ার নিয়ম আছে।
যাঁহারা গ্রহণের সময় স্তবস্তুতি করার প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় যে, তাঁহাদের দুইটি উদেশ্য ছিল। প্রথম উদ্দেশ্য হইল, চাঁদ-সুরুজকে গ্রহণমুক্ত করিয়া বিপদকালে তাহাদের সাহায্য করা; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল, চাঁদ-সুরুজকে গ্রহণমুক্ত করিয়া পরোক্ষভাবে নিজেদের মঙ্গল করা। তাঁহারা হয়ত ভাবিতেন — গ্রহণের সময় চাঁদ-সুরুজের খুব কষ্ট হয়। কেননা সাপে ব্যাঙ ধরিয়া যেরূপ ধীরে ধীরে গিলিতে থাকে, রাহু ও কেতু আসিয়া সেইরূপ চাঁদ-সুরুজকে গিলিতে থাকে এবং উহাদের কষ্ট হয়। গ্রহণ দীর্ঘস্থায়ী হইলে বেচারারা হয়ত মরিয়াও যাইতে পারে। সুতরাং উহাদের আশু মুক্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা ভিন্ন তাঁহাদের হাতে আর কোন উপায় ছিল না। তাই অতীতকালের মহানুভব ব্যক্তিগণ চাঁদ-সুরুজের মঙ্গল, নিজেদের মঙ্গল ও বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনায় নানাবিধ স্তবস্তুতির প্রবর্তন ও প্রচলন করিয়া গিয়াছেন।
জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, মহাকাশে সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া এক গোলাকার কক্ষপথে পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া এক গোলাকার কক্ষপথে চন্দ্র ভ্রমণ করিতেছে। এই ঘূর্ণনে সময় সময় চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী এক সরলরেখায় দাঁড়ায়। ঐ সময় অমাবস্যা তিথি হইলে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চন্দ্র দাঁড়াইয়া সূর্যকে আড়াল করিয়া ফেলে, ইহাকে আমরা ‘সূর্যগ্রহণ’ বলি এবং ঐ অবস্থায় পূর্ণিমা তিথি হইলে চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে পৃথিবী দাঁড়ায়। ইহাতে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে পতিত হওয়ার ফলে আমরা ‘চন্দ্রগ্রহণ’ দেখি। আসলে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ — চন্দ্র ও পৃথিবীর ছায়ামাত্র; রাহু, কেতু বা অন্য কিছু নয়। সূর্য হইতে পৃথিবী ও পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব এবং উহাদের ব্যাস ও গতিবেগ জানা থাকিলে, কোন গ্রহণ কখন হইবে এবং কত সময় স্থায়ী হইবে, তাহা অংক করিয়া বলা যায়। বলা বাহুল্য যে, কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ উহা বলিতেছেন এবং যাহা বলিতেছেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইতেছে, এক মিনিটও এদিক-ওদিক হইতেছে না।
একবার ১৯৬৫ সাল হইতে ২০০০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৬ বৎসরের চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন আকাশ-বিজ্ঞানীগণ। এযাবৎ (১৯৮২) তাহার মধ্যে ১৮ বৎসরের গ্রহণসমূহ যথানির্ধারিত সময়েই ঘটিয়া গিয়াছে এবং আগামী বৎসরগুলিতেও তাহার কোন ব্যত্যয় হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। গ্রহণগুলি অলৌকিক বা ঐশ্বরিক কোন ঘটনা নহে, উহা সম্পূর্ণ লৌকিক ও পার্থিব ঘটনা। চাক্ষুষ প্রমাণের জন্য আগামী ১৯৮৩ হইতে ২০০০ সালের শুধু সূর্যগ্রহণের একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হইল। বাহুল্যবোধে চন্দ্রগ্রহণের তালিকা দেওয়া হইল না এবং পৃথিবীর সকল অঞ্চলে একই সময়ে গ্রহণ দৃষ্ট হয় না বলিয়া সময় দেওয়া হইল না।
সাল তারিখ
১৯৮৩ ১১ জুন
৮৪ ৩০ মে ও ২২ নভেম্বর
৮৫ ১২ নভেম্বর
৮৬ ৩ অক্টোবর
৮৭ ২৯ মে
৮৮ ১৮ মার্চ
৮৯ —
৯০ ২২ জুলাই
৯১ ১১ জুলাই
৯২ ৩০ জুন
৯৩ ——–
৯৪ ৩ নভেম্বর
৯৫ ২৪ অক্টোবর
৯৬ ————
৯৭ ৯ মার্চ
৯৮ ২৬ ফেব্রুয়ারী
৯৯ ১১ আগষ্ট
২০০০ পূর্ণ গ্রহণ হইবে না।
এমতাবস্থায় চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের সময় ‘কসুফ’ বা ‘খসুফ’ নামাজ অথবা অন্য কোনরূপ স্তবস্তুতি করার উপকারিতা কিছু আছে কি?
২১। জীবহত্যায় পুণ্য কি?
কোন ধর্ম বলে, ‘জীবহত্যা মহাপাপ’। আবার কোন ধর্ম বলে, ‘জীবহত্যায় পুণ্য হয়’। জীবহত্যায় পাপ বা পুণ্য যাহাই হউক না কেন, জীবহত্যা আমরা অহরহই করিতেছি। তাহার কারণ — জগতে জীবের খাদ্যই জীব। নির্জীব পদার্থ যথা — সোনা, রূপা, লোহা, তামা বা মাটি-পাথর খাইয়া কোন জীব বাঁচে না। পশু-পাখী যেমন জীব; লাউ বা কুমড়া, কলা-কচুও তেমন জীব। উদ্ভিদকুল মৃত্তিকা হইতে যে রস আহরণ করে, তাহাতেও জৈবপদার্থ বিদ্যমান থাকে। কেঁচো মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলেও উহার দ্বারা সে জৈবিক পদার্থই আহরণ করে এবং মৃত্তিকা মলরূপে ত্যাগ করে। জীবহত্যার ব্যাপারে কতগুলি উদ্ভট ব্যবস্থা আছে। যথা — ভগবানের নামে জীবহত্যা করিলে পুণ্য হয়, অখাদ্য জীব হত্যা করিলে পাপ হয়, শত্রু শ্রেণীর জীব হত্যা করিলে পাপ নাই এবং খাদ্য জীব হত্যা করিলে পাপ-পুণ্য কিছুই নাই ইত্যাদি।
সে যাহা হউক, ভগবানের নামে জীবহত্যা করিলে পুণ্য হইবে কেন? কালীর নামে পাঁঠা বলি দিয়া উহা যজমান ও পুরোহিত ঠাকুরই খায়। কালীদেবী পায় কি? পদপ্রান্তে জীবহত্যা দেখিয়া পায় শুধু দুঃখ আর পাঁঠার অভিশাপ। কেননা কালীদেবীর ভক্তগণ যাহাই মনে করুন, পাঁঠায় কামনা করে কালীদেবীর মৃত্যু। যেহেতু কালীদেবী মরিলেই সে বাঁচিত।
জীবমাত্রেই বলির পাত্র নহে। আবার ধর্মে ধর্মে বলির জীবে পার্থক্য অনেক। মুসলমানদের কোরবানীর (বলির) পশু — গরু, বকরী, উট, দুম্বা ইত্যাদি। কিন্তু হিন্দুদের বলির পাত্র — ছাগল, ভেড়া, হরিণ, মহিষ, শুকর, গণ্ডার, শশক, গোসাপ এবং কাছিম।
ইসলামের বিধানমতে ‘কোরবানী’ একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান। শোনা যায় যে, হজরত ইব্রাহিম (আ.) স্বপ্নাদেশমত তাঁহার প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কোরবানী করিয়া খোদাতা’লার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তাই মুসলমানগণ গরু, ছাগল, উট, দুম্বা ইত্যাদি কোরবানী দিয়া খোদাতা’লার প্রিয়পাত্র হন।
কোরবানী প্রথার মূল উৎস সন্ধান করিলে মনে কয়েকটি প্রশ্নের উদয় হয়। প্রশ্নগুলি এমন —
ক) হজরত ইব্রাহিমের ‘স্বপ্নাদেশ’ তাঁহার মনের ভগব্দভক্তির প্রবণতার ফল হইতে পারে না কি?
খ) খোদাতা’লা নাকি স্বপ্নে বলিয়াছিলেন, ‘হে ইব্রাহিম, তুমি তোমার প্রিয়বস্তু কোরবানী কর।’ এই ‘প্রিয়বস্তু’ কথাটির অর্থে হজরত ইব্রাহিম তাঁহার পুত্র ইসমাইলকে বুঝিয়াছিলেন এবং তাই তাহাকে কোরবানী করিয়াছিলেন। হজরত ইব্রাহিমের প্রিয়বস্তু তাঁহার ‘পুত্র’ ইসমাইল না হইয়া তাঁহার ‘প্রাণ’ হইতে পারে না কি?
শোনা যায় যে, একদা আল্লাহতা’লা হজরত মুসার নিকট দুইটি চক্ষু চাহিয়াছিলেন। হজরত মুসা অনেক কোসেস করিয়াও কাহারও কাছে চক্ষুর খোঁজ না পাইয়া পরের দিন (তুর পর্বতে গিয়া) আল্লাহর কাছে বলিলেন, সমস্ত দেশ খোঁজ করিলাম, কিন্তু কোন ব্যক্তিই আমাকে চক্ষু দিতে রাজী হইল না। তখন নাকি আল্লাহ বলিয়াছিলেন, হে মুসা! তুমি সমস্ত দেশ খোঁজ করিয়াছ সত্য, কিন্তু তুমি তোমার নিজ দেহটি খোঁজ করিয়াছ কি? তোমার নিজের দুইটি চক্ষু থাকিতে অপরের চক্ষু চাহিতে গিয়াছ কেন? হজরত মুসা নিরুত্তর হইলেন।
ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, নবীগণও কোন কোন সময় আল্লাহর বাণীর উদ্দেশ্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভ্রমে পতিত হইতেন। হজরত ইব্রাহিম বহির্জগতে তাঁহার ‘প্রিয়বস্তু’র খোঁজ করিয়া তাঁহার পুত্রকে পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি তাঁহার অন্তর্জগত খোঁজ করিলে কি পাইতেন?
গ) ‘কোরবানী’ কথাটির অর্থ ‘বলিদান’ না হইয়া, ‘উৎসর্গ’ হইতে পারে কিনা। ঈসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্তান উৎসর্গের নিয়ম আছে। কোন সন্তানকে তাহার পিতা-মাতা মহাপ্রভুর নামে উৎসর্গ করিতে পারেন। ঐরূপ উৎসর্গ করা সন্তানের কর্তব্য হয় — সর্বস্বত্যাগী হইয়া আজীবন ধর্মকর্ম ও মন্দির-মসজিদের সেবা করা। এই প্রথাটি ইহুদী জাতির মধ্যেও দেখা যায়। হজরত ঈসার মাতা বিবি মরিয়ম জেরুজালেম মন্দিরে উৎসর্গ করা একজন সেবিকা ছিলেন। সমস্ত নবীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন হজরত ইব্রাহিমের বংশধর। হজরত ইসমাইল, হজরত ইসহাক, হজরত ইয়াকুব, হজরত ইউসুফ, হজরত মুসা, হজরত ঈসা এবং হজরত মোহাম্মদ (দ.) পর্যন্ত সকলেই। ইসমাইল ও ইসহাক পুত্র, হজরত ইয়াকুব পৌত্র এবং হজরত ইউসুফ ছিলেন প্রপৌত্র। অন্যান্য নবীদের মধ্যেও সকলেই ছিলেন হজরত মোহাম্মদ (দ.)-এর পূর্ববর্তী এবং হজরত ইব্রাহিমের অনুসারী। ছেলেদের খাৎনা (ত্বকচ্ছেদ) করার প্রথাটি হজরত ইব্রাহিম প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং তাহা অন্যান্য নবীগণও পালন করিয়া গিয়াছেন। বিশেষত ইহুদী ও খৃষ্টানগণ উহা এখনও পালন করেন। কিন্তু স্বগোত্রীয় ও অনুসারী হইয়াও উহারা ‘কোরবানী’ প্রথাটি পালন করেন নাই। কিন্তু হজরত ইব্রাহিমের আবির্ভাবের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পর উহা প্রবর্তন হইল কেন?
ঘ) যাঁহারা স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনা করেন, তাঁহারা জানেন যে, স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নে যাহা কিছু দেখে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই থাকে ‘রূপক’। হজরত ইব্রাহিমের স্বপ্নের কোরবানীর দৃশ্যটি ‘রূপক’ হইতে পারে কিনা?
উপরোক্ত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, কোরবানী প্রথার ভিত্তিমুল সুদৃঢ় নয়। একটি স্বপ্নের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ পশুর জীবন নষ্ট হইতেছে। উপন্যাসকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিলে যেরূপ ভুল করা হয়, স্বপ্নের রূপককে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিলে সেইরূপ ভুল হইতে পারে না কি?
সে যাহা হউক, হজরত ইব্রাহিম যে একজন খাঁটি খোদাভক্ত ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যদি স্বপ্নাদেশের প্রিয়বস্তু বলিতে তাঁহার নিজ প্রাণকে বুঝিতেন, বোধ হয় যে, তাহাও তিনি দান করিতে কুন্ঠিত হইতেন না। আল্লাহর প্রেমে তিনি এত অধিক আত্মভোলা হইয়াছিলেন যে, তখন তাঁহার কাছে স্ত্রী, পুত্র ও ধনরত্নাদির কোন মূল্য ছিল না। তাই তিনি অম্লানবদনে তাঁহার প্রিয় পুত্র ইসমাইলের গলে ছুরি চালাইয়াছিলেন। হজরত ইব্রাহিমের সন্তান-বাৎসল্য যতই গভীর হউক আর না হউক, উহাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক ছিল, তাহা ‘পিতা ও পুত্র’। আজকাল যে সকল ব্যক্তি পশু কোরবানী করেন, তাহাদের সঙ্গে ঐ পশুর সম্পর্ক কি?
কোরবানীর পশুর সঙ্গে কোরবানীদাতার সম্পর্ক শুধু টাকার। তাহাও অনেক ক্ষেত্রে সুদ, ঘুষ, চোরাবাজারী, লোক ঠকানো ইত্যাদি নানা প্রকার অসদুপায়ে অর্জিত। কাজেই কোরবানীদাতা মনে করেন — ‘যত্র আয় তত্র ব্যয়’। মাঝখানে লাভ হয় কোরবানী করার যশ।
দেখা যায় যে, কেহ কেহ কোরবানীর দুই-তিন দিন পূর্বেই কন্যা-জামাতা ও আত্মীয়-বন্ধুদের দাওয়াত করেন এবং কোরবানীর দিন সকাল হইতে আটা-ময়দা ও চাউলের গুঁড়া তৈয়ারে ব্যস্ত থাকেন। কোরবানীর পশুর মাংস দিয়া মাংস-রুটির এক মহাভোজ হয়। হজরত ইব্রাহিম যখন ইসমাইলকে কোরবানী করিতে লইয়া গিয়াছিলেন তখন কি বিবি হাজেরাকে তিনি আটার রুটি তৈয়ার করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন?
কোরবানীর পশুর জবেহ হইতে আরম্ভ করিয়া — মাংস কাটা, বখরা ভাগ ইত্যাদি ও খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকে যত রকম হাসি-তামাসা, গল্প-গুজব ও পান-সিগারেটের ধুম। হজরত ইব্রাহিমের কোরবানীর সাথে ইহার পরিবেশগত কোন সামঞ্জস্য আছে কি?
হজরত ইব্রাহিমের কোরবানীর মূল বস্তু ছিল তাঁহার ‘প্রাণ’ কোরবানী করা। কেননা ইসমাইল তাঁহার প্রাণ-সমতুল্যই ছিলেন। বিশেষত তাঁহার ঔরসজাত বলিয়া তিনি তাঁহার প্রাণের অংশীদারও ছিলেন (ছিয়াশী বৎসর বয়ষ্ক সুবৃদ্ধ ইব্রাহিমের একই মাত্র সন্তান ইসমাইল)। তাই ইসমাইলকে কোরবানই করার মানে হজরত ইব্রাহিমের প্রাণকে কোরবানী করা। আর আজকাল যে কোরবানী করা হয়, তাহাতে কোরবানীর পশুর সাথে কোরবানীদাতার কোনরূপ স্নেহ বা মায়ার বন্ধন থাকে কি?
হজরত ইব্রাহিম আল্লাহর নির্দেশ মানিয়া শুধু কোরবানীই করেন নাই। আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে চলিতে যাইয়া তিনি নাকি ভীষণ অগ্নিকুণ্ডেও পতিত হইয়াছিলেন। হজরত ইব্রাহিমের পদাঙ্ক অনুসরণ বা তাঁহার কৃতকর্মের অনুকরণ করাই যদি তাঁহার অনুসারীদের উদ্দেশ্য হয়, তবে তিনি যেই তারিখে অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইয়াছিলেন, সেই তারিখে তাঁহারা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেন না কেন?
হজরত ইব্রাহিম তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়বস্তুই কোরবানী করিয়াছিলেন। বর্তমান কোরবানীদাতাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়বস্তু কি দশ-বিশ টাকা মূল্যের একটি পশু?
হজত ইব্রাহিমের খোদাভক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে ইসমাইল পাইয়াছিলেন। তাই নিজেকে কোরবানী করার বাণী শ্রবণে মহানন্দে তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন এবং পিতার ছুরিকার নীচে স্বেচ্ছায় শয়ন করিয়াছিলেন। আর বর্তমান কোরবানী প্রথায় পশুর সম্মতি থাকে কি? একাধিক লোকে যখন একটি পশুকে চাপিয়া ধরিয়া জবেহ করেন, তখন সে দৃশ্যটি বীভৎস বা জঘন্য নয় কি?
মনে করা যাক, মানুষের চেয়ে বেশী শক্তিশালী এক অসুর জাতি পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া, তাহারা পুণ্যার্থে মহেশ্বর নামক এক দেবতার নামে জোরপূর্বক মানুষ বলি দিতে আরম্ভ করিল। তখন অসুরের খাঁড়ার (ছুরির) নীচে থাকিয়া মানুষ কি কামনা করিবে? ‘মহেশ্বরবাদ ধ্বংস হউক, অসুর জাতি ধ্বংস হউক, অন্ধ বিশ্বাস দূর হউক’ — ইহাই বলিবে না কি?
হজরত ইব্রাহিম দ্বিধাহীন চিত্তেই ইসমাইলের গলে ছুরি চালাইয়াছিলেন। কিন্তু বলির শেষে দেখিলেন যে, কোরবানি হইয়াছে একটি দুম্বা, ইসমাইল তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। ঐ সময় দুম্বা কোরবানী না হইয়া প্রকৃতপক্ষে যদি ইসমাইলই কোরবানী হইতেন, তবে তাঁহার অনুকরণে মুসলিম জাহানে আজ কয়টি কোরবানী হইত?
হজরত ইব্রাহিমের কোরবানী দেওয়া হইল বটে, কিন্তু ইসমাইল কোরবানী হইলেন না এবং যে দুম্বাটি কোরবানি হইল, তাঁহার কেনা নয় এবং পালেরও নয়। অধিকন্তু উহা কোথা হইতে কিভাবে আসিল, তাহাও তিনি জানিলেন না। ঘটনাটি আজগুবি নয় কি?
কোরবানী প্রথায় দেখা যায় যে, কোরবানীর পশুর হয় ‘আত্মত্যাগ’ এবং কোরবানীদাতার হয় ‘সামান্য স্বার্থত্যাগ’। দাতা যে মূল্যে পশুটি খরিদ করেন, তাহাও সম্পূর্ণ ত্যাগ নহে। কেননা মাংসাকারে তাহার অধিকাংশই গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, সামান্যই হয় দান। এই সামান্য স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে যদি দাতার স্বর্গলাভ হইতে পারে, তবে কোরবানির পশুর স্বর্গলাভ হইবে কিনা? যদি না হয়, তবে ঐ সকল পশুর আত্মত্যাগের সার্থকতা কি? আর যদি হয়, তবে সকল পশুর হবে কিনা; অর্থাৎ অসদুপায়ে অর্জিত (হারাম) অর্থে দেওয়া কোরবানীর পশুর স্বর্গলাভ হইবে কিনা? যদি না হয়, তবে ঐ সকল পশুর অপরাধ কি?
বাইবেল তথা তৌরিতে পুণ্যার্থে বাহুল্যরূপে গোহত্যার বিবরণ পাওয়া যায়। হজরত ইব্রাহিম ঐ মতের প্রবর্তক বা সমর্থক ছিলেন এবং হজরত মোহাম্মদ (দ.) ঐ মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ গোপালন করিয়া আসিতেছে – দুগ্ধপ্রাপ্তির ও কৃষিকাজের জন্য। কিন্তু মরুময় আরবদেশে কৃষিকাজ নাই বলিলেই চলে। সুতরাং ওদেশে দুগ্ধবতী গাভী কাজে লাগিলেও বলদগুলি কোন কাজেই লাগে না। তাই আরব দেশের লোকে পুণ্যার্থেই হউক আর ভোজার্থেই হউক, বাহুল্যরূপে গোহত্যা করিতেন। কাজেই ঐ দেশীয় ধর্মশাস্ত্রগুলিতেও গোহত্যার ব্যবস্থা দেখা যায়। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে গোজাতি মানুষের পরম উপকারী পশু। কৃষিকাজের সহায়ক বলিয়া আর্যগণ গোহত্যা অন্যায় মনে করিতেন। তাই তাহাদের ধর্মশাস্ত্রেও ‘গোহত্যা মহাপাপ’ বলিয়া উল্লেখ আছে। আর্যগণ মনে করিতেন — গাভী আমাদিগকে দুগ্ধদান করে, সুতরাং সে মাত্রি-সমতুল্যা এবং বলদ কৃষিকাজের সহায়ক হইয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করে, তাই সে পিতৃ-সমতুল্য, কাজেই উহারা আমাদের সম্মানের ও পূজার পাত্র। অধিকন্তু হিন্দুগণ ছাগ ভক্ষণ করে, অথচ দুগ্ধদাতৃ বলিয়া ছাগী ভক্ষণ করে না। কিন্তু ‘দুগ্ধদাতৃ’ বলিয়া কোন পশুর প্রতি মুসলমানদের কৃতজ্ঞতা নাই।
কৃষিপ্রধান দেশগুলিতে আজও ব্যাপক ক্ষেত্রে গরুর দ্বারা কৃষিকাজ চলিতেছে। যদিও ক্বচিৎ ট্রাক্টরাদি দ্বারা যান্ত্রিক চাষাবাদের চেষ্টা চলিতেছে, উহা কবে যে গরুর চাহিদা মিটাইবে, তাহা আজও বলা যায় না। সুতরাং কৃষিপ্রধান দেশগুলিতে গোহত্যা ক্ষতিজনক নয় কি?
২২। পাথর চুম্বন কেন?
যে সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র মক্কা শহরে হজ্বক্রিয়া সম্পাদন করিতে যান তাঁহাদের কতগুলি বিশেষ নীতি পালন করিতে হয়। যথা — তওয়াফ (কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ), এহরাম বাঁধা, সাফা-মারওয়া দৌড়, কঙ্কর নিক্ষেপ ও ‘হেজরল আসোয়াদ’ নামক পাথর চুম্বন ইত্যাদি। শেষোক্ত ‘হেজরল আসোয়াদ’ একখানা কালো রং-এর পাথর। ঐ পাথরখানা নাকি পাহাড়াদির সাধারণ পাথর নয়। শোনা যায় যে, কোন এক সময় ঐ পাথরখানা বেহেস্ত (আকাশ?) হইতে পতিত হইয়াছিল। তাই মক্কার লোকে ঐ পাথরখানাকে যথেষ্ট তাজিম করিতেন। বহুদিন ঐ পাথরখানা উন্মুক্ত জায়গায় পতিত ছিল। অতঃপর পবিত্র কাবাগৃহ মেরামতের সময় ঐ পাথরখানা কাবাগৃহের দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথিয়া সযত্নে রক্ষা করা হইয়াছে। হাজীগণকে ঐ পাথরখানা সম্মানের সাথে চুম্বন করিতে হয়।
পিতা-মাতা স্নেহবশে শিশুদের মুখ চুম্বন করে এবং প্রেমাসক্তিবশে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মুখ চুম্বন করিয়া থাকে। যাহাকে চুম্বন করা হয়, তাহার মমতাবোধ বা সুখানুভূতি থাকা আবশ্যক। যাহার মমতাবোধ বা সুখানুভূতি নাই, তাহাকে চুম্বন করার কোন মূল্য থাকিতে পারে না। ‘হেজরল আসোয়াদ’ চেতনাবিহীন একখণ্ড নিরেট পাথর মাত্র। উহাকে চুম্বন করিবার উপকারিতা কি? উহাকে চুম্বন করিলে তাহাতে আল্লাহতা’লা খুশি হন কেন? নির্জীব ও অচেতন একখানা কালো পাথরকে এতোধিক সম্মান প্রদর্শনের কারণ — উহা বেহেস্তী পাথর। তাহাই নয় কি?
একদা হজরত ওমর (রা.) কাবার হেজরল আসোয়াদ পাথরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, “হে কালো পাথর, যদি রসুলুল্লাহ (দ.) তোমাকে চুম্বন না করিতেন, তবে আমি তোমাকে চুম্বন তো করিতামই না, বরং কাবাগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তোমাকে দূরে নিক্ষেপ করিতাম।” [১৫]
জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সুদূর অতীতকালে কোন নক্ষত্রের আকর্ষণের ফলে সূর্যের জ্বলন্ত বাষ্পীয় দেহের খানিকটা ছিন্ন হইয়া দূরান্তে গিয়া কুণ্ডলী পাকাইতে পাকাইতে পৃথিবীর জন্ম হয়। প্রথমত উহা জ্বলন্ত বাষ্পাকারে ছিল। ক্রমে শীতল হইয়া তরল অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। কালক্রমে আরও শীতল হইয়া পৃথিবীর বহির্ভাগ কঠিন হইতে থাকে। কিন্তু অভ্যন্তরভাগ তরল অবস্থায়ই থাকে। পৃথিবীর বহিরাবরণ শীতল ও কঠিন হইয়া সঙ্কুচিত হইবার ফলে ভূ-গর্ভস্থ তরল পদার্থের উপর যে পরিমাণ চাপ পড়িতে থাকে, অভ্যন্তরভাগের তরল পদার্থ তাপ ত্যাগ করিয়া ঐ পরিমাণ সঙ্কুচিত হইতে না পারিয়া সময় সময় পৃথিবীর বহিরাবরণ ভেদ করিয়া ফোয়ারার আকারে ঊর্ধে উঠিতে থাকে। এইরূপ তরল পদার্থের উদ্গীরণ সময় সময় এত অধিক শক্তিসম্পন্ন হইত যে, উহা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাহিরে চলিয়া যাইত এবং মহাকাশের শীতলস্পর্শে শীতল হইয়া কঠিন পাথরের আকার প্রাপ্ত হইত ও মহাকাশে ইতস্তত ভাসিয়া বেড়াইত। কালক্রমে পৃথিবী আরও শীতল ও কঠিন হইয়া প্রাণীবাসের যোগ্য হইয়াছে এবং মহাকাশে ঐ ভাসমান পাথরগুলি আজও ভাসিয়া বেড়াইতেছে। উহারা মহাকাশে ভাসিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কোন কোন সময় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সীমার ভিতরে আসিয়া পড়ে এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে ভূপতিত হইতে থাকে। ভূপতিত হইবার সময় বায়ুর ঘর্ষণে উহারা প্রথমত উত্তপ্ত হয়, পরে জ্বলিয়া উঠে। ঐ সকল পাথরকে ‘উল্কাপিণ্ড’ বলে। কিন্তু সাধারণ লোকে বলে ‘তারা খসা’।[১৬] উল্কাপিণ্ডগুলি ওজনে দুই-তিন ছটাক হইতে বিশ-পঁচিশ মণ বা ততোধিক ভারি হইয়া থাকে। যে সকল উল্কাপিণ্ড আকারে ছোট, তাহারা জ্বলিয়া মধ্যপথে নিঃশেষ হইয়া ভস্মে পরিণত হয় এবং যেগুলি আকারে বড়, তাহারা জ্বলিয়া নিঃশেষ হইতে পারে না, আধাপোড়া অবস্থায় সশব্দে ভূপতিত হয়। দহনের ফলে সাধারণত উহাদের রং হয় কালো।
ঐ রকম কোন উল্কাপিণ্ড লোকালয়ে পতিত হইলে লোকে উহা সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রক্ষা করে। ঐরূপ সংগৃহীত অনেক আধপোড়া উল্কাপিণ্ড বড় বড় মিউজিয়মে বিশেষত কলিকাতা মিউজিয়মেও রক্ষিত আছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উল্কার দেহ ও পৃথিবীর মাটি-পাথর একই উপাদানে গঠিত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, উল্কাপিণ্ডগুলি পৃথিবীর অংশবিশেষ এবং সুদূর অতীতকালে উহারা পৃথিবীতেই ছিল।
‘হেজরল আসোয়াদ’ পাথরখানা ঐরকম একখণ্ড উল্কাপিণ্ড নয় কি?
পঞ্চম প্রস্তাব
[প্রকৃতি বিষয়ক]
১। মানুষ ও পশুতে সাদৃশ্য কেন?
ধর্মাচার্যগণ বলেন যে, যাবতীয় জীবের মধ্যে মানুষ আল্লাহতা’লার শখের সৃষ্ট জীব। পবিত্র মক্কার মাটির দ্বারা বেহেস্তের মধ্যে আদমের মূর্তি গঠিত হইয়া বেহেস্তেই তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল।
জগতের যাবতীয় জীবের নাকি একই সময়ে সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু জগতের বিভিন্ন জীবের দেহ যথা — পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি কোন স্থানের মাটির দ্বারা কোথায় বসিয়া কখন সৃষ্টি করা হইয়াছিল এবং আদমের পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই উহারা এখানে বংশবিস্তার করিয়াছিল কিনা, উহাদের অনেকের সাথে অনেক বিষয়ে মানুষের সৌসাদৃশ্যের কারণ কি এবং আদমের দেহ ও বিভিন্ন জীবের দেহ একই বস্তু দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছিল কি?
আদম হইতে আদমী বা মানুষ জাতির উৎপত্তি — এই মতবাদের পর্যালোচনায় উপরোক্ত প্রশ্নগুলি স্বতই মনে উদিত হয় এবং আরও যে সকল প্রশ্ন জাগে, তাহার সামান্য আলোচনা করা যাইতেছে।
মানুষের রক্তের প্রধান উপাদান — শ্বেত কণিকা, লোহিত কণিকা, জল ও লবণ জাতীয় কিছু পদার্থ এবং দেহ বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় — লৌহ, কার্বন, ফসফরাস ও গন্ধকাদি কতিপয় মৌলিক পদার্থ। অন্যান্য জীবের রক্তের উপাদানও উহাই কেন?
জীবগণ আহার করে তাহাদের দেহের স্বাভাবিক ক্ষয় পূরণের জন্য। ইহাতে দেখা যায় যে, দেহের যে বস্তু ক্ষয় হইতেছে, তাহা পূরণ করিবার জন্যই আহারের প্রয়োজন। জীবজগতে যখন খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বিদ্যমান, তখন উহাদের দেহ গঠনের উপাদানও হইবে বহুল পরিমাণে এক। যেমন — বাঘ মানুষ ভক্ষণ করে, মানুষ মাছ আহার করে, আবার মাছেরা পোকা-মাকড় খাইয়া বাঁচিয়া থাকে ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, উহাদের একের শরীরের ক্ষয়মান পদার্থ অপরের শরীরে বর্তমান আছে। মাতৃহীন শিশু যখন গোদুগ্ধ পানে জীবন ধারণ করিতে পারে, তখন গাভী ও প্রসূতির দেহের উপাদান এক নয় কি?
প্লেগ, জলাতঙ্ক ইত্যাদি রোগসমূহ ইতর প্রাণী হইতে মানবদেহে এবং মানবদেহ হইতে ইতর প্রাণীতে সংক্রমিত হইতে পারে। ইহাতে উহাদের টিসু (Tissue) ও রক্তের সাদৃশ্য প্রমাণিত হয় না কি?
চা, কফি ও মাদক জাতীয় দ্রব্যাদি গ্রহণে এবং কতক বিষাক্ত দ্রব্য প্রয়োগে মানুষ ও পশুর একই লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে উভয়ের পেশী (Muscle) ও স্নায়ুর (Nerve) সাদৃশ্য প্রমাণিত হয় না কি?
গো-মহিষাদি লোমশ প্রাণী, মানুষও তাহাই। উহাদের শরীরে যেরূপ পরজীবী বাস করে, মানুষের শরীরেও তদ্রুপ উকুনাদি পরজীবী বাস করে। প্রজনন কার্যে মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। পূর্বরাগ, যৌনমিলন, ভ্রূনোৎপাদন, সন্তান প্রসব ও প্রতিপালন সকলই প্রায় এক রকম কেন?
মানুষের সন্তানোৎপাদনের শক্তির বিকাশ হয় যৌবনে। এই শক্তির (নারীর) পার্থিব বিকাশকে বলা হয় ‘রজঃ’। জীবমাত্রেই রজঃ না থাকিলেও স্তন্যপায়ী প্রায় সকল জীবকেই রজঃশীলা হইতে দেখা যায়। তবে বিভিন্ন জীবের যৌবনে পৌঁছিবার বয়স, ‘রজঃ’-এর লক্ষণ ও স্থিতিকাল এক নহে। তথাপি একজন মানবীর রজঃ বা ঋতুর অন্তর এক মাস (সাধারণত ২৮দিন) এবং একটি বানরীরও ঋতুর অন্তর এক মাস; আর একজন মানবীর গর্ভধারণকাল দশ মাস (দশ ঋতুমাস — ২৮০ দিন) এবং একটি গাভীরও ঐরূপ। ইহার কারণ কি? বিশেষত আদি নারী বিবি হাওয়া নাকি রজঃশীলা হইয়াছিল গন্দম ছেঁড়ার ফলে, কিন্তু অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীকুল রজঃশীলা হয় কেন?
মানুষের ন্যায় পশুপাখিদেরও সন্তানবাৎসল্য এবং সামাজিকতা আছে। সর্বোপরি মানুষের ভাষা আছে। কিন্তু পশু-পাখীদের ভাষা কি আদৌ নাই? মানুষ যেরূপ আহ, উহ, ইস ইত্যাদি অনেক প্রকার শব্দ দ্বারা হর্ষ, বিষাদ, ভয়, ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদি মানসিক ভাব ব্যক্ত করে, তদ্রুপ অনেক ইতর প্রাণীও কতগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। গৃহপালিত কুকুরের ঘেউঘেউ শব্দের পাঁচটি রকমভেদ আছে। ইহাতে শত্রুর আগমন বোধক শব্দ, হর্ষের শব্দ, বেদনার শব্দ ইত্যাদি লক্ষিত হয়। গৃহপালিত মোরগ প্রায় বারোটি শব্দ ব্যবহার করে। গাভীর হাম্বা রবে তিন-চারি প্রকার মনোভাব প্রকাশিত হয়। ইতর প্রাণী কথা যে একেবারেই বলিতে পারে না, এমন নহে। ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া ইত্যাদি পাখীরা মানুষের মতই কথা বলিতে শেখে। তাহা হইলে মানুষ ও জীব-জন্তুর ভাষায় পার্থক্য কোথায়? শুধু ধারাবাহিকতা ও ব্যাপকতায় নয় কি?
গরু, ঘোড়া, হাতি, বাঘ, শিয়াল, বিড়াল ইত্যাদি পশুরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী জীব, মানুষও তাহাই। ঐ সকল পশুর ও মানুষের রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ইত্যাদি এবং অভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্র — হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, প্লীহা, যকৃত, মূত্রযন্ত্র, পাকস্থলী ইত্যাদির গঠন, ক্রিয়া, সংযোজন ও অবস্থিতি তুলনা করিলে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। বিশেষত শিম্পাঞ্জী, গরিলা ও বানরের সহিত মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতির সাদৃশ্য যথেষ্ট। ইহার কারণ ক্রমবিবর্তন নয় কি?
২। আকাশ কি?
‘আকাশ’ বলিতে সাধারণত শুন্যস্থান বুঝায়। কিন্তু কোন কোন ধর্মাচার্য বলিয়া থাকেন যে, আকাশ সাতটি। ইহা কিরূপে হয়? যাহা শুন্য, তাহা সংখ্যা দ্বারা সূচিত হয় কিরূপে? যাঁহারা আকাশকে সংখ্যা দ্বারা বিভক্ত করেন, তাঁহারা ‘আকাশ’ বলিতে ‘গ্রহ’কে বুঝেন? কিন্তু গ্রহ তো সাতটি নহে, নয়টি (অধুনা ১০টি)। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান ইত্যাদি ধর্ম প্রবর্তন ও তৎসংক্রান্ত শাস্ত্রাদি প্রণয়ণকাল পর্যন্ত পরিচিত গ্রহের সংখ্যা ছিল ছয়টি। তবে রাহু, কেতু ও সূর্যকে গ্রহদলে ধরিয়া নামকরণ হইয়াছিল নবগ্রহ। প্রকৃতপক্ষে সূর্য গ্রহ নহে এবং রাহু ও কেতু হইল চন্দ্র ও পৃথিবীর ছায়া। প্রকৃত গ্রহ হইল বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি — এই ছয়টি। গ্রহরা আকাশ বা শুন্য নহে।
কেহ কেহ সপ্তাকাশকে পদার্থের তৈয়ারী বলিয়া মনে করেন। তাহারা বলেন যে, আকাশ প্রথমটি জলের, দ্বিতীয় লৌহের, তৃতীয় তাম্রের, চতুর্থ স্বর্ণের তৈয়ারী। উহারা আরও বলেন যে, ছাদে ঝুলান আলোর মত চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রাদি আকাশে ঝুলান আছে। কিন্তু এ সবের প্রমাণ কিছু আছে কি? কোন কোন ধর্মবেত্তা আকাশের দূরত্ব নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। কেননা বলা হইয়া থাকে যে, পৃথিবী হইতে প্রথম আসমান ও তদূর্ধে প্রত্যেক আসমান হইতে প্রত্যেক আসমান ও তদূর্ধে প্রত্যেক আসমান হইতে প্রত্যেক আসমান পাঁচশত বৎসরের পথ দূরে দূরে অবস্থিত।
কোন গতির সাহায্যে দূরত্ব নির্ণয় করিতে হইলে সেই গতির বেগও জানা দরকার। সে যুগে রেল, ষ্টিমার বা হাওয়াই জাহাজ ছিল না। সাধারণত পায়ে হাঁটিয়াই পথ চলিতে হইত। ‘পাঁচশত বৎসরের পথ’ এই বলিয়া যাঁহারা আকাশের দূরত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহারা উহা — হাতী, ঘোড়া, উট, গাধা বা মানুষের গতি অথবা হাঁটা গতি, না দৌঁড়ের গতি তাহা কিছু বলেন নাই। সে যাহা হউক, মানুষের পায়ে হাঁটা গতিই মাইলে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, ধর্মীয় মতে কোন আকাশের দূরত্ব কত মাইল।
যথারীতি আহার ও বিশ্রাম করিয়া একজন লোক সাধারণত দৈনিক বিশ মাইল পথ চলিতে পারে। তাহা হইলে এক চান্দ্র বৎসরে অর্থাৎ ৩৫৪ দিনে চলিতে পারে ৭ হাজার ৮০ মাইল। সুতরাং পাঁচশত বৎসরে চলিতে পারে ৩৫ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল। ধর্মীয় মতে ইহা প্রথম আকাশের দূরত্ব অর্থাৎ চন্দ্রের দূরত্ব। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল। উপরোক্ত হিসাবমতে চতুর্থ আকাশের দূরত্ব অর্থাৎ সূর্যের দুরত্ব ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৬০ হাজার মাইল। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে উহা প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। সে যাহা হউক, আকাশে যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক আছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ উহার দূরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন যান্ত্রিক ও গাণিত্যিক সূত্রে। কিন্তু ধর্মগুরুগণ উহা পাইলেন কোথায় কি সূত্রে?
ধর্মীয় মতে প্রথম আকাশ জলের তৈয়ারী এবং চন্দ্র সেই জলে ভাসিতেছে। অধুনা প্রথম আকাশে অর্থাৎ চন্দ্রের দেশে মানুষ যাওয়া-আসা করিতেছেন এবং তাঁহারা দেখিতেছেন যে, চন্দ্র ভাসিতেছে শূন্যে এবং সেখানে জলের নাম-গন্ধও নাই।
শাস্ত্রীয় মতে চতুর্থ আকাশের দূরত্ব দেড় কোটি মাইলেরও কম। অথচ আধুনিক বিজ্ঞানীগণ ৩ কোটি মাইলেরও অধিক দূরে শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে রকেট প্রেরণ করিতেছেন। কিন্তু কোথাও লোহা, তামা বা সোনার আকাশ (ছাদ) দেখিতেছেন না, সবটাই শুন্য।
ধর্মগুরুদের আকাশ বিষয়ক বর্ণনাগুলি অলীক কল্পনা নয় কি?
৩। দিবা-রাত্রির কারণ কি?
সাধারণত আমরা দেখিয়া থাকি যে, সূর্য প্রত্যহ পূর্বদিক হইতে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। কিন্তু সূর্য তো কোন জীব নয় যে, সে নিজেই দৌড়াইতে পারে। তবে সে চলে কি রকম? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, চতুর্থ আসমানে একখানা সোনার নৌকায় সূর্যকে রাখিয়া ৭০ হাজার ফেরেস্তা সূর্যসহ নৌকাখানা টানিয়া পূর্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে লইয়া যায় ও সারারাত আরশের নীচে বসিয়া আল্লাহর এবাদত করে এবং প্রাতে পুনরায় সূর্য পূর্বদিকে হাজির হয় (প্রচ্ছদ দ্রষ্টব্য)। পক্ষান্তরে হিন্দুদের পুরাণশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কশ্যপ মুনির ঔরসে তৎপত্নী অদিতির গর্ভে সূর্যের জন্ম হয়। এই হেতু সূর্যের আর এক নাম ‘আদিত্য’। ইনি সপ্ত অশ্বযুক্ত রথে চড়িয়া আকাশ ভ্রমণ করেন এবং অরুণ ঐ রথের সারথি।
জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, সূর্য এক জায়গায় দাঁড়াইয়া আছে আর তাহা হইতে প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া পৃথিবী স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর ২৪ ঘন্টায় একবার ঘুরপাক খায়। ইহাতেই দিবারাত্রি হয় এবং সূর্যকে গতিশীল বলিয়া আমাদের ভ্রম হয়।
যদিও ‘সূর্য এক জায়গায় দাঁড়াইয়া আছে’ — ইহা বলা হইল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য এক জায়গায় দাঁড়াইয়া নাই। পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতির ন্যায় সূর্যেরও দুইটি গতি আছে। সূর্য স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর প্রায় ২৭ দিনে একবার ঘুরপাক খাইতেছে এবং সে আমাদের নক্ষত্রজগতের ব্যাসের দূরে থাকিয়া প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৭৫ মাইল বেগে নক্ষত্রজগতের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।[১৭] ইহার একপাক শেষ করিতে সূর্যের সময় লাগে প্রায় সাড়ে বাইশ কোটি বৎসর। কিন্তু মানুষ তাহার সহজ দৃষ্টিতে সূর্যের এই দুইটি গতির কোনটিরও সন্ধান পায় না।
সে যাহা হউক, দিবা-রাত্রির যে তিনটি কারণ বর্ণিত হইল, ইহার মধ্যে প্রামাণ্য ও গ্রহণীয় কোনটি?
৪। পৃথিবী কিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত?
কেহ কেহ বলেন যে, পৃথিবী একটি বলদের শৃঙ্গের উপর আছে। কেহ বলেন, পৃথিবী একটি মাছের উপর এবং কেহ বলেন, পৃথিবী জলের উপর অবস্থিত। তাহাই যদি হয়, তবে সেই মাছ, বলদ বা জল কিসের উপর অবস্থিত? অধুনা বহু পর্যটক জল ও স্থল এবং বিমানপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহ ওসবের সাক্ষাত পান না কেন? বিশেষত পৃথিবী যদি বলদের শৃঙ্গের উপর অবস্থিত থাকে, তবে সেই বলদটির পানাহারের ব্যবস্থা কি? (প্রচ্ছদ দ্রষ্টব্য)
আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, পৃথিবী কোন কিছুর উপরই প্রতিষ্ঠিত নহে। পৃথিবীর কোন দৃশ্যমান অবলম্বন নাই। ইহার সকল দিকেই আকাশ বা শুন্যস্থান। ফুটবল খেলোয়াড়ের পায়ের আঘাতে একটি ফুটবল যেমন ভনভন করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে (শূন্যে) চলিতে থাকে, পৃথিবীও তদ্রুপ সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া উহার আকর্ষণে বাঁধা থাকিয়া শুন্যে ঘুরিতেছে। সূর্যের চারিধারে একবার ঘুরিয়া আসিতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা। ইহাকে বলা হয় সৌরবৎসর বা ‘বৎসর’। বাস্তব ঘটনা ইহাই নয় কি?
৫। ভূমিকম্পের কারণ কি?
কেহ কেহ বলেন যে, পৃথিবীধারী বলদ ভারাক্রান্ত হইয়া কখনও শৃঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করে এবং তাহার ফলে পৃথিবী কম্পিত হয়। যদি ইহাই হয়, তবে একই সময়ে পৃথিবীর সকল অঞ্চলে ভূমিকম্প হয় না কেন?
ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতে — আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ভূগর্ভস্থ অতিশয় উষ্ণ গলিত পদার্থের হঠাৎ স্পর্শে ফাটল পথে প্রবেশ করা সামুদ্রিক জলের বাষ্পীয় রূপ ধারণে উহা বিস্ফোরণের চেষ্টা বা অকস্মাৎ ভূস্তর ধ্বসিয়া যাওয়া ইত্যাদি কারণে ভূমিকম্প হয়।
আলোচ্য দুইটি মতের মধ্যে গ্রহণীয় কোনটি?
৬। বজ্রপাত হয় কেন?
কোন কোন ধর্মপ্রচারক বলিয়া থাকেন যে, স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত হওয়ার পরেও শয়তান স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিত এবং আল্লাহ কর্তৃক পৃথিবীতে প্রযোজ্য ভবিষ্যৎ কার্যাবলীর নির্দেশ পূর্বাহ্নেই জানিয়া আসিয়া পৃথিবীতে ভবিষ্যদ্বাণী করিত। পৃথিবীর লোক শয়তানের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে দেখিয়া তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিত। অর্থাৎ শয়তান যাহার মুখ দিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করাইত, তাহাকেই লোকে ভগবাণের ন্যায় বিশ্বাস করিত এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর কথা একেবারেই ভুলিয়া যাইত। এইরূপে শয়তান খোদাতা’লার বিরুদ্ধাচরণ করিত এবং লোকদিগকে কুপথে লইয়া যাইবার সুযোগ পাইত। কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (দ.)-এর জন্মের পরে স্বর্গরাজ্যে শয়তান যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে এবং উপরোক্ত পদ্ধতিতে মানুষকে বিপথে নিতে না পারে, এজন্য খোদাতা’লা শয়তানের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ চিরতরে নিষিদ্ধ করিয়া দেন এবং ফেরেস্তাগণ কড়া হুকুম দিয়া দেন, যেন শয়তান আর স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। অধিকন্তু শয়তান বিতাড়নের অস্ত্রস্বরূপ ফেরেস্তাগণকে বজ্রবাণ প্রদান করেন। যখনই শয়তান স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা করে, তখনই ফেরেস্তগণ শয়তানের উপর বজ্রবাণ নিক্ষেপ করেন। উহাকে আমরা ‘বজ্রপাত’ বলিয়া থাকি।
উপরোক্ত বিবরণ যদি সত্য হয়, তবে সকল সময় এবং বিনা মেঘে বজ্রপাত হয় না কেন? শীত ঋতুতে বজ্রপাত হইতে শোনা যায় না কেন? সাধারণত আকাশে চারি শ্রেণীর মেঘ জমিয়া থাকে, কিন্তু উহার সকল শ্রেণীর মেঘে বজ্রপাত হয় না কেন? চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে বজ্রপাত ছিল না কি?
সচরাচর দেখা যায় যে, অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানেই বজ্রপাত হয় বেশী। যথা — মাঠের উচু শস্যক্ষেত্র, বাগানের তাল-নারিকেলাদি বৃক্ষ, শহরের উচু দালানাদি, এমনকি মসজিদের চূড়াতেও বজ্রপাতের কথা শোনা যায়। শয়তান কি ঐ সমস্ত উচু জায়গায়ই বাস করে?
হিন্দুগণ বলিয়া থাকেন যে, দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ্রবাণ তৈয়ারী এবং উহা ব্যবহার করেন দেবরাজ ইন্দ্র, তাঁহার শত্রু নিপাতের জন্য। ‘জৈমিনিশ্চ সুমন্তুশ্চ বৈশম্পায়ন এবং চ। পুনস্ত্যঃ পুলহো জিষ্ণু ষড়েতে বজ্র বারকা’—এই মন্ত্রটি উচ্চারিত হইলে সেখানে বজ্রপাত হয় না।[১৮] পক্ষান্তরে মুসলমানগণ বলিয়া থাকেন, ‘লা হওলা অলা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহেল আলিউল আজিম’ — এই কালাম পাঠ করিলে সেখানে বজ্রপাত হয়না। এসবের পরীক্ষামূলক সত্য কিছু আছে কি?
বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বজ্রবারক (Lightning proof) ব্যবহার করিলে সেখানে বজ্রপাত হয় না। শহরে উচু দালানাদি তৈয়ার করিয়া ইঞ্জিনিয়ারগণ উহার উপরে ‘বজ্রবারক’ সন্নিবেশিত করেন এবং তাহাতে বজ্রপাত হইতে দালানাদি রক্ষা পাইয়া থাকে। তবে কি বজ্রবারক দেখিয়াই শয়তা দূর হয়? যদি তাহাই হয়, তবে শয়তান দূর করিবার জন্য অন্যরূপ কোসেস না করিয়া ‘বজ্রবারক’ ব্যবহার করা হয় না কেন?
বজ্রপাত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য কিছুটা জটিল। তবে সংক্ষিপ্ত এইরূপ — গ্রীস্মকালে কোন কোন অঞ্চলে সময়বিশেষে বায়ুর ঊর্ধগতি হয়। ঐ সময় ঐ অঞ্চলের আকাশে যদি মেঘ থাকে এবং সেই মেঘের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া যদি নিম্নগতিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সেই নিম্নগতিসম্পন্ন মেঘ ঊর্ধগতিসম্পন্ন বায়ুর সংঘর্ষের ফলে সময় সময় মেঘের জলকণা ভাঙ্গিয়া অণু ও পরমাণুতে পরিণত হয়। সংঘর্ষের মাত্রাধিক্যে কোন কোন সময় আবার ঐ সকল পরমাণু হইতে ইলেক্ট্রন ও প্রোটন মুক্ত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। এইরূপ বিদ্যুৎযুক্ত মেঘ আকাশে থাকিলে তন্নিম্ন ভূমিতে আর একদফা বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়, ইহাকে ‘আবিষ্ট বিদ্যুৎ’ বলে। এইরূপ অবস্থায় আকাশের বিদ্যুৎ ও মাটিস্থ আবিষ্ট বিদ্যুতের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ চলিতে থাকে। মাটিস্থ আবিষ্ট বিদ্যুৎ আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে মিশিবার জন্য ভূপৃষ্ঠের অপেক্ষাকৃত উচু স্থানে যাইয়া উকি মারিতে থাকে। বিদ্যুতাশ্রিত স্থানটি সূচাগ্রবৎ হইলে সেখানে বিদ্যুৎ জমিতে পারে না, অল্পে অল্পে মুক্ত হইয়া আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে মিশিয়া যায়। কিন্তু ঐ স্থানটি সূচাগ্রবৎ না হইলে সেখান হইতে বিদ্যুৎ মুক্ত হইতে পারে না। বরং ক্রমশ জমিয়া শক্তিশালী হইতে থাকে। আকাশের মেঘে যে বিদ্যুৎ থাকে, তাহা হইতে মাটির আবিষ্ট বিদ্যুতের শক্তি বেশী হইলে, তাহা আকাশের বিদ্যুৎকে টানিয়া ভূপাতিত করে। এইভাবে আকাশের বিদ্যুৎপতনকে আমরা আমরা বজ্রপাত বলি। বিদ্যুৎপতনের তীব্রগতির পথে যে সকল বায়বীয় পদার্থ ও ধূলিকণা থাকে, উহা জ্বলিয়া তীব্র আলোর সৃষ্টি হয় এবং বায়ু কম্পনের ফলে হয় শব্দ।
প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ, একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বজ্রপাত কেন উচুস্থানে হয়, কেন সকল মেঘে ও শীতকালের মেঘে হয় না, কেন উচু গাছ কাছে থাকিলে নীচু গাছে হয় না এবং বজ্রবারক ব্যবহার করিলে কেন সেখানে বজ্রপাত হয় না।
(ধর্মযাজকগণ আলোচ্য বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবেন কি?)
৭। রাত্রে সূর্য কোথায় থাকে?
আল্লাহর ‘আরশ’ কোথায় কোনদিকে জানি না। কিন্তু কোন কোন ধর্মপ্রচারক বলিয়া থাকেন যে, রাত্রে সূর্য থাকে আরশের নীচে। সেখানে থাকিয়া সূর্য সারারাত আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী করে এবং ভোরে পূর্বাকাশে উদয় হয়।
সৌর-বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সূর্য প্রায় ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার মাইল ব্যাসবিশিষ্ট অগ্নিপিণ্ড। উহার কেন্দ্রে তাপমাত্রা প্রায় ৬ কোটি ডিগ্রী এবং বাহিরের তাপমাত্রা প্রায় ৬ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।[১৯] প্রজ্জ্বলনরত সূর্যের দেহ হইতে সতত প্রচণ্ড তাপ ও সুতীব্র আলো বিকীর্ণ হইতেছে এবং সূর্যের সেই আলোর সীমার মধ্যে থাকিয়া পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘুরপাক খাইতেছে। ভূ-পৃষ্ঠের যে অংশ যখন সূর্যের দিকে থাকে, তখন সেই অংশে হয় দিন, অপর অংশে হয় রাত্রি।
পৃথিবীর যে অংশে আমরা বাস করি, তাহার বিপরীত দিকে আছে আমেরিকা রাজ্য। কাজেই আমরা যখন সূর্যের দিকে থাকি, তখন আমেরিকা থাকে বিপরীত দিকে। অর্থাৎ আমাদের দেশে যখন রাত্রি, তখন আমেরিকায় দিন এবং আমাদের দেশে যখন দিন, তখন আমেরিকায় রাত্রি। কাজেই রাত্রে সূর্য থাকে আমেরিকার আকাশে। এ বিষয়টি সত্য নয় কি?
৮। ঋতুভেদের কারণ কি?
কেহ কেহ বলেন যে, দোজখের দ্বার যখন বন্ধ থাকে, তখন শীত ঋতু হয় এবং যখন খোলা থাকে, তখন গ্রীস্ম ঋতু।
আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া এক বর্তুলাকার কক্ষে ঈষৎ হেলান অবস্থায় থাকিয়া পৃথিবী বার মাসে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ইহাতে সূর্য-রশ্মি পৃথিবীর উপর কখনও খাড়াভাবে এবং কখনও তেরচাভাবে পড়ে। সুতরাং যখন খাড়াভাবে পড়ে, তখন গ্রীস্ম এবং যখন তেরচাভাবে বা হেলিয়া পড়ে তখন হয় শীত ঋতু। আলোচ্য মত দুইটির মধ্য গ্রহণীয় কোনটি?
৯। জোয়ার-ভাটা হয় কেন?
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবীধারী বলদ যখন শ্বাস ত্যাগ করে তখন জোয়ার হয় এবং যখন শ্বাস গ্রহণ করে, তখন ভাটা। তাহাই যদি হয়, পৃথিবীর সব অঞ্চলে একই সময় জোয়ার বা ভাটা হয় না কেন?
বিজ্ঞানীদের মতে জোয়ার-ভাটার বিশেষ কারণ হইল চন্দ্রের আকর্ষণ। ভূ-পৃষ্ঠের যে কোন স্থানে চন্দ্র যখন মধ্যাকাশে থাকে, তখন সেই স্থানে চন্দ্রের আকর্ষণ জোরালো থাকে এবং চন্দ্র দিগন্তে থাকিলে তখন আকর্ষণ হয় ক্ষীণ। কাজেই চন্দ্র মধ্যাকাশে থাকিলে যেখানে জোয়ার হয়, দিগন্তে থাকিলে সেখানে ভাটা। অধিকন্তু ভূপৃষ্ঠের যে অংশে যখন জোয়ার বা ভাটা হয়, তাহার বিপরীত পৃষ্ঠেও তাহাই হয়, তাহার বিপরীত পৃষ্ঠেও তখন জোয়ার বা ভাটা হইয়া থাকে। তাই একই স্থানে জোয়ার বা ভাটা হয় দৈনিক (২৪ ঘন্টা) দুই বার।
আলোচ্য দুইটি মতের মধ্যে বাস্তব কোনটি?
১০। উত্তাপবিহীন অগ্নি কিরূপ?
শোনা যায় যে, বাদশাহ নমরূদ হজরত ইব্রাহিম (আ.)-কে বধ করিবার জন্য ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু আল্লাহতা’লার অসীম কৃপায় তিনি মারা যান নাই বা তাঁহার দেহের কোন অংশ দগ্ধ হয় নাই। বস্তুত এই জাতীয় ঘটনার কাহিনী জগতে বিরল নয়। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন কেচ্ছা-কাহিনীতে এরূপ অনেক ঘটনার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে।
সেকালে হিন্দুদের ধারণা ছিল যে, সতী নারী অগ্নিদগ্ধ হয় না। তাই রাম-জায়া সীতা দেবীকে অগ্নিপরীক্ষা করা হইয়াছিল। সীতা দীর্ঘকাল রাবণের হাত একাকিনী বন্দিনী থাকায় তাঁহার সতীত্বে সন্দেহবশত তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু উহাতে নাকি তাঁহার কেশাগ্রও দগ্ধ হয় নাই। আর আজকাল দেখা যায় যে, চিতানলে সতী বা অসতী, সকল রমণীই দগ্ধ হয়।
ইহাতে মনে হয় যে, হয়ত অগ্নিদেব দাহ্য পদার্থ মাত্রেই দহন করে, সতী বা অসতী কাহাকেও খাতির করে না, নতুবা বর্তমানকালে সতী নারী একটিও নাই।
হজরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে পার্শি ধর্মের প্রবর্তক জোরোয়াস্টার নিজদেহে উত্তপ্ত তরল ধাতু ঢালিয়া দিয়া অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইতেন। ক্যাপিডোসিয়ার অন্তর্গত ডায়ানার মন্দিরে পুরোহিতগণ উত্তপ্ত লাল বর্ণের লোহার উপর দিয়া যাতায়াত করিয়া লোকদিগকে স্তম্ভিত করিতেন। ভারতবর্ষে বিশেষভাবে বাংলাদেশে গাজন্নাথের সন্ন্যাসীগণ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়া যাতায়াত করিয়া লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিতেন।
জাপানের ‘সিন্ট’ পুরোহিতগণ তাঁহাদের ‘মাৎসুরী’র (উৎসবের) সময় অনেক অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইয়া থাকেন। সর্বশেষ্ঠ ক্রিয়াটির নাম ‘হাই ওয়াতারী’। অর্থাৎ জ্বলন্ত আগুনের উপর দিয়া যাতায়াত করা। জ্বলন্ত আগুনের উপর দিয়া পুরোহিতগণ তো হাঁটেনই, অধিকন্তু হাত ধরিয়া দর্শকদেরও হাঁটাইতে পারেন। ‘সিন্ট’ পুরোহিতগণ আর একটি বিভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, উহার নাম ‘কুগা-দুচী’ অর্থাৎ ফুটন্ত জলের দ্বারা স্নান করা।[২৩]
উপরোক্ত অগ্নিঘটিত বিভূতিগুলি সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর (Magician) পিসি সরকার মহাশয় বলিয়াছেন, বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে উহার ভৌতিক (অলৌকিক) অংশ চলিয়া যাইয়া ‘ম্যাজিক’ অংশটি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ তিনি উহার অধিকাংশই প্রদর্শন করিতে পারিতেন ও করিতেন।
বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, দহনের একমাত্র সহায়ক হইল ‘অক্সিজেন’। ইহা এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ। যেখানে অক্সিজেনের অভাব, সেখানে আগুন জ্বলে না। এই কারণেই বৃহদায়তনের কাঠের গুড়িতে আগুন ধরাইলে, উহার অভ্যন্তর বা কেন্দ্রভাগ জ্বলে না এবং বিপুল আয়তনের কাষ্ঠরাশিতে আগুন দিলেও উহার মধ্যভাগের কাষ্ঠ থাকে অদগ্ধ।
হজরত ইব্রাহিম (আ.) যখন ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াও দগ্ধ হইলেন না, তখন কি প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া অগ্নির দাহিকা শক্তি লোপ পাইয়াছিল, না বৃহদায়তন হেতু কাষ্ঠরাশির অভ্যন্তরভাগ অক্সিজেন-এর অভাবে অদাহ্যই ছিল?
শোনা যায় যে, আগের দিনে মুনি-ঋষিদের কেহ কেহ কুম্ভব প্রক্রিয়া দ্বারা নাকি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ রাখিয়া অর্থাৎ অক্সিজেন ছাড়া দীর্ঘ সময় বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেন। হযরত ইব্রাহিম (আ.) তাহা জানিতেন কি? নতুবা তিনি অক্সিজেনশূন্য স্থানে বাঁচিলেন কিরূপে?
১২। হযরত নুহ নবীর সময়ের মহাপ্লাবন পৃথিবীর সর্বত্র হইয়াছিল কি?
ধর্মাচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে, হযরত নুহের সময়ে নানাবিধ পাপাচার করায় মানুষ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে খোদাতা’লা পৃথিবীতে এক গজব (মহাপ্লাবন) নাজেল করেন। চল্লিশ দিবারাত্র অবিরাম বৃষ্টির ফলে সমস্ত পৃথিবী জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। এমনকি পর্বতের উপরেও ১৫ হাত জল জমিয়াছিল। পৃথিবীতে মানুষ, পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গাদি কোন প্রাণীই জীবিত ছিল না। হযরত নুহ তাহার জাহাজে যে সকল প্রাণীদের আশ্রয় দিয়াছিলেন, মাত্র তাহারাই জীবিত ছিল।
হযরত আদম হইতে হযরত নুহ দশম পুরুষ এবং উক্ত মহাপ্লাবন হইয়াছল হযরত আদমের জন্মের তারিখ হইতে ১৬৫৬ বৎসর পরে।[২০] মাত্র এক জোড়া মানুষ হইতে এত অল্প সময়ের মধ্যে তখন পৃথিবীতে মানুষ খুব বেশি জন্মিতে পারে নাই। বিশেষত সেকালের মানুষ ছিল শান্ত ও সরল প্রকৃতির। তথাপি তাহাদের পাপকার্য সহ্য করিতে না পারিয়া আল্লাহ জগতময় মহাপ্লাবন-রূপ গজব নাজেল করিলেন, আর বর্তমানে সহ্য করেন কিরূপে? বর্তমান জগতে পাপকর্ম নাই কি?
ধর্মীয় মতে ইরান, তুরান, ইরাক ও আরবের কোন কোন অংশেই তখন লোকের বসতি ছিল। বাকী এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় কোন লোকই ছিল না এবং আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া ছিল অজ্ঞাত। এমতাবস্থায় সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া মহাপ্লাবন হইবার কারণ কি এবং মানুষের পাপের জন্য অন্যান্য প্রাণীরা মরিল কেন?
মানুষের জীবন হরণ করা আজ্রাইল ফেরেস্তার কাজ। সে আল্লাহর আদেশ পাইলে যে কোন সময়ে, যে কোন অবস্থায়ই মানুষের ‘জান-কবজ’ করিয়া নিতে পারে এবং গুটিকতক পাপীর ‘জান-কবজ’ করা হয়ত তাহার এক মুহুর্তের কাজ। মানুষের মৃত্যুই যদি আল্লাহর কাম্য হইত, তবে তিনি আজ্রাইলকে দিয়া উহা এক মুহুর্তে করাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করাইয়া তিনি চল্লিশ দিন স্থায়ী প্লাবনের ব্যবস্থা করিলেন কেন?
ভূমণ্ডলে জলের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, আছে শুধু স্থানান্তর ও রূপান্তর। কোন দেশের উপর যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়, তৎসন্নিহিত সাগরাদির জল সেই পরিমাণ কমিয়া যায়। কেননা বাষ্পাকারে ঐ জল সাগরাদি হইতেই আসিয়া থাকে, আর জলের একটি বিশেষ ধর্ম এই যে, বাহিরের কোন শক্তির প্রয়োগ না হইলেও উহার উপরিভাগ থাকে সমতল।
অরারট পর্বতের চতুর্দিকেই ভিন্ন ভিন্ন সাগর অবস্থিত। যথা — কৃষ্ণ সাগর, কাস্পিয়ান সাগর, পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর, ভূমধ্যসাগর ইত্যাদি। অরারট পর্বতের চূড়ার উপর নাকি পনর হাত জল জমিয়াছিল এবং হজরত নুহের জাহাজখানা ঐ পর্বতের চূড়ায় আটকাইয়াছিল (তৌরিতে লিখিত অরারট পর্বতকে মুসলমানগণ বলে ‘যুদী’ পাহাড়)। কিন্তু ঐ পরিমাণে সাগরগুলির জল কমিয়াছিল কিনা? যদি কমিয়া থাকে, তাহা হইলে সাগরের নীচু জলের সহিত অরারট পর্বতের উচু জল চল্লিশ দিন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিল কিরূপে, জল কাত হইয়ছিল কি?
প্রবল প্রবাহের ফলে হয়ত সমুদ্রের জল আসিয়া কোন দেশ প্লাবিত করিতে পারে এবং বায়ুর বেগ প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ জল স্থলভাগের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু আলোচ্য প্লাবনে কোনরূপ বায়ুপ্রবাহ ছিল না, ছিল অবিরাম বৃষ্টি।[২১] ঐ প্লাবনে কোনরূপ ঝড়-বন্যা হওয়ার প্রমাণ আছে কি?
হজরত নুহের জাহাজখানা নাকি দৈর্ঘ্যে ৩০০ হাত, প্রস্থে ৫০ হাত ও উচ্চতায় ৩০ হাত ছিল এবং প্লাবনের মাত্র সাতদিন পূর্বে উহা তৈয়ারের জন্য খোদাতা’লার নিকট হইতে হযরত নুহ ফরমায়েশ পাইয়াছিলেন[২২]।
বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে লোহা-লক্কড়, কলকব্জা ও ইঞ্জিন-মেশিনের অভাব নাই। তথাপি ঐ মাপের একখানা জাহাজ মাত্র সাত দিনে কোন ইঞ্জিনিয়ার তৈয়ার করিতে পারেন না। হজরত নুহ উহা পারিলেন কিরূপে? নদ-নদী ও সাগরবিরল মরুদেশে সূত্রধর ও কাঠের অভাব ছিল না কি? বিশেষত কাঠ চেরাইয়ের যন্ত্র ছিল কি? অধিকন্তু ইহারই মধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গাদি জোড়া জোড়া এবং যাবতীয় গাছ-পালার বীজ সংগ্রহ করিয়া জাহাজে বোঝাই করিলেন কোন সময়?
উক্ত প্লাবনে নাকি পৃথিবীর সকল প্রাণীই বিনষ্ট হইয়াছিল, মাত্র জাহাজে আশ্রিত কয়েকটিই জীবিত ছিল। বর্তমান জগতের প্রাণীই নাকি ঐ জাহাজে আশ্রিত প্রাণীর বংশধর। তাহাই যদি হয়, তবে মানুষ ও পশু-পাখী সেখান হইতে আসিতে পারিলেও, কেঁচো ও শামুকগুলি বাংলাদেশে আসিল কিভাবে?
ষষ্ঠ প্রস্তাব
[বিবিধ]
১। আদম কি আদিমানব?
হিন্দু মতে ব্রহ্মার মানসপুত্র ‘মনু’ হইতে মানবের উৎপত্তি। ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানদের মতে ‘আদম’ হইতে আদমী বা মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে এবং পারসিকগণের মতে আদিমানব ‘গেওমাড’।
জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতে জীবসৃষ্টির আদিতে অতিক্ষুদ্র এককোষবিশিষ্ট জীব ‘এমিবা’ (Ameba) ক্রমবিবর্তন ও ক্রমবিবর্ধনের ফলে প্রথমে ব্যাক্টেরিয়া, তাহা হইতে স্পঞ্জ, মৎস, সরীসৃপ, পশু ইত্যাদি বহু জীবে রূপান্তরিত হইয়া শেষে বন-মানুষ (Anthorpaidape) ও তাহাদের ক্রমোন্নতির ফলে বর্তমান সভ্য মানুষ উৎপত্তি হইয়াছে। কয়েক কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর অবিচ্ছিন্ন জলরাশিতে ‘এমিবা’ জন্মলাভ করিয়াছিল এবং বিবর্তনের ফলে তাহা হইতে পৃথিবীর সর্বত্র নানাবিধ জীব সৃষ্টি হইয়াছে।
মানুষের আদি জন্ম সম্পর্কে এ সকল ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ শুনিয়া সাধারণ লোক কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারে কি? যে সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহারা মানুষকে সেই মতবাদই বিশ্বাস করাইতে চায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে ইহাতে যে সকল প্রশ্ন জাগে, তাহার কিছু আলোচনা করা যাক।
হিন্দু মতে মনুর জন্ম ভারতে এবং খৃষ্টানাদি সেমিটিক জাতির মতে আদমের প্রথম বাসস্থান আরব দেশে। অন্যান্য যে কোন মতেই হউক, মানুষের আদি জন্ম এশিয়ার বাহিরে নয়।
আদি মানব যদি এশিয়ায়ই জন্মলাভ করিয়া থাকিত, তাহা হইলে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যেই বসতি বিস্তার ঘটিত। কেননা ইহারা পরস্পর প্রায় অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীগণ কি প্রকারে জন্মিল? কলম্বাস সাহেবের আমেরিকা ও ক্যাপ্টেন কুক-এর অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পূর্বে সেখানে কি কোন লোক যাতায়াতের প্রমাণ আছে?
আদম যেখানে বাস করিতেন, তাহার নাম ছিল ‘এদন উদ্যান’। সেই উদ্যানটি বর্তমান তুরস্ক দেশের পূর্বাঞ্চলে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস (ফরাৎ ও হিদ্দেকল) নদীদ্বয়ের উৎপত্তির এলাকার মধ্যে অবস্থিত ছিল (৮নং টীকা দ্রষ্টব্য)। মহাপ্রভুর নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের অপরাধে আদম এদন উদ্যান হইতে বিতাড়িত হইয়া বহু বৎসর ঘোরাফেরার পর আরবের আরাফাতে তাঁহার স্ত্রীর সহিত মিলিত হন এবং ঐ অঞ্চলেই কালাতিপাত করেন।
আদিকালে পৃথিবীতে মানুষ ছিল অল্প এবং ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র মানুষের বসতি ছিল না, ছিল উর্বর অঞ্চলে। তাই প্রথম লোকবসতি ও সভ্যতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল নীল, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদী বিধৌত মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় এবং ভারতের সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে। কালদিয়া, ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতি দেশগুলিও ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর অববাহিকা অঞ্চল এবং ‘এদন’ স্থানটিও তাহাই।
জীববিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হইয়াছিল লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে। তবে আধুনিক চেহারার মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে মাত্র প্রায় ৩০ হাজার বৎসর পূর্বে। আদমের আবির্ভাবের সমকালে ও তাহারও পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে মানুষের বসতি ছিল, ভূতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাইয়াছেন। চীন ও ভারতাদির ন্যায় দূরদেশের কথা না-ই বলিলাম, আরবের নিকটবর্তী মিশর, প্যালেস্টাইন ও ব্যাবিলোন ইত্যাদির মত স্থানে মানব সভ্যতার যে অজস্র নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহার মধ্যে কয়েকটির আলোচনা করা যাইতেছে, যাহা আদমের সমকালীন বা তাহারও পূর্বের বলিয়া সাক্ষ্য দেয়। যথাঃ
খৃষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে হজরত আদম সৃষ্ট হন।
খৃষ্টপূর্ব ৩০৭৪ সালে হজরত আদমের মৃত্যু হয়।
খৃষ্টপূর্ব ৪২৪১ সালে মিশরে সিরিয়াস নক্ষত্রের আবিষ্কার হইতে বর্ষ গণনা আরম্ভ হয়।
খৃষ্টপূর্ব ৪৪৪১ সালে মিশরে ‘সোথিক চক্র’ আবিষ্কৃত হয় (ঊষাকালে উদয় হইতে মহাকাশ প্রদক্ষিণ
করিয়া সিরিয়াস নক্ষত্রটির আবার পূর্ব স্থানে ফিরিয়া আসিতে সময় লাগে প্রায়
১৪০০ বৎসর। এই সুদীর্ঘ কালটিকে বলা হয় ‘সোথিক চক্র’)।
খৃষ্টপূর্ব ৪২২১ সালে মিশরে পঞ্জিকা আবিষ্কৃত হয়।
খৃষ্টপূর্ব ৩০৯৮-৩০৭৫ সালে মিশরে নীলনদের পশ্চিমে গিজাতে রাজা খুফুর সমাধির উপর ১৩ একর জমি
ব্যাপিয়া ৪৮১ ফুট উচু একটি পিরামিড তৈয়ার হয়[৪৩]
খৃষ্টপূর্ব ৫০০০ সালের তৈয়ারী পাথরের হাতিয়ারের সহিত সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুর জিনিস পাওয়া
গিয়াছে মিশরের অন্তর্গত নেগাদা, এমিডোস, এল-আমরা প্রভৃতি অঞ্চলের
কবরগুলিতে।
খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ সালে মিশরে চাষাবাদ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে নীল নদের পশ্চিমে ফাইয়ুম ও
মেরিমডে অঞ্চলে এবং মধ্য ইরানের পশ্চিম সীমান্তে ‘সিয়ালফ’ অঞ্চলে।
খৃষ্টপূর্ব ৫০০৮-৪৫০০ সালে প্যালেস্টাইনের কারমেল পাহাড়ের ‘ওয়াদি এল-নাটুর্ফ’ স্থানের প্রাচীন অধিবাসী নাটুর্ফিয়ানরা কিছু চাষাবাদ করিত তাহার প্রমাণ আছে।
খৃষ্টপূর্ব ৪৩০০ সালের পূর্বের লোকবসতির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে পশ্চিম ইরানের কাশানের কাছাকাছি ‘টেল-শিয়ালফ’ স্থানে। সেখানে ১৭টি ভগ্নস্তূপে ৯৯ ফুট উঁচু একটি ঢিবির
সবচাইতে নীচের ভগ্নস্তূপটিতে লোকবসতির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।
খৃষ্টপূর্ব ৭০০০ সালে লোকবসতির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে মোসালের নিকটস্থ ‘টেপ পাওয়া’তে।
সেখানে ২৬টি ভগ্নস্তূপ মিলিয়া ১০৪ ফুট উঁচু একটি ঢিবির সবচাইতে নীচের
ভগ্নস্তূপটিতে লোকের বসতি ছিল।
খৃষ্টপূর্ব ৩৪০০ সালে মিশরে রাজা মেনেসের রাজত্ব আরম্ভ হয়।
খৃষ্টপূর্ব ৮০০০ সালে লোকবসতির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে সিরিয়ার উত্তর উপকূলে ‘বাস-সামরা’তে।
সেখানে ৪০ ফুট উঁচু একটি ঢিবির নীচে লোকবসতির চিহ্ন আছে।[৪৪]
পবিত্র তৌরিত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, “আর সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্বদিকে এদনে, এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন এবং সেই স্থানে আপনার নির্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমি হইতে সর্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখদায়ক বৃক্ষ এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে জীবনবৃক্ষ ও সদজ্ঞানদায়ক বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন। আর উদ্যানে জল সেচনার্থে এদন হইতে এক নদী নির্গত হইল, উহা তথা হইতে বিভিন্ন হইয়া চতুর্মুখ হইল।”[৪৫]
উক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, সদাপ্রভু পূর্বদিকে এদনে এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু উহা কোন স্থান হইতে পূর্ব — অর্থাৎ আদমের সৃষ্টির স্থান, না তৌরিত লেখকের বাসস্থান, তাহা স্পষ্ট বোধগম্য হয় না। হয়ত লেখকের বাসস্থানই হইবে। তৌরিতের লেখক বোধহয় কেনান দেশবাসী হিব্রু সম্প্রদায়ের কোন অনামা ব্যক্তি ছিলেন এবং এদন স্থানটি কেনান দেশ হইতে প্রায় পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। তৌরিতের বর্ণনামতে — সদাপ্রভু ভূমি হইতে সর্বজাতীয় ‘সুদৃশ্য’ ও ‘সুখাদ্যদায়ক’ বৃক্ষ ঐ বাগানে উৎপন্ন করিলেন। সচরাচর আমরা দেখিয়া থাকি যে, পরমেশ্বরের সৃষ্ট (প্রকৃতিজাত) গাছ-গাছড়ার সমাবেশকে কখনও বাগান বলা হয় না, বলা যায় ‘বন’ বা ‘জঙ্গল’। কেননা জল, বায়ু ও তাপের আনুকূল্যে উর্বর মাটিতে হরেক রকম উদ্ভিদই জন্মিয়া থাকে এবং উহাতে সুখাদ্য, কুখাদ্য ও সুদৃশ্য বৃক্ষের হয় একত্র সমাবেশ। অবাঞ্চিত বৃক্ষোৎপাটনপূর্বক ‘বাঞ্ছিত বৃক্ষ সমাবেশ’কে বলা হয় উদ্যান বা বাগান। এই ‘বাগান’ সর্বত্রই মানুষের তৈয়ারী, ঈশ্বরের নহে। যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি ঈশ্বর-সৃষ্ট (প্রকৃতিজাত) হইলেও অলঙ্কারসমূহ মানুষের তৈয়ারী, কোন অলঙ্কারই ঈশ্বর-সৃষ্ট নহে। কাজেই বলা যাইতে পারে যে, এদনের ঐ উদ্যানটি মানুষের তৈয়ারী ছিল, পরমেশ্বরের নহে।
জীবতত্ত্ববিদগণের মতে মানুষ এককালে গুহাবাসী ছিল এবং বন্য ফলমূল ভক্ষণ করিত। নিয়মিত ফলমূল সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য কাজ, হয়তবা ফলমূল দুষ্প্রাপ্যও ছিল। তাই আদিম মানবরা রুচিসম্মত ও সুখাদ্যদায়ক বৃক্ষাদি কোন নির্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিয়া খাদ্যের ব্যাপারে স্বনির্ভর হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। মানব সভ্যতার আদিতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এইরূপ ‘বাগান চাষ’-এর প্রচলন হইয়াছিল। এমতাবস্থায় মনে উদয় হইতে পারে যে, এদনের উল্লিখিত উদ্যানটি ঐরূপ একটি বাগান চাষেরই ক্ষেত্র।
আদম সৃষ্টি হইয়া সেইদিন বা তাহার পরের দিন হইতেই ঐ বাগানের ফল ভক্ষণ শুরু করিয়াছিলেন। কোন ফলের বীজ রোপিত হইলে তাহাতে বৃক্ষোৎপন্ন হইয়া দুই-চারিদিনের মধ্যেই ফল ধরে না, উহাতে বেশ কয়েক বৎসর সময়ের দরকার হয়। কাজেই একথা স্বীকার্য যে, ঐ বাগানের ফলোৎপাদক বৃক্ষসমূহ আদম সৃষ্টির বহুদিন পূর্বে রোপিত হইয়াছিল। এদন উদ্যানটি পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। কাজেই সেখানকার বাগানে জলসেচের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা ছিল অত্যধিক, তাহা তৌরিত গ্রন্থে উল্লেখ আছে। নিয়মিত জলসেচের সামান্য ত্রুটিতেও বাগানটি নষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। ইহাতে প্রশ্ন আসে যে, আদম সৃষ্টির পূর্বে উহার সেচকার্য করিত কে? উত্তরে স্বভবতই মনে আসে যে, আদমের পূর্বেও মানুষ ছিল।
সেচকার্য করিত ‘কে’ না বলিয়া ‘কাহারা’ বলাই সঙ্গত। কেননা সেই সেচকার্য সম্পাদন করা কাহারও একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যেহেতু বাগানটি আয়তনে ছোট ছিল না, বেশ বড়ই ছিল। তৌরিতে বর্ণিত আছে, “পরে তাঁহারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের রব শুনিতে পাইলেন, তিনি দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমন করিতেছিলেন, তাহাতে আদম ও তাঁহার স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে উদ্যানস্থ বৃক্ষুসমূহের মধ্যে লুকাইলেন।”[৪৬] যেহেতু আদম তখন উলঙ্গ ছিলেন।
‘বৃক্ষ’ বৃক্ষই, উহা লতা-গুল্ম বা ঝোপ নহে। আদম লুকাইয়াছিলেন উদ্যানস্থ ‘বৃক্ষসমূহের’ মধ্যে, কোন একটি বিশেষ বৃক্ষের আড়ালে বা কোন ঝোপের মধ্যে নহে। আম, জাম, তাল, নারিকেল, বিশেষত খেজুর (খুরমা) ইত্যাদি বৃক্ষের গোটা কাণ্ডই শাখা-পত্রহীন এবং উহাদের অবস্থানও সাধারণত দূরে দূরে। অধিকন্তু ‘স্বর্গ’ নামধেয় ‘এদন উদ্যান’টিতে যে ঝোপ-জঙ্গল ছিল না, তাহাও নিশ্চিত। এমতাবস্থায় সেখানে কোন লোক কাহারো দৃষ্টির আড়াল হইতে হইলে, তাহার যে কতটুকু দূরে যাওয়া আবশ্যক তাহা অনুমানসাপেক্ষ। এহেন বাগানটির রক্ষণাবেক্ষণ যথা — কোপান (বোধহয় সেটি ছিল লাঙ্গলচাষের পূর্ববর্তী কোদাল যুগ)[৪৭], বীজ সংগ্রহ ও উহা রোপণ-বপন, বিশেষত জলসেচ ইত্যাদি কাজে বহু লোকের আবশ্যক ছিল এবং আবশ্যক ছিল তাহাদের কঠোর পরিশ্রম। বহু লোকের একত্রে বসবাস এবং কোন এক সুর্দিষ্ট পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করিতে হইলে একজন অধিনায়কও থাকা দরকার। আর ইহা একটি চিরাচরিত নিয়ম যে, অধিনায়কের আদেশ অমান্যকারী ব্যক্তি শাস্তির যোগ্য।
শোনা যায় যে, স্বর্গবাসীরা কোনরূপ কায়িক শ্রম করেন না এমনকি কোন বৃক্ষের ফলও তাঁহারা ছিড়িয়া খান না বা উহা হাতে ধরিয়া মুখে দেন না, ঈপ্সিত ফল আপনি আসিয়াই স্বর্গবাসীর মুখে প্রবেশ করে। মনে হয় যে, এদন উদ্যানে আদম ছিলেন এই ধরণের একজন বাসিন্দা, তিনি কোন কাজ করিতেন না। তাই তিনি ছিলেন উদ্যানের অন্যান্যদের, বিশেষত অধিনায়কের (প্রভুর) অপ্রীতিভাজন।
প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী মর্গানের মতে — আদি মানবরা দলবদ্ধ হইয়া বসবাস করিত। সেই দল বা সমাজ ছিল জ্ঞাতিভিত্তিক। দলের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের থাকিত জ্ঞাতি সম্পর্ক। মর্গান তাহার নাম দিয়াছিলেন ‘গেনটাইল সোসাইটি’ বা জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজ বা ‘ক্লান’। ক্লানের বাসিন্দারা সকলে মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করিত। হয়ত এরূপ নিয়মও ছিল যে, কোন ব্যক্তি কোন কাজ না করিলে তাহার জন্য ক্লান-উৎপন্ন ফলাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ক্লানের নিয়ম মানিয়া চলে না, বা কোন কাজকর্ম করে না এমন অবাধ্য ব্যক্তির চরম শাস্তি ছিল বহিষ্করণ বা ক্লান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া। দলের সকলের সহিত মিলিয়া, সকলের উপর নির্ভর করিয়া, সকলের সহযোগিতায় বাঁচার চেষ্টা করিলেই বাচা সম্ভব ছিল, নচেৎ নয়। কোন দল হইতে কেহ বিতাড়িত হইলে, সে বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়-পর্বতে ঘুরিতে ঘুরিতে দিশাহারা হইত বা মারা যাইত।[৩৭]
পূর্বোক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করিলে মনে আসিতে পারে যে, আদম হয়ত এশিয়া মাইনর বা আর্মেনিয়া দেশের কোন ক্লানের বিতাড়িত ব্যক্তি এবং আরব দেশে আগন্তুক প্রথম মানুষ, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আদিম মানুষ নয়। হজরত আদমের আদিত্বের বাস্তব ও তত্ত্বগত কোন প্রমাণ আছে কি?
২। নীল নদের জল শুকাইল কেন?
কেহ কেহ বলেন যে, ফেরাউনের দাসত্বমুক্ত হইয়া বনিইস্রায়েলগণ মিশর ত্যাগ করিয়া স্বদেশে (কেনান দেশে) আসিবার সময় নীল নদ পার হইয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বনিইস্রায়েলগণ মিশরের যে অঞ্চলে বাস করিতেন, তাহার নাম ‘গোশন’ বা ‘রামিষেষ’ প্রদেশ। নীল নদ ইহার পশ্চিমে অবস্থিত। কাজেই সেখান হইতে কেনান দেশে (পূর্বদিকে) আসিতে হইলে নীল নদ পার হইতে হয় না, পার হইতে লোহিত সাগর বা সুয়েজ উপসাগর অথবা মোররাত বা তিমছাহ হ্রদ। তৌরিতে বলা হইয়াছে — সুপ সাগর।
ধর্মযাজকগণ বলেন যে, খোদাতা’লার হুকুমে হজরত মুসা তাঁহার হাতের (লাঠি) দ্বারা জলের উপর আঘাত করিতেই নদীর এপার হইতে ওপার পর্যন্ত একটি (মতান্তরে বারটি) রাস্তা হইয়া গেল এবং রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রাচীরের আকারে জলরাশি দাঁড়াইয়া রহিল। জলধির তলদেশ দিয়া শুকনা পথে বনিইস্রাইলগণ এপারে আসিলে, ফেরাউন সসৈন্যে ঐ পথ দিয়া বনিইস্রাইলগণের পশ্চাদ্ধাবন করিল। ফেরাউন ঐ পথের মধ্যভাগে আসিলে হঠাৎ জলপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং ফেরাউন সদলে ডুবিয়া মরিল।
আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বনিইস্রাইলদের বারোটি বংশ বা দলের জন্য বারোটি ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক রাস্তার মাঝখানে জলের প্রাচীর ছিল। ঐ সকল রাস্তায় চলিবার কালে এক দলের লোক অন্য দলের লোককে দেখিতে না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইল, ঐ সকল প্রাচীরের গায়ে জানালা এবং খিড়কীও হইয়াছিল।
বলা হইয়া থাকে যে, আল্লাহ হায়াত, মউত, রেজেক ও দৌলত — এই চারিটি বিষয় ভিন্ন আর সমস্ত কাজের ক্ষমতাই মানুষকে দান করিয়াছেন। আল্লাহ মানুষকে শিখাইয়াছেন রেল, ষ্টিমার, হাওয়াই জাহাজ, ডুবো জাহাজ ও রকেট তৈয়ার করিতে; তিনি শিখাইয়াছেন টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও ও টেলিভিশন তৈয়ার করিতে এবং আরও কত কিছু। কিন্তু এই পারমাণবিক যুগের কোন মানুষকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ জলের দ্বারা (বরফের নহে) প্রাচীর, জানালা, খিড়কী-কবাট ইত্যাদি তৈয়ার করা শিক্ষা দিলেন না কেন?
কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। ধর্মযাজকদের কথিত জলের প্রাচীর ও খিড়কী-কবাটাদির আখ্যান কতটুকু সত্য তাহা জানি না; কিন্তু ‘ফেরাউন’-এর মৃত্যু সম্পূর্ণ সত্য নহে। অনেকে মনে করেন যে, ‘ফেরাউন’ কোন বিশেষ ব্যক্তির নাম এবং সে হাজার বৎসর জীবিত ছিল। আসলে ‘ফেরাউন’ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয় এবং হাজার বৎসর বাঁচিয়াও ছিলেন না। সেকালের মিশরাধিপতিদের উপাধি ছিল ‘ফেরাউন’। ফেরাউনদের মধ্যে কেহ কেহ দুর্দান্ত ছিল বটে, কিন্তু কেহ কেহ ছিলেন গুণী-জ্ঞানী ও মহান ব্যক্তির অধিকারী। হজরত মুসার আমলে মিশরের ফেরাউন বা সম্রাট ছিলেন প্রথম ‘সেটি’র পুত্র দ্বিতীয় ‘রেমেসিস’। হজরত মুসার জন্মের আগের বৎসর খৃষ্টপূর্ব ১৩৫২ সালে তিনি সিংহাসন লাভ করেন এবং ৬৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া খৃ.পূ. ১২৮৫ সালে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।[২৪] ফেরাউন দ্বিতীয় রেমেসিস হাজার বৎসর জীবিত ছিলেন না। তবে তাঁহার ‘ফেরাউন’ উপাধিটি জীবিত থাকিতে পারে।
শোনা যায় যে, মিশরে ইস্রায়েল বংশের প্রতিষ্ঠাতা হজরত ইউসুফকে কূপ হইতে তুলিয়া বণিকগণ কেনান দেশ হইতে মিশরে নিয়া বিক্রয় করিয়াছিল। হজরত ইউসুফের ভাইগণ কেনানে দুর্ভিক্ষের সময় স্বদেশ হইতে মিশরে যাইয়া একাধিকবার খাদ্যশস্য আনিয়াছিলেন এবং শেষবারে হজরত ইয়াকুব নবীকে সঙ্গে লইয়া সপরিবারে কেনান দেশ হইতে মিশর যাইয়া সেখানে তাঁহারা স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহারা কেহ কখনও নদী বা সাগরে বাধা পান নাই। কিন্তু হজরত মুসা বাধা পাইলেন কেন?
বলা যাইতে পারে যে, পূর্ববর্তী মিশর ভ্রমণকারী কেনানীয়রা যে পথে মিশরে যাতায়াত করিতেন, হজরত মুসা ‘পলাতক’ বলিয়া সেপথে না চলিয়া শত্রুর অনুগমন ব্যর্থ করিবার জন্য বাঁকাপথে চলিয়া লোহিত সাগর বা সুয়েজ উপসাগর পার হইয়া সীনয় বা তুর পর্বতে পৌঁছিয়াছিলেন।
বনিইস্রায়েলগণের মিশর ত্যাগ করাকে কেহ কেহ ‘পলায়ন’ বলিয়া থাকেন। কিন্তু আসলে উহা পলায়ন বা গোপন ব্যাপার ছিল না। হজরত মুসার অভিশাপে নাকি ফেরাউন ও তাঁহার জাতির উপর ভয়ানক গজব নাজেল হইয়াছিল। সেই গজবে অতিষ্ঠ হইয়া ফেরাউন বনিইস্রায়েলগণকে তাঁহাদের স্বদেশে যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। বিশেষত বিশাল পশুপাল ও যাবতীয় মালামালসহ বনিইস্রায়েলদের যে সুবিশাল বাহিনী সংগঠিত হইয়াছিল তাহাতে নারী ও শিশু ছাড়া শুধু পুরুষের সংখ্যাই ছিল ছয় লক্ষ।২৪ এত লোকের রাষ্ট্রত্যাগ করার ঘটনাকে পলায়ন বা গোপন ব্যাপার বলা যায় কিরূপে?
হজরত মুসার মিশর ত্যাগ সম্বন্ধে তৌরিত কেতাবে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায় — “তখন রাত্রিকালেই ফরৌণ মোশি ও হারোনকে ডাকাইয়া বলিলেন, তোমরা উঠ, ইস্রায়েলদিগকে লইয়া আমার প্রজাদের মধ্য হইতে বাহির হও, তোমাদের কথানুসারে মেষপাল ও গো-পাল সঙ্গে লইয়া চলিয়া যাও এবং আমাকেও আশীর্বাদ কর। … আর সদাপ্রভু মিশ্রীয়দের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে (বনিইস্রায়েলগণকে) অনুগ্রহপাত্র করিলেন, তাই তাহারা যাহা চাহিল মিশ্রয়ীরা তাহাদিগকে তাহাই দিল। এইরূপে তাহারা মিশ্রীয়দের ধন হরণ করিল।”[২৬]
উক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, তখন ফেরাউন ও মিশরবাসীগণ সরল মনেই বনিইস্রায়েলগণকে মিশর ত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন ভাবিতেছিলেন যে, বনিইস্রায়েলগণ তাঁহাদের দেশের আপদস্বরূপ, উহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইতে পারিলেই তাঁহারা নিরাপদ হইবেন। তাই তাঁহারা বিস্তর ধনরত্ন দিয়াও বনিইস্রায়েলগণকে তাঁহাদের স্বদেশে যাইবার সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশ্য মিশরীয়দের এই মনোভাবের পরিবর্তন হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অনেক পরে। পুনঃ বনিইস্রায়েলগণকে আটক করিবার ইচ্ছা ফেরাউনের যখন হইয়াছিল, তখন পর্যন্ত বনিইস্রায়েলগণ মিশর অতিক্রম করিয়া ‘পীহহীরোত’ নামক স্থানের নিকট সমুদ্রতীরে শিবির স্থাপনান্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় হজরত মুসা নিশ্চিন্ত মনে সহজ ও সরলপথে পূর্বদিকে (স্বদেশের দিকে) না চলিয়া, বাঁকাপথ ধরিয়া প্রায় দুইশত মাইল দক্ষিণে যাইয়া লোহিত সাগর পাড়ি দেওয়ার হেতু কি?
কেহ কেহ বলেন যে, হজরত মুসা যে জলাশয় পার হইয়াছিলেন, পূর্বে উহা ভূমধ্যসাগরের সাথে যুক্ত ছিল এবং উহার গভীরতা ছিল নিতান্ত কম। উহা ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল বলিয়া পূর্বীয় বায়ুপ্রবাহের দরুন ভূমধ্যসাগরের পূর্বাংশে জল হ্রাস হইয়া উহা সম্পূর্ণ শুকাইয়া যাইত এবং ঐ বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হইলে পুনরায় উহা জলপূর্ণ হইত। যেমন আমাদের বাংলাদেশে দক্ষিণ বায়ুপ্রবাহে বঙ্গোপসাগরের জল আসিয়া দেশ প্লাবিত করে, পক্ষান্তরে উত্তরীয় বায়ুপ্রবাহে জল কমিয়া যায়। ইহার ফলে নদী ও উপকূলভাগের অগভীর স্থান শুকাইয়া যায়। এই মতের অনুকূলে তৌরিত গ্রন্থে একটি বিবরণ পাওয়া যায়। বিবরণটি এইরূপ — “তাহাতে সদাপ্রভু সেই সমস্ত রাত্রি পূর্বীয় বায়ু দ্বারা সমুদ্রকে সরাইয়া দিলেন ও তাহা বিশুষ্ক করিলেন। তাহাতে জল (গভীর ও অগভীর) দুই ভাগ হইল আর ইস্রায়েল সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল।”[২৭]
উক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, ঐ তারিখে সমস্ত রাত্রি পূর্বদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রায় বার ঘন্টা স্থায়ী বন্যা হইয়াছিল। কাজেই অগভীর জলাশয়টি শুকাইয়া যাওয়ায় বনিইস্রায়েলগণ প্রায় শুকনা পথেই উহা পার হইয়াছিলেন। উহাদের পথানুসরণ করিয়া ফেরাউন যখন ঐ জলাশয়ের মধ্যভাগে আসিলেন, তখন রাত্রি শেষ হইয়াছিল এবং বন্যাও থামিয়াছিল। কাজেই তখন অতি দ্রুত ভূমধ্যসাগরের জল আসিয়া ফেরাউনকে ডুবাইয়া মারিল। যেহেতু পূর্বীয় বায়ু কেবলমাত্র রাত্রেই প্রবাহিত হইয়াছিল এবং ভোরে উহা থামিয়াছিল। এই মর্মে তৌরিতের অন্যত্র লিখিত আছে, “তখন মোশি (মুসা) সমুদ্রের উপর হস্ত বিস্তার করিলেন, আর প্রাতঃকাল হইতে না হইতে সমুদ্র সমান হইয়া গেল। তাহাতে মিশ্রীয়েরা তাঁহার দিকেই পলায়ন করিল, আর সদাপ্রভু সমুদ্রের মধ্যে মিশ্রীয়দিগকে ঠেলিয়া দিলেন।”[২৮]
অধুনা কোন কোন গবেষক বলেন যে, হজরত মুসা ‘তিমছাহ হ্রদ’ পার হইয়াছিলেন। তখন উহাতে জোয়ার-ভাটা হইত। হ্রদ বা সমুদ্রোপকুলের জোয়ার-ভাটা এক আশ্চর্য ব্যাপার। আমাদের বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এরূপ দৃশ্য হয়ত কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবেন। উহাকে ‘সর ডাকা’ বা ‘বান ডাকা’ বলে।
ভাটার শেষে যেখানে শুকনা ভূমি দেখা যায়, জোয়ার হওয়ামাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে সেখানে হয় অথৈ জল। ঐ জল এত দ্রুতবেগে আসিয়া থাকে যে, পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকিলে, সেখানে যাইয়া কেহই বাঁচিতে পারে না। এমনকি সময় সময় অভিজ্ঞ লোকও মারা পড়ে।
ঐরূপ জলাশয় পার হইবার বিপদ ও উপায় অর্থাৎ জোয়ার ও ভাটা সম্বন্ধে বনিইস্রায়েলগণ বোধহয় পূর্বজ্ঞাত ছিলেন। হয়ত তাঁহারা জানিতেন যে, ভাটার প্রথমাবস্থায় ওপার হইতে যাত্রা না করিলে জোয়ারের পূর্বে এপারে পৌঁছিতে পারা যায় না। তাই ভাটার প্রথমাবস্থায় হ্রদে কিছু জল থাকিতেই হজরত মুসা তাঁহার হাতের আসা দ্বারা (অন্ধের পথ চলিবার মত) অগভীর স্থান নির্ণয়পূর্বক সদলে হ্রদ পাড়ি দিয়াছিলেন। ফেরাউনের তখন একমাত্র লক্ষ্য বনিইস্রায়েলগণকে আক্রমণ ও ধৃত করা, জোয়ার বা ভাটার প্রতি লক্ষ্য ছিল না। হয়ত শাহী উমরতবাসী ফেরাউনের ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞতাও ছিল না। তিনি ভাটার প্রথম বা শেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বনিইস্রায়েলগণ যখন এপারে আসিয়াছিলেন, ফেরাউন তখন মধ্যহ্রদে ছিলেন। এই সময় হঠাৎ বান ডাকিয়া জোয়ার আসিলে ফেরাউন দ্বিতীয় রেমেসিস সদলে ডুবিয়া মরিলেন (খৃ.পূ. ১২৮৫)।
হজরত মুসার জলাশয় পার হইবার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের মধ্যে বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য কোনটি?
৩। হজরত মুসা সীনয় পর্বতে কি দেখিয়াছিলেন?
শোনা যায়, হজরত মুসা মিশর হইতে সদলে বাহির হইবার পর তৃতীয় মাসের প্রথম দিনে সীনয় পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হন এবং তৃতীয় দিন ভোরে ঐ পর্বতের উপরে আল্লাহকে দেখিতে ও তাঁহার বাক্য শুনিতে পান। এই সম্বন্ধে তৌরিতের লিখিত বিবরণটি এইরূপ — “পরে তৃতীয় দিন প্রভাত হইলে মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎ এবং পর্বতের উপরে নিবিড় মেঘ হইল; আর অতিশয় উচ্চরবে তুরীধ্বনি হইতে লাগিল। পরে মোশি ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাত করিবার জন্য লোকদিগকে শিবির হইতে বাহির করিলেন আর তাহার পর্বতের তোলে দণ্ডায়মান হইল। তখন সমস্ত সীনয় পর্বত ধূমময় ছিল। কেননা সদাপ্রভু অগ্নিসহ তাহার উপর নামিয়া আসিলেন আর ভাটির ধূমের ন্যায় তাহা হইতে ধূম উঠিতে লাগিল এবং সমস্ত পর্বত অতিশয় কাঁপিতে লাগিল। আর তুরীর শব্দ ক্রমশ অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন মোশি কথা কহিলেন, এবং ঈশ্বর বাণী দ্বারা তাঁহাকে উত্তর দিলেন।”[২৯]
উক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, ঐদিন ভোরে সীনয় পর্বতে (কোহেতুরে) মেঘগর্জন, বিদ্যুৎচমক ও তুরীধ্বনি (শিলাবৃষ্টির সময়ে মেঘস্থিত অবিরাম গর্জন) হইতেছিল এবং মুসা মুহুর্মুহু বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার নুর (আলো) দর্শন করিয়াছিলেন, এই বলিয়া যে একটি আখ্যান আছে উহা মেঘগর্জন ও বিদ্যুতালোক হইতে পারে না কি?
প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ এরিখ ফন দানিকেনের মত ইহুদীদের আরাধ্য দেবতা ‘যিহোবা’ নিরাকার ঈশ্বর নহেন, তিনি ব্যক্তিসত্তার অধিকারী ভিন্ন গ্রহবাসী মানুষ। যিহোবার তূরপর্বতে অবতরণের আখ্যানটি আসলে ভিন্ন গ্রহবাসী কোন বৈমানিকের বিমানযোগে পৃথিবীতে আগমন ও তূরপর্বতে অবতরণ।
৪। হজরত সোলায়মানের হেকমত না কেরামত?
শোনা যায় যে, হজরত সোলায়মান একাধারে বাদশাহ এবং পয়গম্বর ছিলেন। পয়গম্বর হিসাবে তাঁহার প্রসিদ্ধি বোধহয় খুব বেশী ছিল না। কিন্তু ‘বাদশাহ’ হিসাবে বিশাল সাম্রাজ্য, বিভিন্ন জাতির উপর একাধিপত্য ও তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্যের বিষয় পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, তিনি সেই যুগের একজন প্রথম শ্রেণীর সম্রাট ছিলেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি।
কোন কোন ধর্মপ্রচারক বলিয়া থাকেন যে, হজরত সোলায়মান পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, এমনকি পিপীলিকারও ভাষা জানিতেন এবং উহারা তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিত; জ্বীন-পরী, দেও-দানব, এমনকি পবনও। অধিকন্তু তিনি হাওয়ায় উড়িতে পারিতেন।
হজরত সোলায়মান ইতর প্রাণীর ভাষা জানিতেন কি না এবং জ্বীন-পরীরা তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিল কি না, তাহা প্রশ্ন নহে। এখানে প্রশ্ন হইল এই যে, তিনি যে হাওয়ায় উড়িতে পারিতেন বলিয়া দাবী করা হয়, তাহা কি তাঁহার হেকমত, না কেরামত। অর্থাৎ তিনি কি কোন কৌশলে উড়িতেন, না আল্লাহর কৃপায় উড়িতেন? যদি তিনি আল্লাহর দয়ায়ই উড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে লক্ষাধিক পয়গম্বরের মধ্যে অপর কেহ উড়িতে পারিলেন না কেন? তাহাদের প্রতি কি আল্লাহর ঐরূপ অনুগ্রহ ছিল না?
লঙ্কেশ্বর রাবণের পুত্র মেঘনাদ (ইন্দ্রজিৎ)-এর শূন্যে উড়িবারও একটি প্রবাদ আছে। তিনি নাকি ছিলেন অসভ্য রাক্ষস জাতি এবং নানা দেব-দেবীর উপাসক। তিনি যে কোন কৌশলে উড়িতেন তাহা বলা যায় না এবং তিনি যে আল্লাহর রহমতে উড়িতেন, তাহাও কল্পনা করা যায় না। তবে তাঁহার বিমানে (রথে) আরোহণ সম্ভব হইল কিরূপে? উহা কি রামায়ণের কবি বাল্মীকির কল্পনা মাত্র? তাহাই যদি হয়, তবে সোলায়মানের বেলায় ঐরূপ হইতে পারে কি না?
ভগবানের দয়া অথবা জ্ঞানের ক্রিয়া, যাহাই হউক, হজরত সোলায়মানের বিমানে আরোহণ যে সত্য, তাহার প্রমাণ কি? তিনি কি শুধু স্বদেশেই উড়িতেন?
আধুনিক বিজ্ঞানীগণ বিদ্যুৎ ও পেট্রোল খরচ এবং নানারূপ দুর্ঘটনার (Accident) ভয়কে উপেক্ষা করিয়া সারেজাহান সফর করেন। হজরত সোলায়মান কি বিনা খরচে বিঘ্নহীন বিমানে আরোহণ করিয়াও দেশান্তর গমন করেন নাই? যদি করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে তৎকালের কোন সভ্য দেশের ইতিহাসে উহা লিপিবদ্ধ নাই কেন? চীনদেশ না হয় একটু দূরেই ছিল, গ্রীস বা মিশর দেশে কি তিনি কখনও যান নাই? অথবা সে দেশের ঐ যুগের কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বর্তমানে জানা যায় না কি?
হজরত সোলায়মান সিংহাসন লাভ করে খৃ.পূ. ৯৭১ সালে[৩০] এবং মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারতে আসেন খৃ.পূ. ৩৩০, সময়ের ব্যবধান মাত্র ৬৪১ বৎসর। ভারতবর্ষ হইতে গ্রীসের দূরত্ব হজরত সোলায়মানের বাসস্থান জেরুজালেমের দূরত্ব হইতে প্রায় ৭/৮ শত মাইল অধিক। তথাপি গ্রীসাধিপতি আলেকজাণ্ডার হাঁটিয়াই ভারতে আসিয়াছিলেন। আর হজরত সোলায়মান কি উড়িয়াও এ দেশে আসিতে পারিলেন না? যদি আসিয়াই থাকিতেন, তাহা হইলে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ঘটনা যখন এদেশের ঐতিহাসিকগণ ভুলিতে পারিলেন না, তখন হজরত সোলায়মানের ভারতে আগমনের বিষয় ভুলিলেন কিরূপে?
৫। যীশুখৃষ্টের পিতা কে?
‘পিতা’ — এই শব্দটিতে সাধারণত আমরা জন্মদাতাকেই বুঝিয়া থাকি, অর্থাৎ সন্তান যাহার ঔরসজাত তাহাকেই। কিন্তু উহার কতিপয় ভাবার্থও আছে। যেমন, শাস্ত্রীয় মতে পিতা পাঁচজন। যথা — অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, শ্বশুর, জন্মদাতা ও উপনেতা। কেহ কেহ আবার জ্ঞানদাতা অর্থাৎ শিক্ষাগুরু এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পিতৃতুল্য বলিয়া মনে করেন। এ মতে পিতা সাতজন।[৩১]
শোনা যায় যে, যীশুখ্রীষ্ট (হজরত ঈসা আ.) অবিবাহিতা মরিয়মের গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কেহ পিতা নাই, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু তিনি কি ভগবানের ঔরসে ভগবতীর গর্ভজাত গণেশের ন্যায় পুত্র? সেমিটিক জাতির প্রত্যেকেই ইহাতে বলিবেন, “না”। তবে তিনি ঈশ্বরের কোন শ্রেণীর পুত্র? ‘সৃষ্টিকর্তা’ বলিয়া যদি পরমেশ্বরকে ‘পিতা’ বলা যায়, তবে তিনি তাঁহার সৃষ্টি সকল জীবেরই পিতা, যীশুর একার নয়। মহাপ্রভুর দয়া-মায়া, ভালবাসা ইত্যাদি এমন কোন বিষয় আছে, যাহা অন্যান্য আম্বিয়াদের প্রতি ছিল না, যদ্বারা যীশু একাই মহাপ্রভুর পুত্রত্ব দাবী করিতে পারেন? মহাপ্রভু নাকি হজরত মুসাকে সাক্ষাতদান ও তাঁহার সাথে বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, হজরত সোলায়মানকে হাওয়ায় উড়াইয়াছিলেন এবং হজরত মোহাম্মদ (দ.)-কে মে’রাজে নিয়া তাঁহার সহিত নানাবিধ কথোপকথন করিয়াছিলেন। ইহারা কেহই মহাপ্রভুর পুত্র নহেন কেন? পক্ষান্তরে, তৎকালীন ইহুদীগণ রাষ্ট্র ও ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশে আরোহণ করাইয়া তাঁহার হস্ত ও পদে পেরেক বিদ্ধ করিয়া যখন অন্যায় ও নির্মমভাবে হত্যা করিল, তখন তাঁহার পিতা ন্যায়বান পুত্রের পক্ষে একটি কথাও বলিলেন না বা তাঁহাকে উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা করিলেন না। কোন পিতা তাঁহার পুত্রহত্যা দর্শনে নীরব ও নির্বিকার থাকিতে পারেন, এরূপ দৃষ্টান্ত কোথায়ও আছে কি?
হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে, খোদাতা’লা ফেরেস্তার মারফতে বিবি মরিয়মের প্রতি তাঁহার ‘বাণী’ পাঠাইয়াছিলেন এবং সেই বাণীর বদৌলতেই তাঁহার গর্ভ হইয়াছিল এবং তাহাতে যীশু জন্মিয়াছিলেন, তাই তিনি খোদার পুত্র বলিয়া আখ্যায়িত। তাহাই যদি হয়, তবে হজরত জাকারিয়া নবীর স্ত্রী ইলীশাবেত চিরবন্ধ্যাহেতু কোন সন্তানাদি না হওয়ায় বৃদ্ধা বয়সে ফেরেস্তার মারফতে খোদাতা’লার ‘বাণী’ প্রাপ্তিতে তাঁহার নাকি গর্ভ হইয়াছিল এবং সেই গর্ভে হজরত ইয়াহিয়া নবী জন্মলাভ করিয়াছিলেন। তিনি খোদার পুত্র নহেন কেন?
বিজ্ঞানীদের মতে — পুরুষের প্রধান জননেন্দ্রিয় শুক্রাশয় (Testes)। উহার ভিতর এক শ্রেণীর কোষ (Cell) আছে, তাহাকে বলা হয় শুক্রকীট। সেগুলি দেখিতে ব্যাঙাচির মত। কিন্তু এত ছোট যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তাহাদের দেখা যায় না। ইহারা শুক্রাশয়ের ভিতরে যথেচ্ছ সাঁতরাইয়া বেড়ায়।
শুক্রাশয়ের সাথে দুইটি সরু নল দিয়া মূত্রনালীর যোগ আছে। সঙ্গমের সময় শুক্রকীটগুলি ঐ নল বাহিয়া মূত্রনালীর ভিতর দিয়া স্ত্রীঅঙ্গে প্রবেশ করিতে পারে।
মেয়েদের প্রধান জননেন্দ্রিয় ডিম্বাধার (Ovaries)। ইহা তলপেটের ভিতর ছোট দুইটি গ্লাণ্ড। ইহার সহিত সরু নলের দ্বারা জরায়ুর যোগ আছে। ডিম্বাধারের ভিতর ডিম্বকোষ প্রস্তুত হইয়া পূর্ণতা লাভ করিলেই উহা নলের ভিতর দিয়া জরায়ুতে নামিয়া আসে।
স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সময়ে পুরুষের বীর্যের সহিত শুক্রকীট স্ত্রী-অঙ্গ দিয়া প্রবেশ করিয়া জরায়ুর ভিতর ঢোকে। সেখানে স্ত্রীর ডিম্বকোষ তৈয়ারী থাকে শুক্রকীটের আগমনের অপেক্ষায়। শুক্রকীটগুলি জরায়ুতে প্রবেশ করিয়াই লেজ নাড়িয়া (ব্যাঙাচির মত ইহাদের লেজ থাকে) সাঁতার কাটিয়া ডিম্বকোষের দিকে ছুটিয়া আসে। উহাদের মধ্যে মাত্র একটিই ডিম্বকোষের ভিতর ঢুকিতে পারে। কেননা একটি ঢোকামাত্রই ডিম্বকোষের বাহিরের পর্দায় এমন পরিবর্তন ঘটে যে, অন্য কোন শুক্রকীট ঢুকিতে পারে না। ডিম্বকোষের মধ্যে ঢুকিবার সময় শুক্রকীটের লেজটি খসিয়া বাহিরে থাকিয়া যায়।
মানুষের বেলায় সচরাচর প্রতিমাসে নির্দিষ্টদিনে একটি করিয়া ডিম্বকোষ স্ত্রীলোকের ডিম্বাধারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন জন্তুর তিন মাস, কোন জন্তুর ছয় মাস, কাহারো বা বৎসরান্তে একবার ডিম্বকোষ জন্মে। যদি সেই সময় শুক্রকীটের সঙ্গে মিলন না হয়, তবে দুই-চারিদিনের মধ্যেই ডিম্বকোষটি শুকাইয়া মরিয়া যায়। আবার যথাসময়ে (ঋতুতে) আর একটি প্রস্তুত হয়।
শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের মিলন হইলে, মিলনের পরমুহুর্ত হইতে ডিম্বকোষের মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। ডিম্বকোষের মধ্যে ঢুকিবার পর শুক্রকীটের কোষকেন্দ্র আরো বড় হইতে থাকে এবং খানিকটা বড় হইয়া ডিম্বকোষের কোষকেন্দ্রের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া যায়। নানা বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনের পর আরম্ভ হয় বিভাজন। একটি হইতে দুইটি, দুইটি হইতে চারিটি এবং তাহা হইতে আটটি, এইভাবে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া তিন সপ্তাহের মধ্যে ডিম্বকোষসমূহ সংখ্যায় বাড়িয়া গিয়া আয়তনে এত বড় হয় যে, তখন তাহাকে ‘ভ্রূণ’ বলিয়া চেনা যায়। মানুষের বেলায় শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু তখনও উহা ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। দুই মাস পরে পুরা এক ইঞ্চি হয় এবং তখন হইতে উহাকে ‘মানুষের ভ্রূণ’ বলিয়া চেনা যায়। পুরাপুরি শিশুর মত হইতে সময় লাগে আরও সাত মাস। ন্যূনাধিক নয় মাস পর জরায়ু বা মাতৃজঠর ত্যাগ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয় ‘মানব শিশু’।
নারী ও পুরুষের মিলনের অর্থই হইল শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের মিলন সাধন। নারী ও পুরুষের রতিক্রিয়া ব্যতীত শুক্র ও ডিম্বকোষের মিলন সম্ভব হইতে পারে। কোন পুরুষের বীর্য সংগ্রহপূর্বক তাহা যথাসময়ে কোন কৌশলে নারীর জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের মিলন ঘটাইতে পারা যায় এবং তাহাতে সন্তানোৎপত্তি হইতে পারে। কিন্তু কোনও না কোন প্রকারের যৌনমিলন ব্যতীত সন্তানোৎপত্তি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।
সমাজবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সভ্যতা প্রাপ্তির পূর্বে মানুষ ও পশু-পাখির আহার-বিহার, চাল-চলন ইত্যাদিতে বিশেষ পার্থক্য ছিল না, যৌন ব্যাপারেও না। তখন তাহাদের যৌনমিলন ছিল পশু-পাখীদের মতই যথেচ্ছ। কেননা তাহাদের মধ্যে বিবাহপ্রথা ছিল না। সেকালের অসভ্য মানবসমাজে কাহারো জনক নির্ণয় করা ছিল প্রায় দুঃসাধ্য। মানব সভ্যতার ক্রমবৃদ্ধির একটি মস্ত বড় ধাপ হইল বিবাহপ্রথার প্রবর্তন। ইহাতে মানুষের জনক নির্ণয় সাধ্যায়ত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ণায়ত্ত হইয়াছে কি? এ কথা বলিলে হয়ত অসত্য বলা হইবে না যে, সামাজিক তথা আনুষ্ঠানিক পরিণয়াবদ্ধ স্বামী বর্তমান থাকিতে উপস্বামী ধারণ সভ্য মানবসমাজে বিরল নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে কোন সন্তান জন্মিলে প্রায় সর্বত্র বিবাহিত স্বামীকেই বলা হয় শিশুর পিতা এবং মনে করা হয় ‘জনক’ (স্মরণ রাখা উচিত যে, ‘পিতা’ ও ‘জনক’ এক কথা নয়। ‘পিতা’ = পালনকর্তা এবং ‘জনক’ = জন্মদাতা)। এহেন অবস্থায় শিশুর জনক চিরকাল অপ্রকাশ্যই থাকিয়া যায়। কিন্তু জাতকের দৈহিক অবয়ব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, রুচি, ধর্মাধর্ম বা বিষয়বিশেষের প্রতি অনুরাগ-বিরাগ ইত্যাদি বিষয়সমূহে জনকের সহিত বহু সাদৃশ্য থাকে। কিন্তু উহা কেহ তলাইয়া দেখে না বা সকল ক্ষেত্রে দেখা সম্ভবও নয়।
যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের সময় সখরিয়া (হজরত জাকারিয়া আ.) নামক জনৈক ব্যক্তি ছিলেন ইহুদীদের ধর্মযাজক ও জেরুজালেম মন্দিরের সেবাইত বা পুরোহিত। শোনা যায় যে, যীশুর মাতা মরিয়মকে তাঁহার পিতা এমরান মরিয়মের তিন বৎসর বয়সের সময় জেরুজালেম মন্দিরের সেবাকাজের জন্য প্রেরণ করেন এবং সেখানে তিনি সখরিয়া কর্তৃক পালিতা হন।[৩২] সখরিয়ার কোন সন্তান ছিল না, তাঁহার ঘরে ছিলেন অতিবৃদ্ধা বন্ধ্যা স্ত্রী ইলীশাবেত।[৩৩]
সখরিয়া তাঁহার ১২০ বৎসর বয়সের সময় ফেরেস্তার মারফত পুত্রবর প্রাপ্ত হন ও তাহাতে ইলীশাবেত গর্ভবতী হন এবং ইহার ছয় মাস পরে ফেরেস্তার মারফতে পুত্রবর প্রাপ্ত হইয়া ১৬ বৎসর বয়সে মরিয়মও গর্ভবতী হন।
অবিবাহিতা মরিয়ম সখরিয়ার আশ্রমে থাকিয়া গর্ভবতী হইলে লোক-লজ্জার ভয়ে ধর্মমন্দির ত্যাগ করিয়া নিজ জ্ঞাতিভ্রাতা যোসেপের সঙ্গে জেরুজালেমের নিকটবর্তী বৈৎলেহম (বয়তুলহাম) নামক স্থানে গিয়া অবস্থান করেন এবং ঐ স্থানে যথাসময়ে এক খর্জুরবৃক্ষের ছায়ায় যীশুখ্রীষ্ট ভূমিষ্ঠ হন।
অবিবাহিতা মরিয়ম এক পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া (মরিয়ম ও সখরিয়ার স্বজাতীয়) ইহুদীগণ তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিতে থাকে এবং তাহারা মরিয়মের পালক পিতা সুবৃদ্ধ সখরিয়ার উপর ব্যভিচারের অপরাধ আরোপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। প্রথমত ইহুদীগণ সখরিয়াকে ধৃত করিবার চেষ্টা করে এবং সখরিয়া এক বৃক্ষকোটরে লুকাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহুদীগণ খোঁজ পাইয়া করাত দ্বারা ঐ বৃক্ষটি ছেদন করার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ সখরিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।[৩৪] মরিয়ম সদ্যোজাত শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া যোসেপের সঙ্গে রাত্রিকালে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মিশরে চলিয়া যান এবং সেখান হইতে গালীল প্রদেশের নাসরৎ নগরে যাইয়া কালাতিপাত করেন।[৩৫]
তৎকালে সে দেশের রাজার নাম ছিল হেরোদ, তিনি জাতিতে ছিলেন ইহুদী। তাই রাজ্য শাসিত হত তৌরিতের বিধানমতে। তৌরিতের বিধানমতে ‘ব্যভিচার’ ও ‘নরহত্যা’ — এই উভয়বিধ অপরাধেরই একমাত্র শাস্তি ‘প্রাণদণ্ড’।৩৬ এখানে ব্যভিচারের অপরাধে সখরিয়ার প্রাণদণ্ডের বিষয়টি জানা যায় বটে, কিন্তু সখরিয়াকে বধ করার অপরাধে কোন ইহুদীর প্রাণদণ্ডের বিষয় জানা যায় না। ইহাতে ধারণ হইতে পারে যে, সখরিয়া নিরপরাধ হইলে, তাঁহাকে বধ করার অপরাধে নিশ্চয় ঘাতক ইহুদীর প্রাণদণ্ড হইত। কেননা সখরিয়া ছিলেন তৎকালীন ইহুদী সমাজের একজন উচ্চস্তরের ব্যক্তিত্বশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি।
এতদ্বিষয়ে পর্যালোচনা করিলে মনে স্বতই প্রশ্ন জাগে যে, যীশুখ্রীষ্টের জনক মহাপ্রভু, না সখরিয়া?
(যীশুর প্রসঙ্গে — হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত মহর্ষি পরাশরের ঔরসে অবিবাহিতা মৎস্যগন্ধার গর্ভজাত মহামনীষী ব্যাসের কাহিনী অনুধাবনযোগ্য। তবে উহাতে পরাশরের বিকল্পে স্বর্গদূতের পরিকল্পনা নাই।)
৬। জ্বীন জাতি কোথায়?
শোনা যায় যে, এই জগতে জ্বীন নামক একজাতীয় জীব আছে। তাহাদের নাকি মানুষের মত জন্ম, মৃত্যু, পাপ-পুণ্য এবং পরকালে স্বর্গ বা নরকবাসের বিধান আছে। কোন জীব যদি পাপ-পুণ্যের অধিকারী হয়, তবে সে জাতি যে জ্ঞানবান, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অদ্যাবধি পৃথিবীতে জ্বীন জাতির অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ক্যাপ্টেন কুক, ড্রেক, ম্যাগিলন প্রভৃতি ভূ-পর্যটকগণের পর্যটনের ফলে পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত দেশ নাই বলিলেই চলে। কিন্তু জ্বীন জাতির অস্তিত্বের সন্ধান মিলিল কৈ? তবে কি তাহারা গ্রহ-উপগ্রহ বা নক্ষত্রলোকে বাস করে?
দশটি গ্রহ এবং তাহাদের গোটা ত্রিশেক উপগ্রহ আছে। খুব শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যেও ঐ সকল গ্রহ বা উপগ্রহে কোনরকম জীবের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আর যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, নক্ষত্রগুলি সবই অগ্নিময় এবং উহাদের তাপমাত্র কোনটিরই দুই হাজার ডিগ্রীর কম নয়, কোন কোনটির তেইশ হাজার ডিগ্রীর উপর। সেখানে কোনরূপ জীব বাস করা দূরের কথা, জন্মিতেই পারে না। যদি বা পারে, তাহা হইলে বাসিন্দাদের দেহও হওয়া উচিত অগ্নিময় এবং কেহ কেহ বলেনও তাহাই। বলা হয় যে, জ্বীনগণ আগুনের তৈয়ারী। তাহাই যদি হয়, তবে তাহাদের পরকালে আবার দোজখ বা অগ্নিবাস কিরূপ? পক্ষান্তরে তাহারা যদি এই পৃথিবীতেই বাস করে, তবে তাহারা কোন (অদৃশ্য) বস্তুর তৈয়ারী?
ইহুদীশাস্ত্রে ‘শেদিম’ নামে এক শ্রেণীর কাল্পনিক জীবের বর্ণনা পাওয়া যায়। জ্বীনগণ তাহাদের প্রেতমূর্তি নয় কি?
৭। সূর্যবিহীন দিন কিরূপ?
দিন, রাত, মাস ও বৎসরের নিয়ামক সূর্য এবং গতিশীল পৃথিবী। ইহার কোনটিকে বাদ দিয়া আমরা দিবা, রাত্রি, মাস ও বৎসর কল্পনা করিতে পারি না। কেননা সূর্য থাকিয়াও পৃথিবী বিশেষত তাহার গতি না থাকিলে পৃথিবীর একাংশে থাকিত চিরকাল দিবা এবং অপর অংশে থাকিত রাত্রি। সেই অফুরন্ত দিন বা রাত্রিতে মাস বা বৎসর চিনিবার কোন উপায় থাকিত না। পক্ষান্তরে সূর্য না থাকিয়া শুধু গতিশীল পৃথিবীটি থাকিলে, সে চিরকাল অন্ধকারেই ঘুরিয়া মরিত, দিন-রাত-মাস-বৎসর কিছুই হইত না।
শোনা যায় যে, এস্রাফিল ফেরেস্তা যখন আল্লাহর আদেশে শিঙ্গা ফঁকিবেন, তখন মহাপ্রলয় হইবে। তখন পৃথিবী এবং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদির বিলয় হইবে। একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না। এমনকি যে এস্রাফিল শিঙ্গা ফুঁকিবেন তিনিও না। এহেন অবস্থায় চল্লিশ দিন (মতান্তরের ৪০ বৎসর) পরে আল্লাহ এস্রাফিলকে পুনঃ সৃষ্টি করিবেন এবং আল্লাহর হুকুমে তিনি পুনরায় শিঙ্গা ফুঁকিবেন, ফলে পুনরায় জীব ও জগৎ সৃষ্টি হইবে।
মহাপ্রলয়ের (কেয়ামতের) পরে সূর্য বা তদনুরূপ আলোবিকিরণকারী কোন পদার্থই থাকিবে না। এইরূপ অবস্থার পরে এবং পুনঃ সৃষ্টির পূর্বে ‘চল্লিশ দিন বা বৎসর’ হইবে কিরূপে? যদি বা হয়, তবে ঐ দিনগুলির সহিত রাত্রিও থাকিবে কি? থাকিলে, সূর্য ভিন্ন সেই ‘দিন’ ও ‘রাত্রি’ কিরূপে হইবে? আর দিনের সঙ্গে রাত্রি না থাকিলে, অবিচ্ছিন্ন আলোকিত ‘দিন’-এর সংখ্যা ‘চল্লিশ’ হইবে কিভাবে?
৮। ফরায়েজে ‘আউল’ কেন?
মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি তাহার ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টনব্যবস্থাকে বলা হয় ‘ফরায়েজ নীতি’। ইহা পবিত্র কোরানের বিধান। মুসলিম জগতে এই বিধানটি যেরূপ দৃঢ়ভাবে প্রতিপালিত হইতেছে, সেরূপ অন্য কোনটি নহে। এমনটি পবিত্র নামাজের বিধানও নহে। ইহার কারণ বোধহয় এই যে, ফরায়েজ বিধানের সঙ্গে জাগতিক স্বার্থ জড়িত আছে। কিন্তু পবিত্র নামাজের সাথে উহা নাই। থাকিলে বোধ হয় যে, নামাজীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইত। সে যাহা হউক, এই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধানটিতেও একটি ‘আউল’ দেখা যায়। ‘আউল’ কথাটির ধাতুগত অর্থ যাহাই হউক, এতদ্দেশে উহাতে মনে করা হয় — ‘অগোছাল’ বা ‘বিশৃঙ্খল’।
ফরায়েজ বিধানের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায়, মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি তাহার ওয়ারিশগণের মধ্যে নির্ধারিত অংশ মোতাবেক বন্টন করিলে কেহ পায় এবং কেহ পায় না। উদাহারণস্বরূপ দেখানো যায় যে, যদি কোন মৃত ব্যক্তির মা, বাবা, দুই মেয়ে ও এক স্ত্রী থাকে, তবে মা ১/৬ , বাবা ১/৬ , দুই মেয়ে ২/৩ , এবং স্ত্রী ১/৮ অংশ পাইবে। কিন্তু ইহা দিলে স্ত্রী কিছুই পায় না। অথচ স্ত্রীকে দিতে গেলে সে পাইবে ১/৮অংশ। এ ক্ষেত্রে মোট সম্পত্তি ‘১’-এর স্থলে ওয়ারিশগণের অংশের সম্পত্তি হয় ১ ১/৮। অর্থাৎ ষোল আনার স্থলে হয় আঠার আনা। সমস্যাটি গুরুতর বটে।
মুসলিম জগতে উক্ত সমস্যাটি বহুদিন যাবত অমীমাংসিতই ছিল। অতঃপর সমাধান করিলেন হজরত আলী (রা.)।[৪০] তিনি যে নিয়মের দ্বারা উহার সমাধান করিয়াছিলেন, তাহার নাম ‘আউল’।
হজরত আলী (রা.)-এর প্রবর্তিত ‘আউল’ বিধানটি এইরূপঃ
মৃত — অনামা ব্যক্তি (ফরায়েজ মতে)
মা বাবা মেয়ে (২) স্ত্রী
১/৬ ১/৬ ২/৩ ১/৮
প্রথমত উক্ত রাশি চারিটিকে সমান হরবিশিষ্ট করিতে হইবে এবং তাহা করিলে উহা হইবে —
৪/২৪ ৪/২৪ ১৬/২৪ ৩/২৪
ইহার যোগফল হইবে ২৭/২৪ । অতএব দেখা যাইতেছে যে, যেখানে মূল সংখ্যা (হর) ছিল ২৪, সেখানে অংশ বাড়িয়া (লব) হইয়া যাইতেছে ২৭। সুতরাং ‘২৭’-কেই মূল সংখ্যা (হর) ধরিয়া অংশ দিতে হইবে। অর্থাৎ দিতে হইবে—
৪/২৭ + ৪/২৭ + ১৬/২৭ + ৩/২৭ = ২৭/২৭ = ১ ।
পবিত্র কোরানে বর্ণিত আলোচ্য ফরায়েজ বিধানের সমস্যাটি সমাধান করিলেন হজরত আলী (রা.) তাঁহার গাণিতিক জ্ঞানের দ্বারা এবং মুসলিম জগতে আজও উহাই প্রচলিত। এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই মনে উদয় হয় যে, তবে কি আল্লাহ গণিতজ্ঞ নহেন? হইলে, পবিত্র কোরানের উক্ত বিধানটি ত্রুটিপূর্ণ কেন?
আল্লাহ পবিত্র কোরানে পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে, যাহারা আল্লাহর হুকুম পালন করিয়া তাঁহার ফরায়েজ আইন মান্য করিবে, তাহারা বেহেস্তী হইবে এবং অমান্যকারীরা হইবে দোজখী। যথা — “ইহা অর্থাৎ এই ফরায়েজ আইন ও নির্ধারিত অংশ আল্লাহর সীমারেখা এবং আল্লাহর নির্ধারিত অংশসমূহ। যাহারা আল্লাহর আদেশ এবং তাঁহার রসুলের আদেশ মান্য করিবে, তাহাদিগকে আল্লাহ বেহেস্তে স্থান দান করিবেন…।[৩৮]
পুনশ্চ “যে কেহ আল্লাহর আদেশ, আল্লাহর আইনে নির্ধারিত অংশ ও তাঁহার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে আল্লাহ দোজখবাসী করিবেন, তথায় সে চিরকাল থাকিবে এবং তথায় তাহার ভীষণ অপমানজনক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।”[৩১]
পবিত্র কোরানে বর্ণিত ফরায়েজ বিধানের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে কতগুলি (হজরত আলীর প্রবর্তিত) ‘আউল’ নীতির পর্যায়ে পড়ে এবং উহাতে কোরান মানিয়া বন্টন চলে না, আবার ‘আউল’ মানিলে হইতে হয় দোজখী। উপায় কি?
ফরায়েজ বিধানের একশ্রেণীর ওয়ারিশকে বলা হয় ‘আছাবা’। অর্থাৎ অবশিষ্টভোগী। মৃতের ওয়ারিশগণের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা আছাবাগণ পাইয়া থাকে। আছাবাদের মধ্যে অংশ বন্টনের একটি বিশেষ নিয়ম এই যে, নিকটবর্তী ওয়ারিশ একজনও থাকিলে দূরবর্তী কেহ অংশ পায় না এবং এই নিয়মের ফলেই পুত্র থাকিলে পৌত্র (নাতি) কিছুই পায় না। কিন্তু অধুনা রাষ্ট্রীয় বিচারপতিগণ পুত্র থাকিলেও পৌত্রকে অংশ দিতে শুরু করিয়াছেন। যে বিচারপতিগণ উহা করিতেছেন তাঁহারা পরকালে যাইবেন কোথায়?
৯। স্ত্রীত্যাগ ও হিলা প্রথার তাৎপর্য কি?
কেহ কেহ স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী বলিয়া থাকেন। এ কথাটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। অর্ধ-অঙ্গিনী বা সিকি-অঙ্গিনী না হইলেও আদিপুরুষ হজরত আদমের বাম পিঞ্জরের অস্থি হইতেই নাকি প্রথমা নারী হাওয়া বিবি সৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাই বিবি হাওয়াকে আদমের অঙ্গজ হিসাবে ‘অঙ্গিনী’ বলা খুবই সমীচীন। ইহা ছাড়া সংসার জীবনে নারীরা পুরুষদের একাংশ হিসাবেই বিরাজিতা।
মানুষের হস্তপদাদি কোন অঙ্গ রুগ্ন হইলে উহার প্রতিকারের জন্য চিকিৎসা করান হয়। রোগ দুরারোগ্য হইলে ঐ রুগ্নাঙ্গ লইয়াই জীবন কাটাইতে হয়। রুগ্নাঙ্গ লইয়া জীবন কাটাইতে প্রাণহানির আশঙ্কা না থাকিলে কেহ রুগ্নাঙ্গ ত্যাগ করে না। স্ত্রী যদি স্বামীর অঙ্গই হয়, তবে দূষিতা বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করা হয় কেন? কোনরকম কায়ক্লেশে জীবনযাপন করা যায় না কি?
জবাব হইতে পারে যে, শখের বশবর্তী হইয়া কেহ কখনও স্ত্রীত্যাগ করে না। সাংসারিক বিশৃঙ্খলা ও মানসিক অশান্তি যখন চরমে পৌঁছে, তখনই কেহ কেহ স্ত্রীত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কথাটি কতকাংশে সত্য, কিন্তু যাহারা একাধিক স্ত্রী ত্যাগ করিয়া বাছা বাছা রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহারা কি কায়েমী বিবাহিতদের (হিন্দুদের) চেয়ে দাম্পত্যসুখে অধিক সুখী?
রসায়ন শাস্ত্রের (Chemistry) নিয়মে দুইটি পদার্থের মিশ্রণ ঘটাইতে হইলে পূর্বেই জানা উচিত যে, পদার্থ দুইটি মিশ্রণযোগ্য কি না। কেহ যদি জলের সহিত বালু বা খড়িমাটি মিশাইতে চান, তাহা পারিবেন না। সাধারণত তৈল ও জল একত্র মিশে না। তবে উহা একত্র করিয়া বিশেষভাবে রগড়াইলে সাময়িকভাবে মিশিয়া পুনরায় বিযুক্ত হয়। কিন্তু চিনি বা লবণ জলে মিশাইলে উহা নির্বিঘ্নে এক হইয়া যায়। বিবাহ ব্যাপারে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনও এইরূপ একটি মিশ্রণ।
পাত্র ও পাত্রীর মৌলিক চরিত্রসমূহ শেষোক্ত পদার্থের ন্যায় মিশুক কি-না, তাহা বিচার না করিয়া জল-খড়ি ও তৈল-জল মিশ্রণের মত যথেচ্ছ মিলন প্রচেষ্টার বিফলতাই ‘তালাক’ প্রথার কারণ নয় কি?
এতদ্দেশে অনেক হিন্দুর ভিতর কোষ্ঠী বা ঠিকুজীর সাহায্যে বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের প্রচেষ্টা চলিতে দেখা যায়। মানুষের জন্মমুহুর্তে তিথি, লগ্ন ও রাশির সংস্থান এবং চন্দ্র, সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদির আকাশে বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠান জাতকের দেহ-মনের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে আর এ বিষয়ে ফলিত জ্যোতিষ (Astrology)-এর সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত কি না তাহা জানি না। কিন্তু ইহাতে অন্তত ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হিন্দুগণ জানিতে চেষ্টা করেন যে, বিবাহে বর-কন্যার মিল হইবে কি না। মুসলমানদের বিবাহ প্রথায় পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে যদি কোনরূপ মনোবিজ্ঞানসম্মত বিচার প্রণালী উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করা যাইত, তাহা হইলে তালাক প্রথা এত অধিক প্রসার লাভ করিত না।
স্বামী ও স্ত্রীর মনোবৃত্তি বা স্বভাবের বৈষম্যবশতই যে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়, তাহা সুনিশ্চিত। তবে এই বৈষম্য দুই প্রকারে হইতে পারে। কোন ক্ষেত্রে হয়তো স্ত্রীই দোষী, কিন্তু স্বামী সাধু ও সচ্চরিত্র। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রী সচ্চরিত্রা, কিন্তু স্বামী অসচ্চরিত্র ও বদমায়েশ। ভালর সহিত মন্দের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই উপরোক্ত যে কোন ক্ষেত্রেই স্বামী ও স্ত্রীর মনোমালিন্য হইতে পারে এবং তাহাতে বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটিতে পারে। দোষ যাহারই হউক না কেন, বাহিরের লোক উহার বিশেষ কিছু জানিতে পায় না। কিন্তু পরিণাম উভয় ক্ষেত্রেই এক। অর্থাৎ স্ত্রীত্যাগ।
তালাকের ঘটনা যেভাবেই ঘটুক না কেন, ত্যাজ্যা স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণে স্ত্রী যে নির্দোষ, ইহাই প্রমাণিত হয়। মনে হয় যে, ক্রোধ, মোহাদি কোন রিপুর উত্তেজনায় স্বামী ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়াই অন্যায়ভাবে স্ত্রীত্যাগ করে এবং পরে যখন সম্বিৎ (জ্ঞান) ফিরিয়া পায়, তখন স্থিরমস্তিষ্কে সরলান্তকরণে ত্যাজ্যা স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। অর্থাৎ স্বামী যখন তাহার নিজের ভ্রম বুঝিতে পারে, তখনই ত্যাজ্যা স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে অভিলষিত হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, স্ত্রীর উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া অথবা ক্রোধাদির বশবর্তী হইয়া স্ত্রীত্যাগে স্বামীই অন্যায়কারী বা পাপী। অথচ পুনঃগ্রহণযোগ্যা নির্দোষ স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণে ‘হিলা’ প্রথার নিয়মে স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় সেই নির্দোষ স্ত্রীকেই। অপরাধী স্বামীর অর্থদণ্ড, বেত্রাঘাত ইত্যাদি না-ই হউক, অন্তত তওবা (পুনরায় পাপকর্ম না করিবার শপথ) পড়ারও বিধান নাই, আছে নিষ্পাপিনী স্ত্রীর ইজ্জতহানির ব্যবস্থা। একের পাপে অন্যকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় কেন?
ত্যাগের পর স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্যবন্ধন থাকেনা বটে, কিন্তু দাম্পত্যভাবটি কি সহজেই তাহাদের হৃদয় হইতে মুছিয়া যায়? যদি যায়-ই, তবে হিলা প্রথার নিয়মানুসারে অস্থায়ী (Temporary) কলেমাটি যে কোন লোকের সাথে বিশেষত পূর্বস্বামীর চাচা, ফুফা, মামার সহিত না হইয়া প্রায়ই ভগ্নিপতি বা ঐ শ্রেণীর কুটুম্বদের সহিত হয় কেন?
ত্যাগের পর স্বামী তাহার মস্তিষ্কের উত্তেজনা বা ক্রোধাদি বশত স্ত্রীর প্রতি কিছুদিন বীতস্পৃহ থাকিলেও সরলা স্ত্রী সহজে স্বামীরূপ হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় যদি সে স্বামীর পুনঃগ্রহণের কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহার হৃদয়পটে পূর্ব দাম্পত্য-জীবনের স্মৃতি আরো গাঢ়রূপে অঙ্কিত হয়। এমতাবস্থায় স্ত্রী পূর্বস্বামীর পুনঃগ্রহণের প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দেয়। কিন্তু ইহার পরে হিলাকৃত নবীন দুলহার অস্থায়ী কলেমার ইজাব (সম্মতি) দেওয়াটি কি তাহার আন্তরিক?
হিলা প্রথায় বর নির্বাচনে বেশ একটু কারসাজী আছে। বয়স্কা হইলেও হিলাকৃত বর নির্বাচনে স্ত্রীর কোন অধিকার থাকে না, নির্বাচনকর্তা সর্বক্ষেত্রেই পূর্বস্বামী। প্রথমত সে বিচার করে যে, সিন্দুকের চাবি কাহার হস্তে দেওয়া উচিত। নবীন দুলহা তাহার হাতের লোক কি-না। সে তাহার নির্দেশমত সময়োচিত কাজ করিবে কি না। সর্বোপরি লক্ষ্য রাখা হয় যে, নবদম্পতির মধ্যে ভালবাসা জন্মিতে না পারে।
এইরূপ হিসাব মিলাইয়া প্রাক্তন স্বামীর দ্বারা বর নির্বাচিত হইলে, সেই বিবাহকালীন স্ত্রীর ইজাব বা সম্মতির কোন মূল্যই থাকিতে পারে না বা থাকে না। স্ত্রী সম্মতি যাহা দিল তাহা তাহার পূর্ব-স্বামী লাভের জন্য, হাল স্বামীর জন্য নয়। অর্থাৎ সে জানে যে, তাহার এই বিবাহ মাত্র একদিনের জন্য এবং এই বিবাহের মাধ্যমেই হইবে তাহার পূর্বস্বামী লাভ। তখন সে মনে মনে এই সিদ্বান্তই করে—
“মোর বাড়ী আর স্বামীর বাড়ী, মধ্যখানে নদী—
কেমনে যাব, এই খেওয়া পার না হই যদি?”
ফলত স্ত্রী মুখে ইজাব দিল নূতন দুলহার আর অন্তরে কামনা করিল পূর্বস্বামীকে।
অতঃপর বাসর ঘর। এখানে নবীন দুলহার অত্যাচার সহ্য না করিলে শাস্ত্রমতে স্ত্রীর মুক্তির উপায় নাই। কাজেই — মান-অভিমান, লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়া স্ত্রী প্রভাতের অপেক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু তাহার হৃদয় পূর্বস্বামীর উদেশ্যে ব্যাকুলস্বরে গাহিতে থাকে—
“হয়ে তব অভিলাষী আমি এখন কারাবাসী
বুকে মম চাপিল পাষাণ।
জানিনা মোর কি-বা পাপ, কি কারণ এই পরিতাপ,
হবে না কি নিশি অবসান?”
নবদম্পতির এইরূপ মিলন ব্যভিচারের নামান্তর নয় কি?
উপসংহার
মানুষের মনে জিজ্ঞাসার অন্ত নাই। কোন না কোন বিষয়ে কোন না কোন রকমের জিজ্ঞাসা প্রত্যেকের মনেই আছে, যেমন আপনার, তেমন আমার। অসংখ্য জিজ্ঞাসার মধ্যে মাত্র কতিপয় জিজ্ঞাসা এই পুস্তকখানিতে আমরা প্রশ্নাকারে ব্যক্ত করিলাম। কিন্তু ইহা শুধু আমাদেরই প্রশ্ন নহে। যে সকল চিন্তাশীল মনীষী জীব ও জগত বিষয়ক ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করেন, হয়তো তাঁহাদের মনেও অনুরূপ প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু অনেকেই তাহা প্রকাশ করেন না। হয়ত কেহ তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহলে দুই-চারিটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন, কেহবা অন্তরে চাপিয়া রাখেন।
বর্তমান যুগটি বিজ্ঞানের যুগ এবং যুক্তিবাদেরও। বিজ্ঞান পৃথিবীর বুকে আত্মশক্তি বা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, কাহারও অনুকম্পায় নয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মিটাইতেছে বিজ্ঞান। আপনি যদি বিজ্ঞানের দান গ্রহণে অমত করেন, তাহা হইলে আকাশের দিকে তাকান, ঘড়ির দিকে নয়। আপনি যদি বিজ্ঞানের দান গ্রহণ করিতে না চাহেন, তাহা হইলে যানবাহনে বিদেশ সফর ও জামা-কাপড় ত্যাগ করুন এবং কাগজ-কলমের ব্যবহার ও পুস্তক পড়া ত্যাগ করিয়া মুখস্ত শিক্ষা শুরু করুন। ইহার কোনটি করা আপনার পক্ষে সম্ভব? বোধহয় একটিও না। কেননা মানব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বিজ্ঞানের দান অনস্বীকার্য। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন হইতে শুরু করিয়া দেশলাই ও সূচ-সুতা পর্যন্ত সবই বিজ্ঞানের দান। বিজ্ঞানের কোন দান গ্রহণ না করিয়া মানুষের এক মুহুর্তও চলে না। মানুষ বিজ্ঞানের কাছে ঋণী। কিন্তু সমাজে এমন একশ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা হাতে ঘড়ি ও চক্ষে চশমা আঁটিয়া মাইকে বক্তৃতা করেন আর ‘বস্তুবাদ’ বলিয়া বিজ্ঞানকে ঘৃণা ও ‘বস্তুবাদী’ বলিয়া বিজ্ঞানীদের অবজ্ঞা করেন। অথচ তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, ভাববাদীরা বস্তুবাদীদের পোষ্য। বিজ্ঞান মানুষকে পালন করে। কিন্তু ধর্ম মানুষকে পালন করে না, বরং মানুষ ধর্মকে পালন করে এবং প্রতিপালনও। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান-বিরোধী কোন শিক্ষাই গ্রহণীয় নয়।
আধুনিককালের অধিকাংশ মানুষ চায় কুসংস্কার হইতে মুক্তি, চায় সত্যের সন্ধান। ধর্মরাজ্যের যত্রতত্র অল্পাধিক কুসংস্কার স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছে। আবার সভ্য মানব সমাজে এমন কোন মানুষ নাই, যিনি কোন না কোন ধর্মের আওতাভুক্ত নহেন। কাজেই এরূপ মানুষও অল্পই আছেন, যাঁহাদের কোনরূপ কুসংস্কার স্পর্শ করে নাই। উদাহারণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বৈদিক, পারসিক ও ইহুদী ইত্যাদি আদিম জাতি (ধর্ম)-গুলির কল্পিত দেব-দেবী, দৈত্য-দানব, ভূত-পিশাচ, ডাকিনী-যোগিনী, শীতলা, ওলা, পেত্নী, ইত্যাদি জীবসমূহের কোন অস্তিত্ব জগতে পাওয়া যায় না। অথচ ঐগুলির সত্যতা ও চরিত্র সম্বন্ধে সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের আস্থা কম নয়। হয়ত কোন এক সময়ে ঐগুলিকে ‘সত্য’ বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু বর্তমানে উহারা ‘মিথ্যা’ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এখন ঐগুলিকে ত্যাগ ও প্রমাণিত ‘সত্য’কে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। কোন রকম গোঁড়ামীকে প্রশ্রয় না দিয়া প্রত্যেক ধর্মকে যথাসম্ভব কুসংস্কারমুক্ত করা উচিত। কুসংস্কার ত্যাগ করার অর্থ ‘ধর্মকে ত্যাগ করা’ নহে। যদি কেহ কুসংস্কার ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হন এবং বলিতে চাহেন যে, কুসংস্কার ত্যাগ করিলে ধর্ম থাকিবে না, তাহা হইলে মনে আসিতে পারে যে, ধর্মরাজ্যে কি কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নাই? এ প্রসঙ্গে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি। আমাদের অভিযান শুধু অসত্য বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, কোন ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। প্রত্যেকটি ধর্ম থাকিবে মিথ্যার আবর্জনাবর্জিত ও পবিত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।
‘সত্যের সন্ধান’ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া স্বাধীন চিন্তাবীদ বন্ধুগণ সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিকভাবে আমাদের মতবাদ অনুধাবন করিতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস। এ বিষয়ে আমরা স্বাধীন চিন্তাশীল মনীষীদের মূল্যবান মতামতের প্রত্যাশী। আপনারা আপনাদের চিন্তালব্ধ মতামতসমূহ আমাদিগকে জানাইলে এবং অত্র পুস্তকখানির ত্রুটি প্রদর্শনপূর্বক উহা সংশোধনের উপদেশ দান করিলে বাধিত হইব।
আমাদের মনে হয় যে, এমন অনেক সৌভাগ্যশালীও আছেন, যাঁহাদের নিকট এই পুস্তকে লিখিত প্রশ্নগুলি অতিশয় তুচ্ছ। হয়ত তাঁহাদের নিকট প্রশ্নগুলির সমাধান অজ্ঞাত নহে। তাঁহাদের নিকট আমাদের একান্ত অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন এই প্রশ্নগুলির যথাযোগ্য সমাধান ও ব্যাখ্যা সাধারণ্যে প্রকাশ করেন। করিলে আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।
পরিশেষে, এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে সমস্ত পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, উহার গ্রন্থকার মহোদয়গণের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।
বিনীত
গ্রন্থকার
গ্রামঃ লামচরি
ডাকঘরঃ চরবাড়িয়া
জিলাঃ বরিশাল।।
টীকা
টীকার নম্বর পুস্তকের নাম গ্রন্থকারের নাম পৃষ্ঠা বা অনুচ্ছেদ
১। পবিত্র কোরান (সুরা সেজদা) —- ১; ৪
২। সরল বাংলা অভিধান সুবলচন্দ্র মিত্র ৩০০
৩। মানব মনের আযাদি আবুল হাসানাত ৬৭
৪। পৃথিবীর ঠিকানা অমল দাসগুপ্ত ৪৪
৫। পৃথিবীর ঠিকানা অমল দাসগুপ্ত ১৫০, ১৫১
৬। সরল বাংলা অভিধান সুবলচন্দ্র মিত্র ৮৭২
৭। সরল বাংলা অভিধান সুবলচন্দ্র মিত্র ২৫১
৮। আদিপুস্তক (তৌরিত —– ২; ৮-১৪
৯। পৃথিবীর ঠিকানা অমল দাসগুপ্ত ১০২
১০। বিলেতে সাড়ে সাতশো দিন মু. আ. হাই ১৪১, ১৪২
১১। নক্ষত্র পরিচয় প্রমথনাথ সেনগুপ্ত ১৪, ১৬
১২। মহাকাশের ঠিকানা অমল দাসগুপ্ত ৯৫
১৩। পৃথিবীর ঠিকানা অমল দাসগুপ্ত ১০
১৪। খ-গোল পরিচয় মো. আ. জব্বার ৩০৭
১৫। খালেদ ইবনে অলীদ মওলানা আখতার ফারুকী ২২৪, ২২৫
১৬। গ্রহ-নক্ষত্র জগদানন্দ রায় ২৫৪, ২৫৫
১৭। নক্ষত্র পরিচয় প্রমথনাথ সেনগুপ্ত ১৪, ১৫
১৮। সরল বাংলা অভিধান সুবলচন্দ্র মিত্র ৬৯১
১৯। জীব-জগতের জন্মকথা আ. হক খোন্দকার ১৩
২০। আদিপুস্তক (তৌরিত) ——- ৫; ৩-২৮ ও ৭; ৬
২১। আদিপুস্তক (তৌরিত) —— ৭; ১২
২২। আদিপুস্তক (তৌরিত) ——- ৬; ১৫ ও ৭; ৪
২৩। ম্যাজিকের খেলা পি. সি. সরকার ১৬-২২
২৪। ঐতিহাসিক অভিধান মো. মতিয়র রহমান ২
২৫। যাত্রা পুস্তক (তৌরিত) ——— ১২; ৩০-৩৩ ও ৩৭
২৬। যাত্রাপুস্তক (তৌরিত) ——— ১২; ৩১, ৩২ ও ৩৬
২৭। যাত্রাপুস্তক (তৌরিত) ———- ১৪; ২১
২৮। যাত্রাপুস্তক (তৌরিত) ——— ১৪; ২৭
২৯। যাত্রাপুস্তক (তৌরিত) ———- ১১; ১৬-১৯
৩০। ঐতিহাসিক অভিধান মো. মতিয়র রহমান ৫
৩১। সরল বাংলা অভিধান সুবলচন্দ্র মিত্র ৫০৫
৩২। ঐতিহাসিক অভিধান মো. মতিয়র রহমান ১৩
৩৩। লুক (ইঞ্জিল) ——— ১; ৫-৭
৩৪। ঐতিহাসিক অভিধান মো. মতিয়র রহমান ২৩, ২৪
৩৫। মথি (ইঞ্জিল) ——— ২; ১৪-২৩
৩৬। লবীয় পুস্তক (ইঞ্জিল) ——— ২৪; ১৭
দ্বিতীয় বিবরণ (ইঞ্জিল) ——— ২২; ২৩, ২৪, ২৮, ২৯
৩৭। পৃথিবীর ইতিহাস দেবীপ্রসাদ ১৬২-১৬৪
৩৮। পবিত্র কোরান (সুরা নেছা) ——– ২; ১৩
৩৯। পবিত্র কোরান (সুরা নেছা) ——– ২; ১৪
৪০। আল সিরাজী ফিল মিরাস সিরাজউদ্দিন মুহাম্মদ ২০
৪১। আদিপুস্তক (তৌরিত) ——– ৫; ৫
৪২। ঐতিহাসিক অভিধান মো. মতিয়র রহমান ২
৪৩। প্রাচীন মিশর শচীন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায় ৯, ১৮৭, ১৮৮
৪৪। পৃথিবীর ইতিহাস দেবীপ্রসাদ ১৩৫, ১৩৬, ২৮১, ৩০৮, ৩২৮
৪৫। আদিপুস্তক (তৌরিত) ——— ২; ৮-১০
৪৬। আদিপুস্তক (তৌরিত) ——— ৩; ৮
৪৭। পৃথিবীর ইতিহাস দেবীপ্রসাদ ১৩৫-১৩৭ □